
প্রিন্ট: ১৪ এপ্রিল ২০২৫, ০৬:০২ পিএম
পরিচয়ের রাজনীতি ও বাঙালি মুসলমান
ড. হাসান মাহমুদ
প্রকাশ: ০৬ এপ্রিল ২০২৫, ১২:০০ এএম
প্রিন্ট সংস্করণ
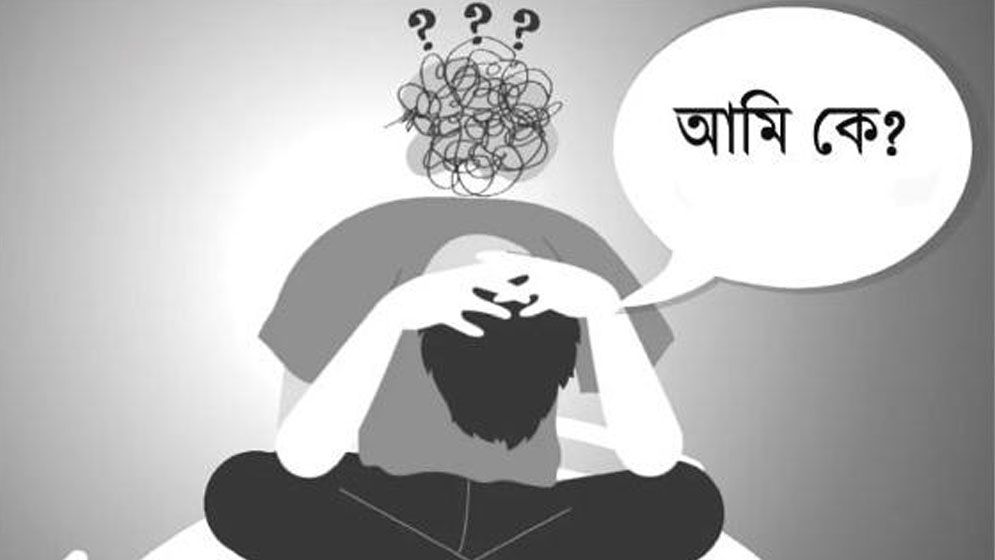
গত বছরের ২৯ ফেব্রুয়ারি ঢাকার বেইলি রোডে একটা ভবনে অগ্নিকাণ্ডে আরও ৪৩ জন হতভাগ্যের সঙ্গে অভিশ্রুতি শাস্ত্রী নামের একজন তরুণীরও প্রাণহানি ঘটে। অভিশ্রুতি একটা অনলাইন নিউজ পোর্টালে রিপোর্টার হিসাবে কাজ করেছেন। দুর্ঘটনার সময় তিনি সেই ভবনে একটা রেস্টুরেন্টে তার এক বন্ধুর সঙ্গে খেতে গিয়ে দুর্ভাগ্যবশত অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন।
নামের শেষে শাস্ত্রী আছে, এমন বিখ্যাত দুজন ব্যক্তির একজন হলেন পড়াশোনার পরিমণ্ডলে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আর খেলাধুলার জগতে ক্রিকেটার রবি শাস্ত্রী। তাদের দুজনই হিন্দু। অভিশ্রুতি নামটাও হিন্দুদের মধ্যেই প্রচলিত। অকালপ্রয়াত অভিশ্রুতি তার ফেসবুক প্রোফাইলে বেশকিছু ছবি পোস্ট করেছিলেন; যেখানে দেখা গেছে, তিনি রমনার কালীমন্দিরে পূজা করতেন। উপরন্তু সেই কালীমন্দরের পরিচালক মৃত অভিশ্রুতিকে হিন্দু দাবি করে তার মৃতদেহের হিন্দু নিয়মে সৎকার করার লিখিত দাবি জানিয়েছিলেন পুলিশের কাছে। তার দাবি অনুযায়ী, অভিশ্রুতির জন্ম উত্তর ভারতে। জন্মের পর তাকে কুষ্টিয়ার এক মুসলমান দম্পতি পালন করে। কিন্তু গোল বাঁধে, সবুজ শেখ নামের একজন পুলিশের কাছে অভিশ্রুতিকে নিজের কন্যা হিসাবে দাবি করে লাশের দাফনের অনুমতি চাইতে গেলে। প্রথমে সম্ভাব্য প্রতারক মনে করে পুলিশ সবুজ শেখকে আটক করে রাখে। এরপর প্রতারণার জোরালো প্রমাণের অভাবে তাকে ছেড়ে দেয়। পত্রিকা ও টিভিতে অভিশ্রুতির মায়ের বিলাপ আর মৃত কন্যার লাশের জন্য আকুল আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ তার প্রকৃত পরিচয় নির্ণয় করার জন্য ডিএনএ টেস্টের সিদ্ধান্ত নেয়। এগারো দিনের মাথায় ডিএনএ টেস্টের রেজাল্ট নিশ্চিত করে, অভিশ্রুতি আসলেই সবুজ শেখের কন্যা বৃষ্টি খাতুন। পুলিশ তার লাশ জন্মদাতা পিতা-মাতার কাছে হস্তান্তর করে। তারা লাশ নিজ বাড়িতে নিয়ে মুসলমান প্রথামতো দাফন ও কবরস্থ করার ব্যবস্থা করে। মহান আল্লাহর কাছে তার রুহের মাগফিরাত ও নাজাতের জন্য দোয়া করি।
বৃষ্টি, বর্ষা আর ঝর্ণা। তিন বোন। সবুজ শেখ আর বিউটি বেগমের ঘরে আলো করে আসা তিন কন্যা। পল্লিগ্রামে সীমিত আয়ের এক বাঙালি মুসলমানের পরিবারে জন্ম নেওয়া এ মেয়েরা মা-বাবার আদরে বেড়ে উঠছিল গ্রামের আলো-বাতাসে। মুসলমান প্রতিবেশীদের আর সব সন্তানের মতোই নামাজ-রোজাসহ অন্যান্য ধর্মীয় আচার-আচরণের মধ্য দিয়ে বাঙালি মুসলমান কন্যা হিসাবেই বেড়ে উঠছিল তিনজন। স্থানীয় স্কুল থেকে কলেজ, সেখান থেকে ঢাকায় ইডেন কলেজে ভর্তি হয়েছিল বড় কন্যা বৃষ্টি খাতুন। পরিবারের আর্থিক টানাপোড়েনের কারণে প্রয়োজনীয় অর্থ উপার্জনের জন্য পড়াশোনার পাশাপাশি সাংবাদিকতায় জড়িত হয় বৃষ্টি। তার সর্বশেষ কর্মক্ষেত্র ছিল দ্য রিপোর্ট ডট লাইভ নামের একটা নিউজ পোর্টাল।
পল্লিগ্রামের নিুআয়ের মুসলমানের ঘরে জন্ম নিয়ে, জীবন ও জীবিকার সংগ্রামে জয়ী হওয়ার আশায় ঢাকা শহরে এসে এমন কী পরিস্থিতিতে পড়ে মুসলমানের সন্তানরা নিজেদের বাবা-মায়ের দেওয়া নাম-পরিচয় পরিত্যাগ করে, শেকড়ের সঙ্গে সব সামাজিক বন্ধন ছিন্ন করে, হিন্দু পরিচয় গ্রহণ করে, নামাজ-রোজা বাদ দিয়ে মন্দিরে গিয়ে পূজা দিয়ে সমাজে নিজেকে হিন্দু হিসাবে পরিচয় দেয়? হিন্দু পরিবারে জন্ম হওয়া ব্যতিরেকে, হিন্দু হওয়ার রীতি না থাকা সত্ত্বেও কেন বৃষ্টি খাতুন নিজের জন্য একটা হিন্দু নাম গ্রহণ করেছিল এবং হিন্দু পরিচয় গ্রহণ করতে চেষ্টা করেছিল? আর তার সেই চেষ্টা কেনই বা সফল হতে পারল না?-এ প্রশ্নগুলো অভিশ্রুতি বা বৃষ্টি খাতুনের সম্পর্কে হলেও এগুলো সার্বিকভাবে বাঙালি মুসলমান জনগোষ্ঠীর পরিচয়ের একটা সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংকটকে নির্দেশ করে, যেটা একাত্তরে স্বাধীন বাংলাদেশ হওয়ার পর থেকে ক্রমাগত বেড়েই চলেছে।
পল্লিগ্রামের মুসলমান পরিবারে জন্ম নিয়ে ঢাকায় এসে উচ্চশিক্ষা অর্জন করে মধ্যবিত্ত সমাজে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পথে নিজের ইসলামগন্ধী নামকে পছন্দমতো পরিবর্তন করে নেওয়ার একটা প্রচলন লক্ষণীয়। নব্বইয়ের দশকের শেষভাগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এসে দেখেছি বন্ধুবান্ধবের কেউ কেউ মা-বাবার দেওয়া মুসলিম নাম (মূলত আরবি বা ফারসি) পরিবর্তন করে ফেলে। আশফাক থেকে অয়ন, আক্কাস থেকে আকাশ, কুলসুম থেকে কলি, নাসিমা থেকে ন্যান্সি ইত্যাদি। ডাকার সুবিধার্থে ডাকনামের এ পরিবর্তন তেমন একটা গুরুতর বিষয় নয়। কিন্তু কেউ কেউ দেখা যায়, তাদের আসল বা অফিশিয়াল নামও পরিবর্তন করে ফেলে এবং সেই পরিবর্তিত নামেই নিজেকে পরিচিত করতে সচেষ্ট হয়। নিজে নিজেই পরিবর্তন করে নেওয়া এ নামগুলো সহজেই অনুমান করা যায়; যেমন-স্বকৃত নোমান, রাখাল রাহা, ব্রাত্য রাইসু, দন্ত্যস রওশন, অনন্ত জলিল ইত্যাদি। এ নামগুলোর মধ্যে খানিকটা আরবি বা ফারসি শব্দ, আর খানিকটা সংস্কৃত বা দেশি শব্ধ। নাম পরিবর্তনের এই ধারা বাড়তে বাড়তে কারও কারও ক্ষেত্রে এমন পর্যায়ে চলে যায়, সেখানে থেকে আরবি/ফারসি সম্পূর্ণভাবে বাদ দিয়ে সংস্কৃত বা দেশি শব্দের নাম গ্রহণ করা হয়। যেমন : বৃষ্টি খাতুন থেকে অভিশ্রুতি শাস্ত্রী বা সুরাইয়া সুলতানা থেকে বীথি সপ্তর্ষি। আবার কিছু কিছু ব্যক্তির ক্ষেত্রে, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষিত এবং উচ্চ বা মধ্যবিত্ত মুসলমান পরিবারের মা-বাবাই তাদের সন্তানকে দেশি বা সংস্কৃত শব্দের নাম দিয়ে থাকেন, যেমন : শ্রেয়া সর্বজয়া।
এই যে বাঙালি মুসলমান পরিবারের সন্তানদের নামের পরিবর্তনের একটা প্রবণতার উল্লেখ করলাম, এর মধ্যে একটা বিশেষভাবে লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, এ নামগুলো থেকে ইসলামের সঙ্গে সম্পর্কিত শব্দগুলো বাদ দিয়ে এমন কিছু শব্দ যোগ করা হয়, যা দিয়ে আরবি/ফারসি ব্যাকগ্রাউন্ডের থেকে দূরত্ব বোঝা যায়। মা-বাবার প্রজন্মের নাম যেখানে পুরোপুরি আরবি/ফারসি শব্দ দিয়ে গড়া এবং যা পুরোপুরি ইসলামি সামাজিক পরিচয়কে নির্দেশ করে, সেখানে পরিবর্তিত নামগুলো ইসলাম থেকে খানিকটা দূরত্ব নির্দেশ করে। আর এই যে ইসলাম থেকে দূরত্বসূচক নাম বা এর অংশবিশেষ গ্রহণ করা, এটা কিন্তু আবার স্বেচ্ছায়ই। উল্লিখিত নামের ব্যক্তিদের সবাই নিজ নিজ ইচ্ছায় তাদের ইসলামগন্ধী নামকে আংশিক বা পরিপূর্ণভাবে বদল করে সংস্কৃত বা দেশি শব্দের নতুন নাম গ্রহণ করেছেন, যা দিয়ে তারা নিজেদের সমাজে নতুনরূপে পরিচিত করাতে চান। তাদের এ নতুন পরিচয়ের একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো, এটি বাংলাদেশে প্রচলিত প্রথাগত ইসলামি নাম থেকে আলাদা হয়ে দেশীয় বা সেক্যুলার হিসাবে গ্রহণযোগ্য একটা পরিচয়কে নির্দেশ করে।
প্রত্যেক সমাজেই ব্যক্তির নামকরণ বিষয়টি সামাজিক, ব্যক্তির ইচ্ছা অনুযায়ী হয় না। ব্যক্তির নাম পরিবার থেকে পছন্দ করা হয়, প্রায়ই ব্যক্তির জন্মেরও আগে। আর প্রত্যেকের পরিবারই সমাজে বিদ্যমান প্রথা অনুযায়ী সন্তানের নামকরণ করে থাকে। এ নামের মধ্য দিয়েই ব্যক্তি সমাজে পরিচিত হয়। আর এজন্যই নামের মধ্যে ব্যক্তির পারিবারিক, ধর্মীয়, জাতিগত প্রভৃতি ব্যাকগ্রাউন্ডেরও ইশারা থাকে। বাঙালি মুসলমান জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই যে নামের পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে, এটা থেকে বাংলাদেশের সার্বিক সামাজিক অবস্থায় একটা পরিবর্তনের হদিস পাওয়া যায়। নামের এ পরিবর্তনকে ব্যাখ্যা করার জন্য আমাদের দেখতে হবে এমন বিষয়গুলো, যা থেকে একটা মুসলিম নামধারী ব্যক্তি বঞ্চিত হয় বা হতে পারে এমন আশঙ্কা থাকে। পাশাপাশি এটাও দেখতে হবে, ইসলামি নামের কারণে আগের প্রজন্মের ব্যক্তি যেসব সামাজিক স্বীকৃতি বা সুবিধাদি লাভ করতে পারত, সেসব এখনো পাওয়া সম্ভব কি না।
পরাশক্তির বিরুদ্ধে বাঙালি মুসলমানের স্বাধিকার সংগ্রামের সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে। ফকির বিদ্রোহ, হাজী শরীয়তুল্লাহর ফরায়েজী আন্দোলন, মীর নেসার আলী তিতুমীরের আন্দোলনসহ ব্রিটিশ শাসনামলজুড়েই বাঙালি মুসলমান সংগ্রাম করেছে। কখনো স্বাধিকারের জন্য হলেও প্রায়ই নিজেদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক দাবিদাওয়াভিত্তিক ছিল সেসব আন্দোলন; যেমন : জমিদারের অন্যায্য খাজনার বিরুদ্ধে, গরু কুরবানির অধিকারের দাবিতে প্রভৃতি। রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনও চলছিল, যা বাঙালি মুসলমান সমাজ সামাজিক-সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যমূলক প্রথা ও নানা কর্মকাণ্ডের জন্ম দিয়েছিল। যেমন : বর্তমানে প্রচলিত ইসলামের নানা মাজহাবের জ্ঞানী বক্তাদের নিয়ে ‘বাহাস’ আয়োজন করা, অন্য ধর্মের পণ্ডিত ব্যক্তিদের সঙ্গে ধর্মীয় ও সামাজিক বিষয়াদি নিয়ে পাবলিক বিতর্ক করা, রাসুল (সা.), বড় পির আবদুল কাদের জিলানীসহ অন্যান্য প্রসিদ্ধ ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের জন্ম-মৃত্যু উপলক্ষ্যে নানা সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা প্রভৃতি। এসবের মধ্য দিয়ে উনিশ শতকের শেষভাগে বাঙালি মুসলমান সমাজে একধরনের ইসলামি পুনর্জাগরণের সূচনা হয়। সেই পরিপ্রেক্ষিতে উনিশ শতকের শেষার্ধে রাফিউদ্দিন আহমেদ বাঙালি মুসলমান সমাজে নামকরণের মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ করেন। The Bengal Muslims 1871-1906 : A Quest for Identity নামক গবেষণা গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে রাফিউদ্দিন আলোচনা করেন কীভাবে একটা উদীয়মান মুসলমান মধ্যবিত্ত তৎকালীন হিন্দু ভদ্রলোক সমাজের সঙ্গে প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে একটা ইসলামি সামাজিক পরিচয় নির্মাণে ব্রতী হয়, যার প্রকাশ ঘটে নামকরণের মধ্যে। তিনি উল্লেখ করেন, উনিশ শতকের শুরুর দিকে বাঙালি মুসলমানদের প্রকাশিত তিনটি খবরের কাগজের বাংলা নাম ও প্রকাশিত খবরের বিষয়বস্তু ছিল বাংলা। কিন্তু শতাব্দীর শেষভাগে এসে দেখা যায়, বাঙালি মুসলমানরা যে ডজনখানেক পত্রিকা প্রকাশ করছে, তার সবকটির নামই সম্পূর্ণ আরবি বা ফারসি তথা ইসলামি। বাঙালি মুসলমান সমাজে এমন ইসলামিকরণ তিনি লক্ষ করেন ব্যক্তির নামকরণেও। নামের এ পরিবর্তনকে তিনি আশ্রাফাইজেশন হিসাবে চিহ্নিত করেছেন, যার মধ্য দিয়ে সামাজিকভাবে ক্রমবর্ধিষ্ণু বাঙালি মুসলমান একই সঙ্গে ইসলামি পরিচয় এবং উচ্চ সামাজিক মর্যাদার দাবি প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পায়।
ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধিকার আন্দোলন যতই জোরালো হয়ে ওঠে, ইসলামি তথা আরবি/ফারসি নামের প্রতি বাঙালি মুসলমানের এ আকর্ষণও সমানুপাতে বেড়ে চলে। ইতিহাসের কালক্রমে ১৯৪৭ সালে সমগ্র ইন্ডিয়ান মুসলমানের সঙ্গে সম্মিলিত প্রয়াসে মুসলমানদের জন্য আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হলে আরবি/ফারসির প্রতি বাঙালি মুসলমানের এ অনুরাগ সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে। ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় সব পর্যায়ে পরিচয়ের মূল পাটাতনে অন্যতম নির্ধারণ হয়ে দাঁড়ায় ইসলাম। পত্রিকা, বইপুস্তক ইত্যাদির প্রকাশনা, সামাজিক-সাংস্কৃতিক আচার অনুষ্ঠান, ইত্যাদিতেও ইসলামের প্রাধান্য দেখা যায়। একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টাকে আরও ভালোভাবে বোঝা যাবে। ১৯২২ সালে প্রকাশিত মওলানা আকরম খাঁর অনূদিত সুরা ইনশিরাহর শেষ চার আয়াত : ৫. অনন্তর নিশ্চয় সংকটের সঙ্গেই স্বাচ্ছন্দ্য, ৬. নিশ্চয় সংকটের সঙ্গে স্বাচ্ছন্দ্য, ৭. অতএব অবসর পাইতে কৃতসংকল্প হইবে, ৮. স্বীয় প্রভুর পানে মনোনিবেশ করিবে।
ইন্ডিয়ান মুসলমানের জন্য স্বাধীন রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার এক যুগ পরে ১৯৫৯ সালে তার অনূদিত সুরা ইনশিরাহর শেষ চার আয়াত : ৫. কারণ, প্রত্যেক মুশকিলের পর আছে আছানি, ৬. নিশ্চয় বর্তমান মুশকিলের পরও আসিতেছে আছানি, ৭. অতএব অবসর পাইবে যখন, তখন দৃঢ়সংকল্প হইও, ৮. এবং নিজ পরওয়ারদেগারের প্রতি মনোনিবেশ করিও (সূত্র : কুরআন শরিফ আমপারা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮২, ভূমিকা: সৈয়দ আলী আহসান)।
দুই অনুবাদের মধ্যে সময়ের ব্যবধান ৩৭ বছর। এর মধ্যে পাকিস্তান আন্দোলন এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হলো, মুসলমানদের সাংস্কৃতিক পুনর্জন্ম হলো নজরুল, আব্বাসউদ্দীন, ফররুখ আহমদদের হাত ধরে। ব্রিটিশ শাসনামলে কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে হিন্দু, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের হাতে সুলতানি আমলের উদীয়মান বাংলা ভাষাকে সাংস্কৃত্যায়নের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। ফলস্বরূপ, প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে ব্যবহৃত বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শব্দের আধিক্য প্রতিষ্ঠা পায়, যা দেখা যাচ্ছে ১৯২২ সালের অনুবাদে। মুসলমানদের জন্য আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হলে বাঙালি মুসলমান তার ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় হিন্দু পরিচয়ের ধারক সংস্কৃত শব্দের বদলে বাংলা ভাষায় ইসলামি পরিচয়ের ধারক আরবি ও ফারসি শব্দ নিয়ে আসা শুরু করে। এরই ফলে দেখা যায়, একই অনুবাদক কুরানের একই সুরার আয়াতগুলো বাংলায় অনুবাদ করতে গিয়ে সংকটকে মুশকিলে, স্বাচ্ছন্দ্যকে আছানিতে আর প্রভুকে পরওয়ারদেগারে বদলে ফেলেছেন।
অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি, নামের পরিবর্তন আপাতদৃষ্টিতে ব্যক্তির ঐচ্ছিক একটা বিষয় হলেও এর মধ্য দিয়ে সামাজিক বাস্তবতাই প্রকাশিত হয়। কুষ্টিয়ার বৃষ্টি খাতুনের ঢাকায় এসে ইসলামি নাম পরিবর্তন করে অভিশ্রুতি শাস্ত্রী নাম নেওয়া কিংবা ফেনীর মৌলভী মোহাম্মদ নোমান বাবলুর ঢাকায় এসে স্বকৃত নোমান নাম নেওয়া, মোহাম্মদ সাজ্জাদুর রহমানের বামপন্থি আন্দোলনে যুক্ত হয়ে রাখাল রাহা নাম গ্রহণ করা কিংবা আলী যাকেরের কন্যার শ্রেয়া সর্বজয়া নামকরণ-এসবই বর্তমান বাংলাদেশে, সুনির্দিষ্ট করে ঢাকার সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে ইসলামি পরিচয়কে ত্যাগ করে একটা সেক্যুলার পরিচয় ধারণ করার আকাঙ্ক্ষাকেই প্রকাশ করে। ব্যক্তি ও পরিবারের মধ্যে নামকরণ নিয়ে এ প্রবণতা শুধু বাংলাদেশেই নয়, বরং বিশ্বের অধিকাংশ সমাজেই লক্ষণীয়, যেখানে ব্যক্তি ও পরিবার সমাজের মূলধারার সঙ্গে নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে একটা গ্রহণযোগ্য পরিচয় ধারণ করে।
বাংলাদেশের চলমান সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতায় ইসলামি পরিচয়ের বদলে সেক্যুলার পরিচয় মূলধারা হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। এর ফলে বাঙালি মুসলমানের সন্তানরা নিজেদের মা-বাবার দেওয়া ইসলামি নাম থেকে আরবি/ফারসি শব্দ বাদ দিয়ে সেখানে সংস্কৃত বা অনৈসলামিক শব্দের সমাহারে নতুন নাম ধারণ করে, যার মাধ্যমে তারা ইসলাম থেকে নিজেদের দূরত্বের ইশারা করে। কিন্তু কেন? কারণ, বাংলাদেশে ইসলাম নয়, বরং মূলধারা হয়ে উঠেছে ইসলামের বিপরীতে সেক্যুলার বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, যাকে আবার ডিফাইন করা হয় ইসলামের বিপরীতে। ফলে এ মূলধারায় হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টানসহ আর সব ধরনের ধর্ম ও সম্প্রদায়গোষ্ঠী অন্তর্ভুক্ত হতে পারে নিজ নিজ ধর্ম ও সম্প্রদায়গত পরিচয় নিয়েই; কিন্তু বাঙালি মুসলমানকে তার ইসলামি পরিচয় পরিত্যাগ করেই কেবল এ মূলধারায় আসতে হয়।
ড. হাসান মাহমুদ : সহকারী অধ্যাপক, নর্থওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কাতার



-67fcf62bea4b0.png)





-67fceff4e95fc.png)
