
প্রিন্ট: ০৫ এপ্রিল ২০২৫, ০৪:২৬ এএম
গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিচর্চার অন্যতম উপায় নির্বাচন
ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী
প্রকাশ: ০২ জানুয়ারি ২০২৫, ১২:০০ এএম
প্রিন্ট সংস্করণ
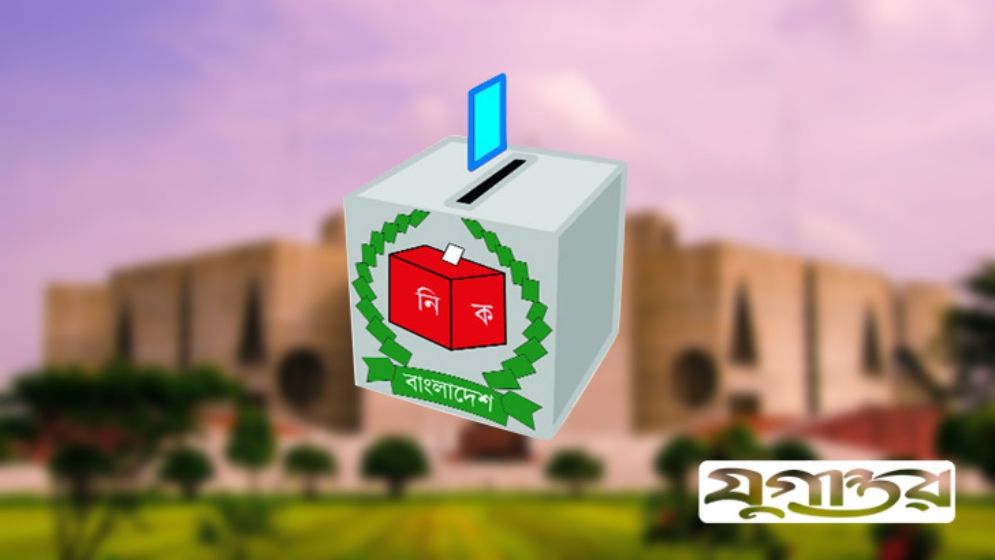
আরও পড়ুন
অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সম্ভাব্য সময় ঘোষিত হয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনে অংশগ্রহণে প্রস্তুতির জন্য পর্যাপ্ত সময় পাচ্ছে। জনকল্যাণে সব ধরনের অসংযত আচার-আচরণ, জনগণকে ভয়ভীতি প্রদর্শন, দখল-চাঁদাবাজি পরিহার করে নেতারা দলকে সুসংহত করার সতর্কবার্তা দিয়েছেন। জনগণ অধির আগ্রহে ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে পছন্দের প্রার্থীকে নির্বাচিত করার প্রতীক্ষায় আছে। সংবিধান অনুযায়ী সুচারুরূপে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের প্রক্রিয়া দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির অংশ। নির্বাচন কমিশন যথাযথ নিরপেক্ষতা বজায় রেখে সুষ্ঠু নির্বাচন উপহার দেবে, এটিই কাম্য। কমিশনের ক্ষমতাই নির্বাচন পরিচালনার অন্যতম নিয়ামক। নির্বাচনের তফশিল ঘোষণার পর থেকে সরকারের রুটিন দায়িত্ব পালন ছাড়া নীতিগত কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন কাঙ্ক্ষিত নয়। বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশেই যথাযথ আইনি কাঠামোয় নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং জনপ্রতিনিধি নির্বাচন, সরকার গঠন একটি স্বাভাবিক পরিক্রমা। জনগণের সমর্থনের প্রতি পূর্ণাঙ্গ আস্থার ভিত্তিতে ঘোষিত রায়ে ফলাফল গ্রহণ এবং তদানুসারে রাষ্ট্র পরিচালনায় পরিপূর্ণ সহযোগিতা প্রদান প্রত্যেক নাগরিকের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্য।
সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে পরবর্তী সরকার গঠনের কার্যক্রম গ্রহণ করা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। মূলত প্রাগ্রসর সমাজের দৃষ্টান্ত হিসাবে মৌলিক অধিকার সুরক্ষায় প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার প্রয়োগ সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে যে কোনো ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ নির্বাচন কমিশনের ওপর বর্তায়। যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীসহ রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণও এক্ষেত্রে প্রযোজ্য। দেশের জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটিয়ে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাঝেই নির্বাচন কমিশনের সাফল্য। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের যথার্থ ধারণ ও পরিচর্যা আধুনিক রাষ্ট্রে উন্নতির অন্যতম উপাদান। যথাযথ প্রক্রিয়ায় অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং জনপ্রতিনিধি দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রগতিশীল রাজনৈতিক ধারার পরিচায়ক। মূলত সব দল-মতের সম্মিলিত অংশগ্রহণ ও সমর্থনে নেতৃত্ব বাছাই এবং সঠিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে সরকার গঠন ও রাষ্ট্র পরিচালনা গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করে।
গণতন্ত্র হলো আধুনিক বিশ্বের সর্বাপেক্ষা সমাদৃত শাসনব্যবস্থা, যা বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে শুরু করে বিশ্বের সর্বত্রই জনপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হয়েছিল। বিপুল পরিবর্তন-পরিমার্জনের মধ্য দিয়ে বর্তমানেও গণতন্ত্র সমধিক জনপ্রিয় শাসনব্যবস্থার রূপ পরিগ্রহ করে চলছে। গণতন্ত্র যে কোনো সমাজে পরিশুদ্ধ পন্থায় সমগ্র জনগোষ্ঠীর কল্যাণ সাধনে রাষ্ট্র বা সরকারকে পরিচালিত করে। একনায়কতন্ত্র বা রাজতন্ত্রের বিপরীতে জনগণের শাসন বা শাসননীতির ইচ্ছানুসারে পরিচালিত রাষ্ট্রব্যবস্থায় গণতন্ত্রের সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটে। গণতন্ত্র সরকার পরিচালনা ও নীতিনির্ধারণে জনগণের অংশগ্রহণ, মানুষের স্বাধীনতা-অধিকার নিশ্চিতকরণ, রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠাসহ সরকারকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনে সহায়তা করে। প্রকৃতপক্ষে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিচর্চার অন্যতম উপায় হলো নির্বাচন অনুষ্ঠান।
নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দেশের সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ব্যাপক প্রস্তুতি সত্ত্বেও জনমনে সহিংসতা-নাশকতার আশঙ্কা থেকেই যায়। উজ্জীবিত কর্মীদের উদ্দেশে দলীয় নেতাদের দেওয়া উত্তেজক বক্তৃতা-বিবৃতিতে নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়ার পাশাপাশি রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমান্বয়ে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। কাজেই নির্বাচন ঘিরে কোনো ধরনের হুমকি-ধমকি এবং অসংযত আচরণ কাম্য হতে পারে না। যে কোনো দলের অস্বাভাবিক পরিবেশ সৃষ্টির পাঁয়তারা জনগণ সহজেই অনুধাবন করতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সচল রাখতে হলে সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের কোনো বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে রাজনীতির সব পক্ষকেই দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হবে।
স্বাধীনতার পর থেকে অদ্যাবধি বিভিন্ন দল কর্তৃক সরকার পরিচালনা এবং নানা পটপরিবর্তনের মধ্য দিয়ে দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছে। এটি প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, রাষ্ট্র শাসনে দলগুলো যথার্থ অর্থে আদর্শিক ঐতিহ্য তৈরি করতে পারেনি। জাতীয় আদর্শের প্রকৃত ভিত রচনাতেও তারা কতটুকু সফল ছিল, তা পর্যালোচনার দাবি রাখে। একটি গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠার মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণ। ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের জাঁতাকলে নিষ্পেষিত ছিল এতদঞ্চলের মানুষ ও মানুষের জীবনপ্রবাহ। আর্থসামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রচণ্ড অবহেলার শিকার হয়েছিল এ পূর্বাঞ্চল। দেশ বিভাগের পর থেকেই, বিশেষ করে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে প্রজ্জ্বলিত হয় বাঙালির স্বজাত্যবোধের স্ফুলিঙ্গ।
স্বাধিকারের দীর্ঘ সংগ্রাম বাঙালিকে স্বাধীন সত্তার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় উজ্জীবিত করে। এরই ফল ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ। অসংখ্য প্রাণ বিসর্জন ও অজস্র জননী-জায়া-কন্যার ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হয় এ স্বাধীন মাতৃভূমি। প্রায় এক কোটি মানুষের শরণার্থীর জীবনযাপনের অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশা কখনো ভোলার নয়। প্রতিমুহূর্তে হায়েনাদের আক্রমণে দেশে থাকা মানুষের আর্তনাদে বাতাস হয়ে উঠেছিল অসম্ভব ভারী। এত বিসর্জনের পরও অর্জিত স্বাধীনতাকে অর্থবহ করার প্রচেষ্টা কেন ব্যর্থতার কালো মেঘে ঢাকা পড়ল, তারও বিচার-বিশ্লেষণ প্রয়োজন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে এর ভাঙনের মূলে যে কারণগুলো বিদ্যমান ছিল তা হচ্ছে, প্রধানত গণতন্ত্রবিবর্জিত কেন্দ্রীয় একদেশদর্শী শাসনব্যবস্থা এবং পূর্ব বাংলার প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণ, এ অঞ্চলের ভাষার প্রতি অগণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সর্বোপরি শিক্ষিত-সংস্কৃতিমান মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশকে রুদ্ধ করার অপচেষ্টা।
১৯৬১ সালের জরিপ অনুযায়ী এ অঞ্চলের জনসংখ্যা ছিল পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৬ শতাংশ, এ অঞ্চলে রপ্তানি আয় ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের ৩০ থেকে ৫০ শতাংশের বিপরীতে ৫০-৭০ শতাংশ। আমদানি ব্যয় ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের ৫০-৭০ শতাংশের বিপরীতে ২৫-৩০ শতাংশ। বেসামরিক চাকরির ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের ৮০-৮৪ শতাংশের বিপরীতে ১৬-২০ শতাংশ। সামরিক চাকরির ক্ষেত্রে ৯০ শতাংশের বিপরীতে ১০ শতাংশ। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে পুঁজি বিনিয়োগ ২.১ শতাংশের বিপরীতে ০.৬ শতাংশ। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে মঞ্জুরি ও আর্থিক সাহায্যের ক্ষেত্রে ১০.২ শতাংশের বিপরীতে ১.৪ শতাংশ। বৈদেশিক সাহায্য বিতরণের ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের ৭০-৮০ শতাংশের বিপরীতে ২০-৩০ শতাংশ। শিক্ষা অনুদানের ক্ষেত্রে ১.৫ শতাংশের বিপরীতে ০.২ শতাংশ। সামরিক ব্যয়ের ক্ষেত্রে ৪.৭ শতাংশের বিপরীতে ০.১ শতাংশ। ১ম ও ২য় পাঁচশালা পরিকল্পনায় অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের ৬৮ শতাংশের বিপরীতে ৩২ শতাংশ, ৩য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৬৮ শতাংশের বিপরীতে ৩৬ শতাংশ।
মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের ৪১৯ টাকার বিপরীতে ১৯৬৫-৬৬ সালে ছিল ২৮৫ টাকা এবং ১৯৬৮-৬৯ সালে ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের ৪৭৩ টাকার বিপরীতে ২৯১ টাকা। ১৯৪৯-৫০ সালে প্রাদেশিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে পূর্ব অঞ্চলে ছিল ১২৩৭.৪ কোটি টাকা এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল তা ১২০৯.১ কোটি টাকা, যা ১৯৬৯-৭০ সালে গিয়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ২২৭১.৩ কোটি এবং ৩১৫৬.৩ কোটি টাকায়। একই সময় মাথাপিছু উৎপাদনের ক্ষেত্রে যেটি ছিল পূর্ব পাকিস্তানে ২৯৩ কোটি এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ৩৪২ কোটি, তা গিয়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩২১ কোটি এবং ৫৪৬ কোটি টাকায়। ১৯৫০-৭০, দুই দশকে ৬৫০ কোটি বিদেশি ঋণের বিপরীতে পূর্ব পাকিস্তানে খরচ করা হয় ১৯৪.২ কোটি ডলার এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ৪৫৫.৮ কোটি ডলার।
তুলনামূলক বিশ্লেষণে বোঝা যায় কীভাবে আর্থসামাজিক বৈষম্য সৃষ্টির মাধ্যমে এ জাতিকে নিষ্পেষিত করা হয়েছিল। শোষণ-শাসনে বাঙালিদের বাকস্বাধীনতা থেকে শুরু করে সর্বত্রই রুদ্ধ করার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতি ধীরে ধীরে ঐক্যবদ্ধ হয়। একমাত্র ঐক্যবদ্ধতার শক্তিই জাতিকে মহান মুক্তিযুদ্ধের মতো চ্যালেঞ্জ গ্রহণে সাহস জুগিয়েছে। নানা ঘাত-প্রতিঘাতে বাঙালির সচেতনতা প্রতিবাদী রূপ পরিগ্রহ করে। ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন ইস্যুতে আন্দোলনের শক্তি পুঞ্জীভূত হয়। ক্ষোভের মাত্রা অপরিমেয় পর্যায়ে পৌঁছে গেলে প্রায় সব ক্ষেত্রেই বাঙালির চেতনাবোধ নবতর অধ্যায় রচনা করে। এ পথ বেয়েই আসে সত্তরের নির্বাচনের ফলাফল এবং একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ।
একটি প্রচলিত প্রবাদ হচ্ছে, স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে তা রক্ষা করা বহুগুণ কঠিন। রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় দেশের জনগণ ও সেনাবাহিনীসহ সবাই ঐক্যবদ্ধ। নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণে জুলাই ’২৪-এর শহিদদের সর্বোচ্চ ত্যাগকে প্রাধান্য দিতে হবে।
ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী : শিক্ষাবিদ, সমাজ-অপরাধবিজ্ঞানী







-67f0232f19e91.jpg)
-67f020b1bbbaf.jpg)

