সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নতুন বিশ্বের জন্ম হচ্ছে
ড. ইমতিয়াজ আহমেদ
প্রকাশ: ০১ জানুয়ারি ২০২৫, ১২:০০ এএম
প্রিন্ট সংস্করণ
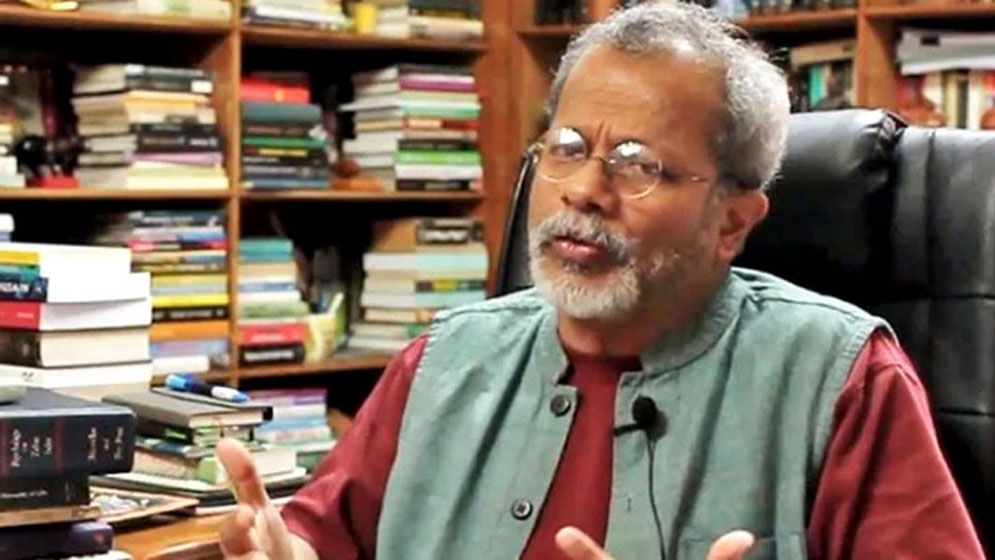
ড. ইমতিয়াজ আহমেদ। ফাইল ছবি
বিশ্ব বলতে গেলে একটা বহুমাত্রিক কাঠামোর দিকে যাত্রা শুরু করেছে। কোনো পরিবর্তন যখন হয়, বিশেষ করে বৈশ্বিক পরিবর্তন, সেটা খুব সহজে হয় না। বিভিন্ন বাধা, নানা ধরনের সমস্যা তৈরি হয়। ইতালির দার্শনিক আন্তোনিও গ্রামসির একটা সুন্দর কথা আছে : The old world is dying and the new world struggles to be born. যার অর্থ দাঁড়ায়-পুরোনো বিশ্বের মৃত্যু ঘটছে এবং নতুন বিশ্ব জন্মের জন্য সংগ্রাম করছে। এখন দানবের সময়, তার মানে যখন পুরোনো বিশ্বের মৃত্যুর ক্ষণ ঘনিয়ে আসে, সে সময়টা একটা দানবের সময় হয়, যার কিছু নমুনা আমরা ২০২৪ সালে দেখতে পেয়েছি। বিশেষ করে আমরা যদি ইউক্রেনের যুদ্ধ দেখি, ফিলিস্তিনের অর্থাৎ গাজার যুদ্ধ দেখি, তাহলেই এ দানবের বিষয়টা অনেকটাই বোঝা যায়।
ইউক্রেনের যুদ্ধে আমরা দেখেছি, যদিও তা মূলত শুরু হয়েছিল ন্যাটোর সম্প্রসারণকে কেন্দ্র করে, সেখানে একটা নির্বাচিত সরকারকে বলা যেতে পারে জনগণের ক্যুয়ের মাধ্যমে সরানো হয়েছে। এরপর আমরা দেখলাম, জেলেনস্কি নির্বাচিত হয়ে এলেন বটে; কিন্তু যে প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছিলেন তখন, সেটা তিনি মানলেন না, বরং ন্যাটোর সম্প্রসারণের দিকেই তিনি ঝুঁকে পড়লেন। অন্যদিকে রাশিয়ার সব সময়ই ইউক্রেনের ব্যাপারে একটা চিন্তা থাকে। কারণ অতীতে বড় আকারে তিন-তিনটা যুদ্ধ রাশিয়ার ওপর হয়েছে এ ইউক্রেনের মাধ্যমেই। একটা হলো নেপোলিয়নের যুদ্ধ, তারপর প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। তিনবারই যে যুদ্ধ পশ্চিম থেকে একেবারে মস্কো পর্যন্ত চলে গিয়েছিল, সেখানে ইউক্রেনের একটা বড় ভূমিকা ছিল। এ কারণে ইউক্রেন যেন নিউট্রাল (নিরপেক্ষ) থাকে, সেটা সব সময়ই রাশিয়ার পলিসির মধ্যে থাকে। অর্থাৎ যেটাকে মস্কোর রেডলাইন বলা হতো, তা যেন কখনো অতিক্রম না করা হয়। কিন্তু দেখা গেল, পশ্চিমা বিশ্ব, বিশেষ করে আমেরিকা ন্যাটোর সম্প্রসারণটি রাশিয়ার দিকেই ঘটাতে চাইল। কাজেই সেটা বড় আকারেই বাধার মুখে পড়ল এবং ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ বেধে যেতে আমরা দেখলাম, যা এখনো চলছে। এতে প্রচুর ইউক্রেনবাসী বাস্তুচ্যুত হয়েছেন, দেশটা তছনছ হয়ে গেছে বলতে গেলে। আমেরিকা বিপুল অঙ্কের ডলার ঢেলেছে এ ইউক্রেনে, যে ডলারগুলো কোনো না কোনো সময় ইউক্রেনকে ফেরত দিতে হবে। এটা কিন্তু বিনা পয়সার যুদ্ধ নয়, সবই ঋণ হিসাবে দেওয়া এবং তাতে আমেরিকার সমর শিল্পের একটা বড় লাভ হয়েছে। এখন এ যুদ্ধটা কীভাবে থামবে, সেটা দেখার বিষয়। বর্তমানে যুদ্ধটা থামার একটা সম্ভাবনা অবশ্য দেখা যাচ্ছে, সেটা আমেরিকায় রিপাবলিকান পার্টি বা ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিজয়ের কারণে। কারণ তিনি প্রথম থেকেই এ যুদ্ধের বিপক্ষে ছিলেন। তিনি যুদ্ধটা কীভাবে থামাবেন, সেটাই এখন দেখার বিষয়।
দানবের দ্বিতীয় যে লক্ষণ আমরা দেখলাম, তা হলো গাজার যুদ্ধ, যেখানে এরই মধ্যে ৪৫ হাজারের বেশি মানুষ মারা গেছেন। নিহতদের মধ্যে নারী ও শিশুর সংখ্যা প্রচুর। যেসব সংস্থা বিশ্বব্যাপী গণহত্যা নিয়ে কাজ করে, তারা এটাকে জেনোসাইডই বলছেন। জাতিসংঘের বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম, এমনকি আইসিজেও বলছে, গাজায় এক ধরনের গণহত্যা সংঘটিত হচ্ছে। তো পশ্চিমা বিশ্বে যে কাঠামোটা তৈরি হয়েছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর, বিশেষ করে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারকে সামনে নিয়ে, সেটা গাজাতে এসে বলতে গেলে একেবারেই ভেঙে গেল ইসরাইলকে সাহায্য করার কারণে। আমেরিকাই শুধু নয়-যুক্তরাজ্য, জার্মানি, ফ্রান্স সবাই মিলে ইসরাইলকে অস্ত্র-অর্থ দিয়ে সাহায্য করে যাচ্ছে। গণহত্যার পেছনে তাদেরও একটা ভূমিকা আছে। সেটার একটা বিশাল বিরোধী অবস্থানও আমরা দেখতে পেয়েছি। খোদ আমেরিকার জনগণই এর প্রতিবাদে বড় আকারে রাস্তায় নেমেছেন, ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও প্রতিবাদ হয়েছে, এমনকি ইহুদিরাও গাজায় গণহত্যার প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছে এবং বলেছে, আমার নামে যেন এ যুদ্ধ না করা হয়। বলা হচ্ছে, গত বছরের অক্টোবরে হামাসের পক্ষ থেকে যে আক্রমণটা করা হয়েছিল, সেটার কারণেই এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু ফিলিস্তিনের ইতিহাস দেখলেই বোঝা যায়, যুদ্ধটা সেই ১৯৪৮ সাল থেকেই চলে আসছে এবং ইহুদিরা রীতিমতো একটা ঔপনিবেশিক কাঠামো সেখানে করার কারণেই হামাসের দিক থেকে বা ফিলিস্তিনিদের দিক থেকে এ রকম একটা প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। যদিও হামাসের আক্রমণেরও সমালোচনা করা যেতে পারে; কিন্তু আমেরিকা ও ইউরোপের কয়েকটা দেশের সমর্থন নিয়ে এর পালটা যে জবাব ইসরাইল দিয়েছে, সেটা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্যতা পায়নি, বরং একটা বড় ধরনের মতৈক্য তৈরি হয়েছে যে, সেখানে গণহত্যা চলছে।
সব মিলিয়ে বোঝা যাচ্ছে, পৃথিবী একটা মাল্টিপোলার বা বহুমেরুকেন্দ্রের দিকে যাচ্ছে। পশ্চিমা বিশ্ব আগে যেভাবে আধিপত্য ধরে রাখতে পারত, সেটা এখন আর সম্ভব হচ্ছে না। যেমন, ইউক্রেনের ব্যাপারে তাদের চিন্তাভাবনা ছিল, যুদ্ধের মাধ্যমেই রাশিয়াকে জব্দ কিংবা কাবু করা যাবে; কিন্তু সেটা তো হয়ইনি, বরং রাশিয়া আরও শক্তিশালী হয়ে গেছে। প্রথমদিকে আমেরিকা হয়তো চিন্তা করেছিল পুরো পৃথিবী তার সঙ্গে থাকবে; কিন্তু আমরা দেখলাম, সেখানে বড় ধরনের একটা সম্পর্ক রাশিয়া স্থাপন করতে পেরেছে চীন ও ভারতের সঙ্গে। এ তিনটা দেশ যখন একসঙ্গে থাকল ইউক্রেন যুদ্ধের সময়, তখন বোঝা যাচ্ছে, পৃথিবীটাও আর ইউনিপোলার বা একমেরুকেন্দ্রিক থাকল না, যেটা সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাঙার পর বলতে গেলে হয়ে গিয়েছিল। সেটা এখন মাল্টিপোলারের দিকে চলে গেল।
পৃথিবীর এ নতুন কাঠামোটা এখন কোনদিকে যাবে, সেটা বলা মুশকিল। তবে এরই মধ্যে আমরা কতকগুলো পরিবর্তন দেখলাম। যেমন, ইরানে ক্ষমতার একটা নতুন কাঠামো তৈরি হয়েছে, বিশেষ করে ইসরাইলের বিরুদ্ধে। ইসরাইল যদিও বলতে গেলে শুরু থেকেই হামাস, হিজবুল্লাহ ও হুতির সঙ্গে লড়াই করছিল; কিন্তু দেখা গেল ইরানকেও সেখানে সরাসরি, বিশেষ করে ড্রোন প্রযুক্তির মাধ্যমে একটা যুদ্ধ দুই দেশের মধ্যেও হতে দেখলাম। বোঝাই গেল, ইরানও আগের অবস্থানে নেই। এ দেশটিও একটা শক্তিশালী কাঠামো তৈরি করতে পেরেছে।
এমন পরিস্থিতিতে পৃথিবী কোনদিকে যাবে, তা বলা মুশকিল। কারণ এরই মধ্যে আবার সিরিয়াতেও আমরা দেখলাম ক্ষমতার পালাবদল হতে। যদিও এর আবার দুটো মত আছে। কেউ মনে করছে, এতে পশ্চিমাদের ও ইসরাইলের লাভ হয়েছে। আবার কেউ মনে করছে, তা নয়, বরং ভবিষ্যতে এতে ইসরাইলের লোকসানই হবে। কারণ, আসাদের যে সিরিয়া ছিল, সেটা আসলে ইসরাইলকেই বলতে গেলে সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছিল পরোক্ষভাবে। যদিও তারা দেখাচ্ছিল যে, তারা ইরান কিংবা হিজবুল্লাহর সঙ্গে; কিন্তু বড় আকারে সিরিয়ার আসাদ সরকার ইসরাইলের বিরুদ্ধে কোনো ভূমিকা রাখেনি। এখন এ পরিবর্তনটা হয়তো আরও পরিষ্কার হবে, কারণ আসাদের যখন অপরসারণ হলো, দেখা গেল ফিলিস্তিনিরাও বিজয় উল্লাস করল। কারণ তারাও ভালো করে জানে যে, আসাদের সিরিয়া তাদের পক্ষে তেমনভাবে ছিল না, মানে সেই সরকার একটা দ্বৈত ভূমিকা পালন করছিল।
এই যে পুরোনো পৃথিবী চলে যাচ্ছে এবং নতুন ব্যবস্থা আসতে চলেছে, এর মধ্যে আমেরিকার নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিজয় দেখলাম। যেহেতু আমেরিকা পরাশক্তি, সেহেতু দেশটির ক্ষমতার পালাবদল বিশ্বে কোনো না কোনোভাবে প্রভাব ফেলে। ডোনাল্ড ট্রাম্প ও রিপাবলিকান পার্টি যে ম্যান্ডেটটা পেয়েছে, সে ম্যান্ডেটটা বিশাল। গত ১২৮ বছরে আমেরিকার কোনো প্রেসিডেন্ট এত বড় ম্যান্ডেট পায়নি। তারা শুধু যে ইলেক্টোরাল ভোটে জিতেছে, তা নয়। পপুলার ভোটও তারা পেয়েছে; হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভ, এমনকি সিনেটেও দলটি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে। জুডিশিয়ারিতেও দেখা গেছে রিপাবলিকানদের আধিপত্য। এরপর যেসব সুইং স্টেট রয়েছে, যে রাজ্যগুলোর নির্বাচনি ফলাফলে একটা ব্যালেন্স অতীতে থাকতে আমরা দেখেছি, সেখানেও দেখা গেল সবই রিপাবলিকানদের হয়ে গেল। তো এই যে বিশাল ম্যান্ডেট ১২৮ বছর পর পেলের একজন প্রেসিডেন্ট, এতে বোঝাই যাচ্ছে, আমেরিকার জনগণ বড় আকারে একটা পরিবর্তন চাইছে। মূলত তারা শান্তিই চাইছে, তারাও এ যুদ্ধের মধ্যে থাকতে চাইছে না। কারণ নির্বাচনি প্রচারণার সময় ট্রাম্প বড় আকারেই বিশেষ করে ইউক্রেন যুদ্ধের ব্যাপারে তার অবস্থানটা খুবই স্পষ্ট করেছেন। যদিও গাজার যুদ্ধের ব্যাপারে তার অবস্থান এখনো বোঝা মুশকিল, কিন্তু ইউক্রেনে যুদ্ধ বন্ধে তার অবস্থান বেশ স্পষ্ট। অবশ্য মার্কিন নির্বাচনে গাজায় যে গণহত্যা চলছে, সেটা কিন্তু প্রভাব ফেলেছে দুভাবে। একটা হলো, যে প্রযুক্তি এসেছে, বিশেষ করে টিকটকস প্রযুক্তির মাধ্যমে আমেরিকাসহ গোটা পৃথিবী প্রথমবারের মতো যুদ্ধের নামে একটা জেনোসাইড সরাসরি দেখতে পেয়েছে। পৃথিবীর মানুষ এর আগে কখনো এমন জেনোসাইড সরাসরি দেখতে পারেনি। এটা আমেরিকার তরুণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে একটা বিশাল প্রভাব ফেলেছে এবং যে সুইং স্টেটগুলোর কথা বলেছিলাম, দেশটির নির্বাচনে যারা কম বয়সি ভোটার, তারা হয় ডেমোক্রেটিক পার্টিকে ভোট দেয়নি বা ভোটদান থেকে বিরত ছিল, নয়তো তারা সরাসরি রিপাবলিকানদের ভোট দিয়েছে। যেটা আগে এত বড় আকারে দেখা যায়নি। এবং আমরা এটাও দেখেছি, দেশটির শ্রমিক শ্রেণিও বড় আকারে রিপাবলিকানদের সমর্থন করেছে। এটাও একটা বড় পরিবর্তন। কারণ এই শ্রমিক শ্রেণির অনেকেই মূলত ডেমোক্রেটিক পার্টিকেই সমর্থন দিয়ে আসত। এখন দেখা যাচ্ছে, ডেমোক্রেটিক পার্টির বড় আকারে একটা এলিট পার্টিতে রূপান্তর ঘটেছে। আমরা দেখেছি, আমেরিকার বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, যেগুলোতে এলিট শ্রেণির সন্তানরাও পড়াশোনা করে, তারা যুদ্ধের নামে গাজায় গণহত্যা বন্ধের দাবিতে রাস্তায় নেমেছিল। এ তরুণরা যেভাবে ডেমোক্রেটিক পার্টির সমালোচনা করে যুদ্ধের বিরুদ্ধে জোরালো ভূমিকা রেখেছিল, তাতে বোঝা গিয়েছিল, জনগণ ম্যান্ডেটটা ডোনাল্ড ট্রাম্পকে দিয়েছে মূলত শান্তির আকাঙ্ক্ষায়। এখন দেখা দরকার, এই ম্যান্ডেট ট্রাম্প কাজে লাগাতে পারেন কিনা। শপথের পর প্রথম দুবছর বলতে গেলে পুরো ক্ষমতাই তার কাছে থাকবে (মিড টার্ম নির্বাচনের আগে পর্যন্ত), এখন প্রথম দুবছরে শান্তির যে ম্যান্ডেটটা আমেরিকার জনগণ দিয়েছে, সেটা তিনি বাস্তবায়ন করতে পারবেন কিনা। সেটির জন্য হয়তো আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। তবে যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে, যদিও একটা পুরোনো পৃথিবী চলে যাচ্ছে, নতুনটা এখনো সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, তারপরও আমরা আশা দেখতে পারছি। যেহেতু, আমেরিকার জনগণও জেগে উঠেছে এবং সে কারণেই তারা রিপাবলিকান পার্টিকে সমর্থন দিচ্ছে যুদ্ধের বিরুদ্ধে। এখন কতখানি শান্তি আসবে পৃথিবীতে, সেটার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।
ড. ইমতিয়াজ আহমেদ : শিক্ষাবিদ ও আন্তর্জাতিক বিশ্লেষক

