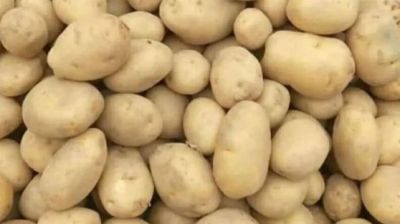প্রিন্ট: ০৩ এপ্রিল ২০২৫, ০২:৫৩ পিএম
আলুর দাম নিয়ন্ত্রণে থাকছে না কেন
ড. জাহাঙ্গীর আলম
প্রকাশ: ২১ ডিসেম্বর ২০২৪, ১২:০০ এএম
প্রিন্ট সংস্করণ

ছবি: সংগৃহীত
আলুর দাম অনেক বেড়েছে। এখন কৃষকদের উৎপাদিত আগাম জাতের নতুন আলু সীমিত আকারে উঠছে বাজারে। আমদানির মাধ্যমেও আলু আসছে বিদেশ থেকে। তবু এর দাম চড়া। ঢাকার খুচরা বাজারে গ্রানুলা জাতের ভালো গোল আলু বিক্রি হচ্ছে প্রতি কেজি ৭০ টাকা। ডায়মন্ড জাতের ডিম্বাকার আলু বিক্রি হচ্ছে ৭৫ টাকায়। কার্ডিনাল জাতের লালচে আলুর দাম প্রতি কেজি ৮০ টাকা। নতুন আলুর দাম প্রতি কেজি ১০০ টাকা। দেড় মাস আগেও আলুর দাম ছিল প্রতি কেজি কমবেশি ৫০-৬০ টাকা। এর উৎপাদন মৌসুম শেষ হয়েছে প্রায় ৯ মাস আগে। এখন শীতকাল। মূল্য কমেছে বিভিন্ন শাকসবজির। কিন্তু আলুর দাম সেভাবে কমছে না। প্রায়োজন অনুপাতে কোল্ড স্টোরেজ থেকে আলু খালাস করা হচ্ছে না। এখনো আলু উৎপাদনের ভরা মৌসুম আসতে আরও প্রায় মাসখানেক বাকি। তাই বাজারে সরবরাহ সংকট অনুভূত হচ্ছে। ফলে ভোক্তা পর্যায়ে আলুর দাম বেশি। এক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদেরও কারসাজি আছে। সরকারের কাছে আলুর মজুত নেই। কোল্ড স্টোরেজও নেই। ফলে বাজারে হস্তক্ষেপ করা যাচ্ছে না। এ অবস্থায় শুধু কথা বলে আর বাজার পরিদর্শন করে পণ্যমূল্য হ্রাস করা কঠিন।
আলু বাংলাদেশের তৃতীয় প্রধান খাদ্যশস্য। ২০ বছর আগে এর মোট উৎপাদন ছিল ১৪.৪ লাখ টন। তখন মাত্র ১.৩ লাখ হেক্টরে এর উৎপাদন হতো। বর্তমানে (২০২৩-২৪) এর উৎপাদন প্রায় ১০৬ লাখ টন। আবাদি এলাকা প্রায় ১১২৬ হাজার একর। গত ২০ বছরে আলুর উৎপাদন বছরে গড়ে প্রায় ৭ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। আলু চাষের আওতাধীন জমির পরিমাণ বৃদ্ধি এবং হেক্টরপ্রতি উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে আলুর মোট উৎপাদন। সেই সঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছে আলুর অভ্যন্তরীণ চাহিদা। দেশের ভেতর আলু প্রক্রিয়াজাতকরণ, হিমায়িত সংরক্ষণ, ব্যবহারের বৈচিত্র্যকরণ এবং বিদেশে রপ্তানির বাজার সম্প্রসারণ ইত্যাদির অগ্রগতি আলুর বাজারমূল্য কিছুটা বাড়িয়েছে। তাছাড়া কৃষি উপকরণের মূল্যবৃদ্ধির ফলে আলুর উৎপাদন খরচ বেড়েছে। তেল ও বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় বেড়েছে আলু সংরক্ষণ ও পরিবহণ খরচ। অন্যান্য খাদ্যশস্য যেমন-চাল, গম ইত্যাদির জন্য ফসল উত্তোলনের মৌসুমে একটা সংগ্রহমূল্য নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। সেই নির্ধারিত মূল্যে সরকারিভাবে সংগ্রহ করা হয় ৫ থেকে ৬ শতাংশ খাদ্যশস্য। তাতে উৎপাদন মৌসুমে বাজারে কিছুটা চাঙ্গাভাব বিরাজ করে ওই খাদ্যশস্যের। পরে দাম বেড়ে গেলে খোলাবাজারে অপেক্ষাকৃত কম দামে খাদ্যশস্য বিক্রি করা হয় সরকারি সংরক্ষণাগার থেকে। কিন্তু আলুর ক্ষেত্রে তেমন কোনো সরকারি হস্তক্ষেপ নেই। মৌসুম শুরুতে দাম থাকে কম। পরে বেড়ে যায়। তা নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। এবার আলুর দাম বেশি থাকায় এর আবাদ বাড়ছে। উৎপাদনও বৃদ্ধি পাবে। এ অবস্থায় নিষ্ফল মৌসুমে বাজারে আলুর সরবরাহ ও মূল্য স্থিতিশীল রাখার জন্য বাজারে হস্তক্ষেপের উদ্দেশ্যে সরকারিভাবে ৫-৭ লাখ টন আলু সংগ্রহ ও মজুত করা প্রয়োজন।
আলু পচনশীল শস্য বিধায় ব্যবসায়ীরা ভবিষ্যতে ভালো দাম পাওয়ার আশায় তা সংরক্ষণ করে রাখেন হিমাগারে। বাংলাদেশে বর্তমানে মোট হিমাগারের সংখ্যা প্রায় ৪০০। এগুলোর ধারণক্ষমতা প্রায় ৬০ লাখ টন। কৃষক পর্যায়ে চিরায়ত পদ্ধতিতেও কিছু আলু ও বীজ সংরক্ষণ করা হয়। কিন্তু তা যথাযথ নয়। তাই চিরায়ত মজুতের পরিমাণ কম। সরকারি হিসাব অনুযায়ী এবার আলুর উৎপাদন হয়েছে ১ কোটি ৬ লাখ টন। ব্যবসায়ীরা বলেছেন, এ হিসাব অতিরঞ্জিত, স্ফীত। এবার আলুর উৎপাদন হয়েছে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কম। সর্বসাকুল্যে উৎপাদন হয়েছে ৮৫ থেকে ৯০ লাখ টন। এ দুটি হিসাবের মাঝামাঝি স্থানে প্রকৃত উৎপাদন ধরে নিলে এবার আলুর মোট উৎপাদন দাঁড়ায় ন্যূনপক্ষে ৯৫ লাখ থেকে ১ কোটি টন। আমাদের অভ্যন্তরীণ চাহিদা, বীজ, অপচয় ও রপ্তানি মিলে মোট প্রয়োজন ৮০-৮৫ লাখ টন আলু। তাতে এবার উদ্বৃত্ত আছে প্রায় ১৫ লাখ টন। বর্তমানে হিমাগারে ও কৃষক পর্যায়ে চিরায়তভাবে সংরক্ষণ মিলে আলুর মজুত প্রায় ৫ লাখ টন। তা সত্ত্বেও ভোক্তা পর্যায়ে আলুর সরবরাহ হ্রাস এবং উল্লেখযোগ্য মূল্যবৃদ্ধি অত্যন্ত অযৌক্তিক। তাতে ব্যবসায়ী ও কোল্ড স্টোরেজ মালিকদের কারসাজি আছে। এক্ষেত্রে তাদের সিন্ডিকেট ক্রিয়াশীল। এটাকে অকার্যকর করার জন্য প্রয়োজন ছিল আলুর বাজারে সরকারি হস্তক্ষেপ। কিন্তু সরকারি পর্যায়ে আলু সংরক্ষণ ও মজুতের কোনো ব্যবস্থা না থাকায় তা সম্ভব হচ্ছে না।
এক হিসাবে দেখা যায়, আলুর কেজিপ্রতি উৎপাদন খরচ বর্তমানে প্রায় ১১ টাকা। কৃষক পর্যায়ে আলুর প্রতি কেজি বিক্রয় মূল্য গড়পড়তা ১৫ টাকা। এর সঙ্গে কোল্ড স্টোরেজের ফি, অপচয়, পরিবহণ ও বাজারজাতকরণের খরচ যোগ করা হলে পাইকারি পর্যায়ে আলুর প্রতি কেজির মূল্য ২৫ টাকা হতে পারে। খুচরা পর্যায়ে তা ৩০-৩৫ টাকা হওয়া উচিত। আমদানি করা আলুর দামও ৩৫ টাকার বেশি হওয়া উচিত নয়। কিন্তু সেক্ষেত্রে ভোক্তা পর্যায়ে ৭০-৭৫ টাকা আলুর কেজিপ্রতি মূল্য খুবই অস্বাভাবিক। গত পাঁচ বছরের মধ্যে এর দাম এবারই সর্বোচ্চ। চার বছর আগে ২০২০ সালেও আলুর মূল্য আচমকা বৃদ্ধি পেয়েছিল। তখন এর ওপর বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের উদ্যোগে একটি সমীক্ষা হয়েছিল আমার তত্ত্বাবধানে। তাতে প্রতীয়মান হয়েছিল, আলু ব্যবসায়ীদের অসাধু তৎপরতা এবং কোল্ড স্টোরেজ থেকে বাজারে খালাসের ধীরগতির কারণে ওই মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছিল। এবারও তা-ই হয়েছে। বরাবরের মতো এবারও আলুর উৎপাদন উদ্বৃত্ত। বর্তমানে দেশের অভ্যন্তরে আলুর মজুতও ভালো আছে। আমদানিও হচ্ছে। তারপরও বাজারে পণ্যটির মূল্যবৃদ্ধির কারণ ব্যবসায়ীদের কারসাজি।
গত প্রায় ১ দশক ধরে আলু রপ্তানি হচ্ছে বিদেশে। কিন্তু এর পরিমাণ তেমন বেশি নয়, ২০১০-১১ সালে বাংলাদেশ থেকে টাটকা আলু রপ্তানি হয়েছে ৩৯ হাজার ৫৩৯ টন। ২০১১-১২ সালে এর পরিমাণ ছিল ১৮ হাজার ৮৬২ টন। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ২৮ হাজার ৫৭২ টনে। গত বছর (২০২৩-২০২৪) রপ্তানির পরিমাণ হ্রাস পায় ১২ হাজার ৩৫২ টনে। আমদানি করা হয় ৯৮ হাজার টন। এবারও অভ্যন্তরীণ বাজারে সরবরাহ বৃদ্ধি ও দাম নিয়ন্ত্রণের জন্য আমদানি করা হচ্ছে আলু। অনুমতি দেওয়া হয়েছে ১ লাখ ৬১ হাজার টন আলু আমদানির জন্য। দীর্ঘদিন ধরে আলু রপ্তানিকারী দেশ হিসাবে পরিচিত বাংলাদেশ এখন পরিণত হয়েছে নিট আমদানিকারক দেশ হিসাবে। এবার আলুর আমদানিকে উৎসাহিত করার জন্য আমদানি শুল্ক ২৫ শতাংশ থেকে হ্রাস করা হয়েছে ১৫ শতাংশে। তাছাড়া নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক ৩ শতাংশ মওকুফ করা হয়েছে। এরপরও অভ্যন্তরীণ বাজারে আলুর দাম চালের দামের চেয়ে বেশি।
অন্যান্য বছর ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে প্রচুর নতুন আলু আসে বাজারে। এবার এর উৎপাদন ও সরবরাহ কম। গত অক্টোবর মাসে অতিরিক্ত বৃষ্টির কারণে আলুর আবাদ বিলম্বিত হয়েছে। এর পর দেখা গেছে বীজের অভাব। বাংলাদেশে প্রায় সাড়ে ৭ লাখ টন আলু বীজের দরকার হয়। এর মধ্যে বিএডিসি সরবরাহ করে ৩৭ হাজার টন। ব্যক্তি খাতের ব্যবসায়ীরা সরবরাহ করে ৫০ হাজার টন। বাকি বীজ কৃষকরা সংরক্ষণ করে থাকে। এবার আলুর মূল্যবৃদ্ধির কারণে অনেক বীজ-আলু খাবারের আলু হিসাবে বিক্রি হয়ে গেছে। তাতে দেখা দিয়েছে বীজের সংকট। ক্ষেত্রবিশেষে তা ১০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়েছে বাজারে। সেই সঙ্গে বেশি দাম গুনতে হয়েছে রাসায়নিক সারের জন্য। তাতে উৎপাদন খরচ বেড়েছে কৃষকদের। ফলে সামনের ভরা মৌসুমে খামার প্রান্তে আলুর দাম হবে বেশি। খুচরা পর্যায়ে দাম হতে পারে প্রতি কেজি ৩৫ থেকে ৪০ টাকা। বর্তমানে দেশে অবমুক্ত প্রায় ৪০টি জাতের উন্নত আলুর চাষাবাদ হচ্ছে কৃষক পর্যায়ে। উচ্চ ফলনশীল জাতের আলু বীজ সম্প্রসারিত হয়েছে ৮০ শতাংশেরও বেশি আবাদি এলাকায়। কিন্তু কৃষক পর্যায়ে প্রত্যায়িত বীজ ব্যবহারের হার মাত্র ১০ শতাংশ। বাকি ৯০ শতাংশ অপ্রত্যায়িত। ভালো খামার ব্যবস্থাপনা, যথাযথ পর্যায়ে উপকরণ ব্যবহার, রোগ প্রতিরোধ, পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সম্পর্কিত ভালো ধ্যান-ধারণার ঘাটতি আছে কৃষকদের। এর জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিতে হবে তাদের। এছাড়া ভালোভাবে প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্যাকেটজাতকরণ ও সংরক্ষণ অবকাঠামোর উন্নয়ন সাধন করতে হবে। আমাদের দেশে প্রতিবছর ১০ থেকে ১৫ লাখ টন আলু পচে যায় কিংবা রোগ-বালাই ও পোকার আক্রমণে এর মান নষ্ট হয়ে যায়। এ অপচয় হ্রাস করতে হবে। তাতে আলুর মূল্য হ্রাস পাবে।
বিশ্বব্যাপী একটি জনপ্রিয় খাদ্য আলু। নিউজিল্যান্ড ও হল্যান্ডসহ পৃথিবীর অনেক দেশে আলুই মানুষের প্রধান খাবার। কিন্তু আমাদের দেশে মানুষের খাদ্য তালিকায় আলুর নাম প্রায়ই থাকে অনুপস্থিত। দেশের মোট খাদ্যশস্যের উৎপাদন, ভোগ ও বিতরণের ক্ষেত্রে সরকারিভাবে যে হিসাব দেওয়া হয়, তাতেও আলু সম্পর্কে কোনো পরিসংখ্যান থাকে না। এদেশে আলুর পরিচিতি মূলত সবজি হিসাবে। আদিকাল থেকেই এখানকার মানুষ ভাতের সঙ্গে ভর্তা হিসাবে অথবা মাছ-মাংসের তরকারির সঙ্গে সবজি হিসাবে আলুর ব্যবহার করে আসছে। তাছাড়া আলু ভাজি ও আলুর দম সবার কাছেই উপাদেয় সবজি। সাম্প্রতিক সময়ে বিরিয়ানিতে আলুর ব্যবহার বেড়েছে। অভিজাত হোটেলগুলোতে সিদ্ধ আলু এবং আলুর চিপস নিয়মিত পরিবেশন করা হচ্ছে। শিশু ও কিশোরদের কাছে আলুর চিপস খুবই উপাদেয় খাবার। কিন্তু সাধারণভাবে আলুকে আমরা কখনোই প্রধান খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করিনি। এদেশে এর ব্যবহার মূলত সহযোগী খাদ্য হিসাবে। ভাতের বিকল্প হিসাবে ‘রোস্টেড পটেটো’, সিদ্ধ আলু কিংবা আলুর চিপস জনসাধারণের মাঝে এখনো জনপ্রিয় হওয়ার অপেক্ষায় আছে। একে উৎসাহিত করা দরকার। এক্ষেত্রে খাদ্য হিসাবে আলুর বিভিন্ন ব্যবহার জনপ্রিয় করে তোলা প্রয়োজন। মানুষকে জানানো প্রয়োজন এর পুষ্টিমান সম্পর্কে। এর জন্য প্রতিটি ইউনিয়ন ও গ্রামে আয়োজন করা দরকার আলুর মেলা। প্রতিটি মহল্লা থেকে মেয়েদের ডেকে এনে খাবারের মধ্যে আলুর বিচিত্র ব্যবহার বিষয়ে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া দরকার।
আদিকালে আলুর ব্যবহার ছিল পশুখাদ্য হিসাবে। এর আদি নিবাস ছিল পেরু। ১৫৭০ সালে এর বিস্তার ঘটে স্পেনে। অতঃপর ১৬০০ সালে এর আবাদ ছড়িয়ে পড়ে ইতালি, ফ্রান্স, হল্যান্ড, ইংল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, জার্মানি ও অন্যান্য দেশে। ১৯৭৫ সালে ইংল্যান্ডের কৃষি বিভাগ একটি পুস্তিকা বের করে, যার শিরোনাম ছিল ‘আলু ভালোবাসুন, আলুর ব্যবহার বাড়ান’। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে বিশ্বব্যাপী খাদ্য সংকট নিরসনকল্পে মানুষের খাদ্য হিসাবে আলুর কদর বেড়ে যায়। গোল আলু এবং মিষ্টি আলু দুটিই যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর খাদ্য সংকট মোকাবিলায় বিশেষ ভূমিকা রাখে। এক্ষেত্রে মিষ্টি আলুর ভূমিকা খুবই উল্লেখযোগ্য। এটি পুড়িয়ে বা সিদ্ধ করে খাওয়া যায়, কাঁচাও খাওয়া যায়। যে কোনো জমিতে অতি অল্প পরিচর্যায় আলু ফলানো সম্ভব। অন্য যে কোনো শস্যের চেয়ে আলুর ফলন বেশি। মুনাফাও বেশি। আলু থেকে আমরা শ্বেতসার পাই। এতে অনেক পুষ্টির উপাদানও বিদ্যমান। এসব কারণে বাংলাদেশেও ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে আলু। এর চাহিদা বাড়ছে। আবাদও বাড়ছে। বাড়ছে উৎপাদন ও মুনাফা। এর জন্য টেকসই উৎপাদন ও সংগ্রহ নীতিমালা থাকা উচিত। মোট উৎপাদিত আলুর ন্যূনপক্ষে ৫-৭ শতাংশ সরকারিভাবে সংরক্ষণ করা উচিত। তাতে আলুর সরবরাহ ও মূল্য স্থিতিশীল রাখা সম্ভব হবে।
ড. জাহাঙ্গীর আলম : কৃষি অর্থনীতিবিদ, গবেষক ও শিক্ষক। সাবেক মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং সাবেক উপাচার্য, ইউনিভার্সিটি অব গ্লোবাল ভিলেজ