
প্রিন্ট: ২৩ এপ্রিল ২০২৫, ০৮:০৫ এএম
সনদের উপযোগিতা ও বাস্তবতা
নাজমুল আহসান শেখ
প্রকাশ: ০৮ জুন ২০২৩, ১২:০০ এএম
প্রিন্ট সংস্করণ
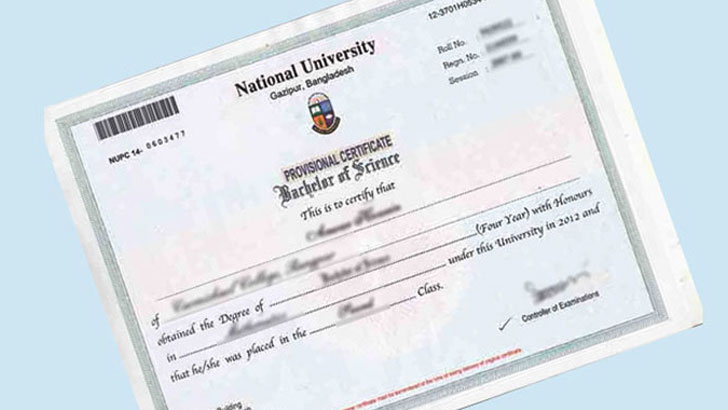
ফাইল ছবি
আরও পড়ুন
বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়ালে প্রায়ই একটি স্লোগান দেখতে পাওয়া যেত-‘শিক্ষা সুযোগ নয়, অধিকার!’ ডিজিটাল যুগে দেওয়ালের স্থান দখল করে নিয়েছে ডিজিটাল ডিভাইস, যেমন মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ, ট্যাবলেট ইত্যাদি। আর দেওয়ালের লেখনকে প্রতিস্থাপিত করেছে ইউটিউব, ফেসবুক এবং অন্যান্য ডিজিটাল মাধ্যম। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত দুটি বিষয়/খবর সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় তুলেছে। এ বিষয়ে আলোচনা করার আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা নিয়ে একটু আলোচনা করার দরকার আছে বলে মনে করি।
শিক্ষা একটি মৌলিক অধিকার, তবে তা উচ্চ বা বিশেষায়িত শিক্ষা নয়, প্রাথমিক শিক্ষা হচ্ছে মৌলিক অধিকার। প্রাথমিক শিক্ষার সংজ্ঞা আবার বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পর্যায়ের। উন্নত বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাকেই প্রাথমিক শিক্ষা বলে ধরা হয়ে থাকে। আমাদের দেশে পঞ্চম/অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাকেই অনেক শিক্ষাবিদ প্রাথমিক শিক্ষা বলে মনে করেন।
অষ্টম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাকে মাধ্যমিক/উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা হিসাবে অধিকাংশ দেশেই গণ্য করা হয়। আমাদের দেশে দশম শ্রেণি, দ্বাদশ শ্রেণিতে বোর্ডের পরীক্ষা পাশের পর সনদপত্র দেওয়া হয়। দ্বাদশ শ্রেণির পর শুরু হয় বিশেষায়িত শিক্ষা, যা মূলত বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই প্রদান করা হয়ে থাকে। ডাক্তারি শিক্ষা আমাদের দেশে যদিও মেডিকেল কলেজ থেকে দেওয়া হয়ে থাকে, কিন্তু ডাক্তারি সনদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই দেওয়া হয়।
আমাদের সময় এসএসসি/এইচএসসি পাশ করার পর এই সনদপত্র প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। প্রথম শ্রেণির মধ্যে প্রথম বিশজনকে স্থান অধিকারী হিসাবে বিশেষ মর্যাদা দেওয়ার প্রচলন ছিল। ৭৫০ অথবা এর ঊর্ধ্বে নম্বর পেলে স্টার মার্ক্স বলা হতো। তাই দেখা যায়, সব সনদের মর্যাদা ও মূল্য এক ছিল না। এখন জিপিএ পদ্ধতিতে মেধা নির্ণয় করা হয়, এখানেও বিভাজন আছে এবং থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিভিন্ন কলেজে ভর্তির সময় মেধাবী শিক্ষার্থী যাচাই করার ক্ষেত্রে এ বিভাজনের ওপর সম্পূর্ণ বা আংশিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। চাকরির ক্ষেত্রে সনদের বিষয়, সনদ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এবং ফলাফল যাচাই-বাছাই করে মূল্যায়ন করা হয়। তাই সব সনদ সমান নয়। প্রায় সব ক্ষেত্রেই সনদকে পরবর্তী ধাপের উচ্চশিক্ষা, কিংবা চাকরির জন্য ন্যূনতম নির্ণায়ক হিসাবে ব্যবহার করা হয়। উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং সরকারি/বেসরকারি চাকরিদাতা প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে সনদধারীর যোগ্যতা যাচাই করে।
পশ্চিমা বিশ্বে অর্থবান ও অসাধারণ মেধাবীদের এবং সাবেক সমাজতান্ত্রিক বিশ্বে (চীন/সোভিয়েত ইউনিয়ন) বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু অসাধারণ মেধাবীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ দেওয়া হয়। বর্তমানে চীন, জাপান, সিঙ্গাপুরের মতো উন্নত দেশে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা অধিক মেধাবীর জন্য উন্মুক্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বল্প আসনের কারণেই শুধু অসাধারণ মেধাবীরা বিশেষায়িত শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পায়। মৌলিক বিষয় ছাড়া অন্যান্য ফলিত বিষয়ের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ইন্ডাস্ট্রি, দেশ এবং বিশ্ববাজারে চাহিদার সঙ্গে সংগতি রেখেই বিভিন্ন বিষয় পাঠ্যসূচি তৈরি করে। কারণ সমাজের চাহিদার তুলনায় অতিরিক্ত ছাত্রছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করলে উচ্চশিক্ষিত হতাশ বেকার তৈরি করা ছাড়া কোনো ফল পাওয়া যায় না। তূলনামূলকভাবে কম মেধাবীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়ন করিতে চাইলে নিজ অর্থায়নে দেশে-বিদেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়।
আমাদের দেশে বর্তমানে সমাজ ও অর্থনীতির চাহিদার সঙ্গে কোনোরকম সামঞ্জস্য না রেখে অনেক সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আরও অনেক চাহিদাবিহীন বিভাগ স্থাপন করার ফলে লাখ লাখ অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে সনদধারী ও হতাশ বেকার তৈরি হচ্ছে, যা জনগণের অর্থের এবং এসব জনশক্তির সময় এবং শ্রমের মারাত্মক অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়। যে কোনো সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন স্নাতক ছাত্রের পেছনে দেশের লাখ লাখ টাকা ব্যয় হয়। চাহিদাবিহীন শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত বিপুলসংখ্যক যুবশক্তি তাদের পছন্দমতো দূরের কথা, যোগ্যতা অনুযায়ী কোনো ধরনের চাকরিই পায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার ফলে তৈরি অহংবোধের কারণে অন্য ধরনের কাজ (যেমন কৃষিকাজ, গাড়ি বা এসির মেকানিক) করতে আগ্রহী হয় না। পরবর্তীকালে বাস্তবতার কারণে এবং জীবিকার তাগিদে অনেক কম শিক্ষাগত যোগ্যতা দরকার, এ ধরনের কাজে থিতু হয়। অথচ এ ধরনের তুলনামূলকভাবে কম মেধাবীরা মাধ্যমিক/উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার (জিপিএ ২-৩) পর কারিগরি বা হাতেকলমে শিক্ষা গ্রহণ করলে দেশের অর্থ এবং তাদের শ্রম এবং সময় দেশের এবং নিজেদের কাজে লাগত।
সম্প্রতি ডিজিটাল মিডিয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় নিশ্চিতভাবে অকৃতকার্য হওয়ার আশঙ্কায় ভর্তি পরীক্ষার পর এক ছাত্রীর বক্তব্য-‘কোনো চিপাচাপা থেকে প্রশ্ন করা হয়েছে যে কিছুই সে বুঝতে/উত্তর দিতে পারেনি।’ তার কথাবার্তা, বাচনভঙ্গি, শারীরিক ভাষা সবই বলে দিচ্ছিল সে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করার যোগ্য নয়। এ ধরনের মেধাহীনদের বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন না করা দেশের এবং তার জন্য মঙ্গলজনক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে আসনসংখ্যার চেয়ে কম শিক্ষার্থী ভর্তি পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়ার কারণে কিছু আসন খালি রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, যা শিক্ষার মান সমুন্নত রাখার জন্য অতীব প্রয়োজনীয় ও প্রশংসাযোগ্য।
সম্ভবত ইডেন কলেজের একজন স্নাতক সনদধারী নিজের সনদ পুড়িয়ে ফেসবুকের কল্যাণে ভাইরাল হয়েছিলেন এবং সাধারণ মানুষের সহানুভূতি অর্জন করেছিলেন। আমি জানি না সেই শিক্ষার্থী কোন বিষয়ে স্নাতক লাভ করেছেন এবং তার ফলাফল কেমন। ধারণা করতে কষ্ট হয় না, তিনি নিশ্চয়ই তেমন মেধাবী নন, কারণ তিনি ৫৩টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটিতেও ভর্তি হতে পারেননি। তার ফলাফল ও বিষয় সম্পর্কে কিছুই বলেন না। এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি অভিযোগ করেছেন, উদ্যোক্তা হতে অর্থের প্রয়োজন! তার মতো আরও অনেকেই এ ধরনের অভিযোগ করে থাকেন। আমি জানি না তিনি কী ধরনের উদ্যোক্তা হইতে চান; তবে ইউটিউবে প্রায়ই দেখা যায়, অনেক সফল উদ্যোক্তাই খুবই অল্প পুঁজি নিয়ে শুরু করে সাফল্য অর্জন করেছেন। তাদের অধিকাংশই বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ মারাননি। আবার অনেক উদ্যোক্তার কেউ সেলাই করে, ছাত্র পড়িয়ে, রান্না করা খাবার সরবরাহ করে, দোকানে কাঁচামাল, সবজি সরবরাহ করেই সাফল্য লাভ করেছেন। এজন্য তাদের মধ্যে ছিল না কোনো অহংবোধ, তারা সবাই ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী, তাদের ছিল কাজ করার স্পৃহা আর যে কোনো কাজ করার মানসিকতা। তুলনামূলকভাবে কম মেধাবীদের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রকারান্তরে উদ্যোক্তা হওয়ার পেছনে মানসিক বাধা হিসাবে কাজ করে বলেই প্রতীয়মান হয়।
আমাদের দেশে চাহিদার তুলনায় অনেক বেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে স্নাতক তৈরি করার ফলে স্নাতকধারী বেকারের সংখ্যা দিনদিন বাড়তেই থাকবে, সরকারি চাকরির বয়সসীমা বৃদ্ধি করলে কোনো লাভ হবে না। হয়তো স্নাতকধারীরা ৩০ বছরের ক্ষেত্রে ৪০ বছর পর্যন্ত চাকরির পরীক্ষা দিতে পারবেন, কিন্তু এতে পরীক্ষাজনিত খরচ এবং শ্রমের অপচয় ছাড়া কোনো লাভ হবে না। এমনকি শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ কখনোই চাকরির নিশ্চয়তা দেয় না, এ তথ্য সবারই জানা থাকা উচিত।
ওষুধ, খাদ্যের মতো প্রতিটি পণ্যের যেমন কার্যকর জীবনকাল থাকে, তেমনি সনদেরও কার্যকর জীবনকাল আছে। সনদ লাভ করার কয়েক বছরের মধ্যে কর্মক্ষেত্রে যোগদান না করলে সনদের মূল্য অতি দ্রুত কমতে থাকে। বিশেষ করে কম্পিউটার, তথ্যপ্রযুক্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রে কয়েক বছর কাজ না করলে সেই সনদ অনেকটা অকার্যকর হয়ে যায়।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগে শিক্ষার্থীর অভাবে বেশ কিছুসংখ্যক আসন খালি থাকার খবর বাস্তবতা সম্পর্কে ধারণা দেয়। দেরিতে হলেও ধীরে ধীরে উচ্চশিক্ষা এবং সনদের বাস্তব মূল্য, উপযোগিতা ও উপকারী কার্যকাল সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ শিক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকদের চোখ খুলছে। সামাজিক কারণে যেমন: সামাজিক মর্যাদা, বিয়েশাদি, ভবিষ্যতে নির্বাচনে অংশগ্রহণের কারণে কেউ যদি চাহিদাবিহীন বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ নিতে আগ্রহী হন, তাদের কথা ভিন্ন।
তাই আর কালক্ষেপণ না করে সব বিশ্ববিদ্যালয়ে বাস্তব সামগ্রিক চাহিদার সঙ্গে সংগতি রেখে বিষয় ও আসনসংখ্যা নির্ণয় এবং পুনর্বিন্যাস করা উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকসমাজ যদি ক্ষুদ্র ব্যক্তি স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে ভবিষ্যৎ চাহিদার নিরিখে বিষয় এবং আসনসংখ্যা নির্ণয় ও পুনর্বিন্যাস না করেন, তাহলে তারা তাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছেন বলে মনে করা হতে পারে। বিশেষায়িত শিক্ষা একজন শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগ। ইউজিসি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এ ব্যাপারে আরও অনেক সজাগ হওয়া উচিত। এর পাশাপাশি শিক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকদের উচিত উচ্চশিক্ষা গ্রহণের আগে বিষয়ের চাহিদা এবং চাকরির সম্ভাবনা সম্পর্কে ভালোমতো গবেষণা করা, অন্যথায় সনদ পোড়ানো অথবা হতাশার আগুনে পুড়তে হতে পারে।
সর্বশেষ : ইডেন কলেজের স্নাতক সনদধারী নিজের সনদ পুড়িয়ে ফেসবুকের কল্যাণে ভাইরাল হয়ে ঊর্ধ্বতন ব্যক্তিদের নজরে পড়ে একটি চাকরি জোগাড় করতে সমর্থ হয়েছেন। তার এ দ্রুত সাফল্য বেকার চাকরিপ্রত্যাশীদের মধ্যে কী বার্তা দেয়, তা দেখার অপেক্ষায় রইলাম। তবে আমি নিশ্চিত, এ ধরনের বিচ্ছিন্ন পদক্ষেপ জটিল রোগের ব্যথা নিরসনে পেইন কিলারের মতো সাময়িক কাজ করলেও মূল সমস্যা নিরসনে অবিলম্বে পদক্ষেপ না নেওয়া হলে এ ধরনের ‘হতাশাগ্রস্ত উচ্চশিক্ষিত বেকারদের সমস্যা’ সমাজে ক্যানসারের মতো ছড়িয়ে পড়বে।
নাজমুল আহসান শেখ : শিক্ষক ও প্রাবন্ধিক
victory1971@gmail.com
