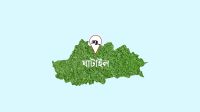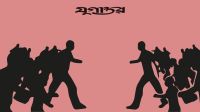প্রিন্ট: ০৩ এপ্রিল ২০২৫, ০৯:৩৫ পিএম
রিজার্ভ বৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতি
ড. রাজীব চক্রবর্তী
প্রকাশ: ২৩ নভেম্বর ২০২৪, ১২:০০ এএম
প্রিন্ট সংস্করণ

দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ধীরে ধীরে বাড়ছে এবং স্থিতিশীল হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর। ৮ অক্টোবর পর্যন্ত বিপিএম ৬ অনুযায়ী বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ দাঁড়িয়েছিল ১৯ দশমিক ৮২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। আর মোট রিজার্ভ ২৮ দশমিক ৯৭ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছিল। ডলারের বিপরীতে টাকার মানকে সমন্বয় করার ফলে প্রবাসীরা ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স পাঠাতে উৎসাহিত হচ্ছেন। ফলে বিগত বছরের অক্টোবরে ১৯৭ কোটি ডলারের বিপরীতে এ বছর অক্টোবরে রেকর্ড ২৪০ কোটি মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স এসেছে, যা একক মাস হিসাবে একই সময়ের তুলনায় ২১ শতাংশ বেশি। যদিও ডলারের বিপরীতে টাকার দরপতন, ডলারের সংকট অপ্রয়োজনীয় আমদানিকে এখনো নিরুৎসাহিত করছে। এই ফাঁকে রেমিট্যান্সের ওপর ভর করে রিজার্ভ বাড়িয়ে বৈদেশিক মুদ্রার বাজার স্থিতিশীল করা অর্থনীতির জন্য একটি ভালো দিক।
তবে বৈদেশিক মুদ্রা আহরণের অন্যতম আরেক খাত পোশাকশিল্পে অস্থিরতা যেন আর না বাড়ে, সেদিকে নজর দিতে হবে। এমনিতেই আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক সংশোধিত আকারে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধির হার নিম্নগামী হওয়ার পূর্বাভাস দিয়েছে; যা আগের ৬ থেকে কমিয়ে ৪ দশমিক ৫ শতাংশ হতে পারে বলে আশঙ্কা করছে। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেছেন, ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিনিয়োগের আস্থার সংকট তৈরি হয়েছে। যতই ব্যবসায়ীদের রপ্তানি আয়ের একটি অংশ পাচার করেছে বলে গালি দেওয়া হোক না কেন, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য তাদের অবশ্যই আস্থায় আনা দরকার। তবে তদারকি বাড়াতে হবে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) ও বাংলাদেশ ব্যাংকের মধ্যে রপ্তানি তথ্যর যে গরমিল, তা রোধে পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি। তবে ইপিবি বলছে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) পরিসংখ্যানের ভিত্তিতেই রপ্তানির হিসাব প্রকাশ করা হয়েছে, যার মধ্যে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের (ইপিজেড) প্রচ্ছন্ন রপ্তানি যুক্ত আছে।
এদিকে ব্যাংক ঋণের ৯ শতাংশ সুদ বেড়ে এখন ১৪ থেকে ১৫ শতাংশ হওয়া, শিল্পাঞ্চলে অস্থিরতা ও বিদ্যুৎ-জ্বালানি সংকটে বিনিয়োগে স্থবিরতা চলছে। এ ছাড়া রাজনৈতিক সরকার না থাকার ফলে অনেক উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ অর্থছাড়ের অভাবে থমকে আছে। এ কথা ঠিক, অর্থনীতিতে টাকার সঞ্চালন বাড়লে মানুষের আয় বাড়বে, বিনিয়োগ উৎসাহিত হবে, কর্মসংস্থান তৈরি হবে। আবার অতিরিক্ত বৈদেশিক ঋণে উন্নয়ন প্রকল্পের যৌক্তিকতা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে।
ইদানীং খবরে প্রকাশ, রিজার্ভে হাত না দিয়ে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোতে সঞ্চিত অতিরিক্ত রিজার্ভ থেকে ২ বিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ করা হয়েছে। বস্তুত, একদিকে বৈদেশিক ঋণ ছাড় কিছুটা ধীর হলেও রেমিট্যান্সের ঊর্ধ্বমুখী প্রবাহ, আমদানি নিয়ন্ত্রণ ও বিদেশগামিতা কমে যাওয়ার কারণেই মূলত খোলাবাজারে ডলারের দাম স্থিতিশীল রয়েছে। তবে ব্যাংকগুলোতে তারল্য সংকট কাটেনি। ৫ আগস্টের আগে একটা সময় দেশে ডলার সংকট ছিল বলে মুদ্রা বাজার অস্থিতিশীল ছিল। তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক টাকা ছাপিয়ে ব্যাংকগুলোতে সরবরাহ করেছিল। বর্তমান গভর্নর টাকা ছাপিয়ে তারল্য সংকট নিরসনের পক্ষে নন। তাছাড়া, দেশে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে জুলাইয়ে মূল্যস্ফীতি ছিল ১১ দশমিক ৬৬ শতাংশ। বিশেষ করে খাদ্য মূল্যস্ফীতি ১৪ দশমিক ১ শতাংশ, যা সবচেয়ে বেশি কষ্টে ফেলেছে নিম্নআয়ের মানুষকে।
কয়েকদিন আগে পিকেএসএফের এক অনুষ্ঠানে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ দুঃখ প্রকাশ করে বলেছেন, অনেক পণ্যের ওপর শুল্ক ছাড় দেওয়ার পরও বাজারে তার প্রভাব পড়ছে না। মানুষ ৫০০ টাকা নিয়ে বাজারে গেলে সামান্য কিছু কিনতেই টাকা শেষ। অনেক প্রতিষ্ঠান কার্যক্ষমতা হারিয়েছে। প্রতিষ্ঠান আছে, কিন্তু মানুষ নেই।
তবে বিগত মাসে রপ্তানি আয় ইতিবাচক ধারায় ফিরেছে। চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম চার মাস জুলাই-অক্টোবরে ১ হাজার ৫৭৯ কোটি ডলার মূল্যের পণ্য রপ্তানি হয়েছে, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ১০ দশমিক ৮০ শতাংশ বেশি। ইপিবির তথ্যানুযায়ী, সর্বশেষ অক্টোবর মাসে ৪১৩ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে, যা এর আগের ২০২৩-২৪-এর একই সময়ে ৩৪২ কোটি ডলারের চেয়ে ২০ দশমিক ৬৫ শতাংশ বেশি।
মোদ্দাকথা, জিডিপির আকার যেহেতু বেড়েছে, প্রবৃদ্ধিও বাড়াতে হবে। আর এটি সম্ভব হবে, যখন দেশে বহুমুখী অর্থনৈতিক কার্যক্রম বেগবান হবে, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে, অভ্যন্তরীণ খাতে রাজস্ব আয় বাড়বে, মানুষের মধ্যে ভোগের চাহিদা বাড়বে, তখন। এসবের জন্য অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা আনার লক্ষ্যে বহুমুখী উৎপাদন-বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা চাই। এর জন্য অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ব্যবস্থায় বিশেষ নজর দিতে হবে। ক্ষুদ্র, মাঝারি বিনিয়োগকে আরও উৎসাহিত করতে হবে। বিদেশি বিনিয়োগ যেহেতু কিছুটা স্থবির, সেহেতু দেশীয় চাহিদা দেশীয় উৎপাদন দিয়ে মেটাতে হবে। এতদিন বড় বড় করপোরেট হাউজগুলো যে ইচ্ছামতো মনোপলি সৃষ্টি করেছে বাজার সরবরাহ ব্যবস্থায়, তার লাগাম টানতে হবে। বাজার তদারকি বা মনিটরিং জোরদার করা না গেলে, বাজার ব্যবস্থাপনার পদ্ধতিগত ত্রুটি ও প্রাতিষ্ঠানিক ত্রুটি দূর করা না গেলে সাধারণ মানুষ সুফল পাবে না।
অভ্যন্তরীণ খাতের আরেকটি আয়ের উৎস হলো রাজস্ব আয়। তবে বাংলাদেশের কর-জিডিপি অনুপাত ১০ শতাংশের নিচে, যা দক্ষিণ এশিয়ায় শুধু আফগানিস্তানের উপরে। সাধারণ মানুষকে পর্যাপ্ত সেবা দেওয়ার মাধ্যমে সরকারকে কর আদায় করতে হয়। এটাই নিয়ম। দেশে প্রত্যক্ষ করের অবস্থা ইতিবাচক নয়। অর্থনীতির ভিতকে মজবুত রাখার জন্য রাজস্ব আয় বাড়ানোর কোনো বিকল্প নেই। তবে দেশের বিগত সব রাজনৈতিক সরকারই জনরোষ এড়াতে নতুন করে করারোপ না করার কৌশল নিয়ে এগিয়েছে। আবার ব্যবসায়ীরা রাজনীতিবিদ বনে জাতীয় সংসদে যাওয়ায় ২০২২ সালের হিসাবমতে সরকারকে প্রায় আড়াই লাখ কোটি টাকার কর ছাড় দিতে হয়েছিল। অন্যদিকে ইচ্ছামতো বিবিধ ভ্যাট, আবগারি শুল্ক, ট্যারিফ বাড়িয়ে পণ্যের বাজারকে প্রতিযোগিতাহীন করা হয়েছে। ফলে যুগোপযোগী ব্যবসাবান্ধব কর নীতিমালা না থাকায় দেশে কোনো শিল্পই বিকশিত হয়নি। যত সুবিধা দেওয়া হয়েছে, তার বেশিরভাগই তৈরি পোশাক শিল্পকেন্দ্রিক। অনেক সম্ভাবনাময় রপ্তানি খাত যেমন-পাদুকা শিল্প, হিমায়িত খাদ্য, চামড়া, পাটশিল্পসহ বেশকিছু খাত রপ্তানিতে সাফল্য এনেছে। এখন তাদের জন্য দরকার আরও পৃষ্ঠপোষকতা। তবে ব্যাংক খাতে শৃঙ্খলা ফেরানো সবচেয়ে জরুরি।
ড. রাজীব চক্রবর্তী : গবেষক ও অর্থনীতি বিশ্লেষক



-67abc35b463b8.jpg)


-67eed7b2b8e78.jpg)
-67eed42f32a94.jpg)
-67eec44993662.jpg)