যে কারণে একুশ জরুরি
নাভিদ সালেহ
প্রকাশ: ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, ১২:০০ এএম
প্রিন্ট সংস্করণ
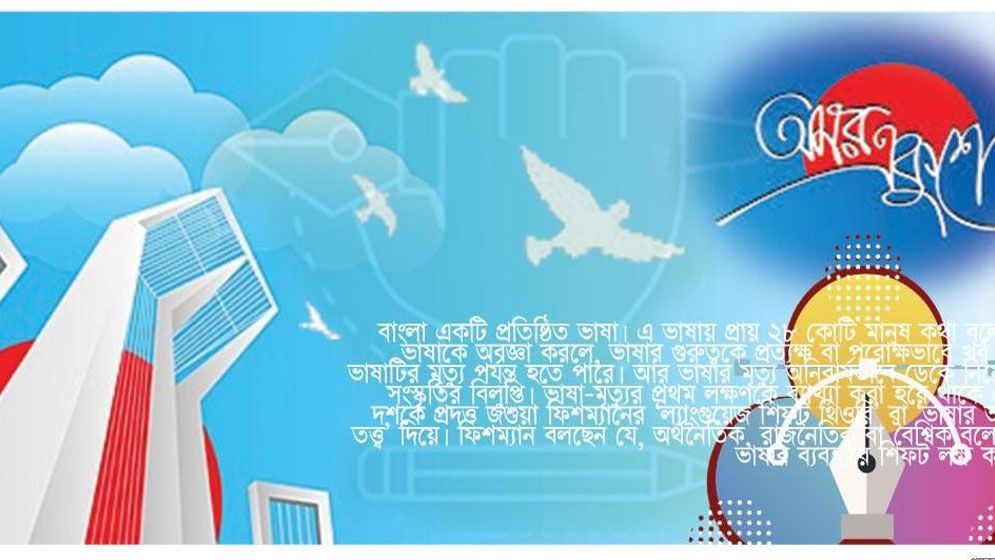
উপনিবেশের একটা অদৃশ্য অনিবার্যতা আছে। যারা উপনিবেশ স্থাপন করে তারা তাদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে চাপিয়ে দিয়ে ‘সফ্ট পাওয়ার’ চরিতার্থ করতে চায়। এটি ক্ষমতা কুক্ষিগত করা ও এর বিস্তারের একটি আদি পন্থা। অটোমান সাম্রাজ্যের সময়কালে বলকান অঞ্চলে আধিপত্য তৈরি করতে তুর্কি ভাষার প্রচার বাড়ানো হয়েছিল। ক্যালিগ্রাফি আর ক্ষুদ্র চিত্রকর্মে অর্চনা করা হয়েছিল অটোমান সম্রাটদের জীবনধারার জৌলুসকে। ইংরেজদের শাসনামলে সব কেন্দ্রীয় কার্যক্রম ইংরেজিতে সম্পন্ন করা হতো শুধু সাহেবদের সুবিধার্তে নয়, বরং তা ছিল কলোনিস্টদের ক্ষমতা প্রদর্শন ও নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব জারি রাখার একটি নিগূঢ় পন্থা।
ভেবে দেখুন, একজন ব্যক্তি যখন একটি বিষয় বা পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত থাকেন না, তখন তা নিয়ে কথা বলতে বা তার ব্যবহারে যে অস্বস্তি অনুভূত হয়, তা ব্যক্তিকে প্রথমেই দুর্বল করে তোলে, তাকে পিছিয়ে দেয়। যেমন, আমার মা স্মার্ট ফোন ব্যবহার করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন না। তার কাছে এ বোতামবিহীন যন্ত্রটি ছিল অচেনা, অস্বাভাবিক। মুঠোফোন ব্যবহারে তার ভেতর যে দুর্বলতা আমি দেখেছি তা অচেনার-উপস্থাপনে ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়ার একটি প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত। ইংরেজরা তার ঔপনিবেশিক আধিপত্য বিস্তার করতে স্থানীয়দের অপ্রস্তুত করে তুলতে চেয়েছে, আর এজন্য তারা ব্যবহার করেছে ভাষাকে। বাংলাদেশের মানুষকে শোষণ করার ক্ষেত্রে জোর করে উর্দু চাপিয়ে দেওয়ার চেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র কি খুঁজে পেত তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকরা? আন্তোনিও গ্রামসি তার হেজিমনি তত্ত্বে ভাষা ও সংস্কৃতির ব্যবহার করে শোষণকে উপনিবেশের এমনি একটি অন্যতম মাধ্যম হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।
উপমহাদেশের মানুষের ভেতর তাই নিজের ভাষাকে নিয়ে একটা হীনমন্যতা লক্ষ করা যায়। হালে এ প্রবণতা যেন বাড়ছে। পশ্চিম বাংলার বাঙালি গীতিকাররা উচ্চ মুনাফার লোভে যেমন মুম্বাইতে হিন্দি গান লিখতে পাড়ি জমাচ্ছেন, তেমনি বাংলাদেশের বাঙালিরা উঁচু বেতনের চাকরির আশায় ইংরেজিনির্ভর শিক্ষাব্যবস্থায় মন দিচ্ছেন, কিংবা প্রবাসী হচ্ছেন।
গত কয়েক মাসে এর সঙ্গে এসে যুক্ত হয়েছে বাঙালি বনাম বাংলাদেশি পরিচয়ের অতিতর্ক। বাংলাদেশের মানুষ বাংলাদেশি, এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত কী আদৌ থাকে? এ পরিচয় কী কোনো দলের একার, নাকি এটি সর্বজনীন? পরিচয়ভিত্তিক রাজনীতিকীকরণ তাই আমাদের ভাষার ওপর একটি অহেতুক চাপ সৃষ্টি করেছে। রাজনৈতিক মেরুকরণ যেন ঘরের শত্রু বিভীষণের মতো অভন্তরীণ দলবদল আর কোন্দলের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। ভাষা, যা আমাদের সংস্কৃতিকে মূর্ত করে তোলে, তার বিরুদ্ধে গিয়ে দাঁড় করিয়েছে আমাদের। বাংলা ভাষার কবি-সাহিত্যিকদের তাই জাতীয় সীমানার ভেতর বাঁধতে চাইছি আমরা। নজরুল আমাদের, রবীন্দ্রনাথ ওদের। এ ‘আদারিং’-এর চর্চা আমাদের ভাষা আর সংস্কৃতির বিকাশকে শ্লথ করছে। উপনিবেশবাদী শক্তিকে না চাইতেই উপহার হিসাবে আমরা তুলে দিচ্ছি ‘অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র’।
ভাষা জন্মের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মানুষ জন্মগতভাবেই নিজের ভাব প্রকাশ করার তাগিদ অনুভব করে এবং একটি ‘সর্বজনীন ব্যাকরণ’গত কাঠামো স্বভাবজাতভাবে ধারণ করে জন্মায়। নোম চমস্কি তার ‘অন ল্যাংগুয়েজ’ গ্রন্থে বলছেন, ভাব প্রকাশের জন্য মানবকণ্ঠ নিঃসৃত ৫০টি স্বরযোগে তৈরি হয় ‘পিজিন’ নামের প্রাথমিক ভাষা। পরবর্তী সময়ে জীবনের প্রয়োজন, যেমন বাণিজ্য কিংবা গোষ্ঠীবদ্ধতার তাগিদ থেকে, শব্দকে সুগঠিত কাঠামো দিলে প্রস্তুত হয় ‘ক্রিয়োল’। এমন নিদর্শন দেখা গেছে ১৯ শতকের শেষদিকে হাওয়াইতে। ট্রান্স-প্যাসিফিক দাস লেনদেন তখন শুরু হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, চীন, জাপান, কোরিয়া, ও ফিলিপিন্সের ভেতর। নানা দেশের সে মানুষগুলো একে অপরের ভাষা বুঝতে না পারায়। আখ চাষের দাবি থেকে সেই যূথবদ্ধ মানুষ অন্য দেশীয় ভাষার শব্দ আহরণ করতে শুরু করে। তৈরি হয় পিজিন এবং অতঃপর ক্রিয়োল।
তবে বাংলা ভাষার জন্মের ইতিহাস খানিকটা আলাদা। আদি-ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে বাংলার জন্ম। আজ থেকে প্রায় ৪৫০০ বছর আগে ইউক্রেন-রাশিয়া-কাজাখস্তানের মানুষ এ ভাষায় কথা বলতেন। অভিপ্রয়াণের কারণে ৩৫০০ বছর আগে এ ভাষা বেশ কয়েকটি ধারায় ভাগ হয়ে পড়ে, যার ভেতর আদি-ইন্দো-ইরানি ধারা অন্যতম। আর এ ধারা থেকেই বৈদিক চর্চার হাত ধরে আজ থেকে ১০০০ বছর আগে চর্যাপদ লেখার মধ্য দিয়ে আদি-বাংলার প্রথম আত্মপ্রকাশ। মনে রাখতে হবে, ঠিক একই সময় মুঘলদের আবির্ভাব ঘটেছিল ভারতীয় উপমহাদেশে। অর্থাৎ বাংলার জন্ম বৈদিক চর্চার সঙ্গে জড়িয়ে থাকলেও এর বিবর্তনে মুসলিম সংস্কৃতির ব্যাপক প্রভাব ছিল। অন্যদিকে, উর্দু ও ফার্সি ভাষাও আদি-ইন্দো-ইরানি ধারা থেকে উদ্ভূত। অর্থাৎ এ অঞ্চলের প্রায় সব ভাষার উৎস একই।
তাহলে একুশ জরুরি কেন? ভাষার এ মাস, একুশের গুরুত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে ভাষার সঙ্গে সংস্কৃতির একাত্মতায়। বার্ট্রান্ড রাসেল ১৯৪০ সালে প্রকাশিত তার ‘অর্থবহতা ও সত্যের অনুসন্ধান’ গ্রন্থে ভাষা কীভাবে সামাজিক অর্থ তৈরি করে এবং সত্য সম্পর্কে মানুষের ধারণাকে প্রভাবিত করে, তা অন্বেষণ করেছেন। তিনি বলেছেন, ভাষা শুধু একটি সময়কে বা সে সময়ে ঘটে যাওয়া ঘটনাকে বর্ণনাই করে না বরং ভাষা সময় ও স্থানকে এবং সেখানে অবস্থিত পাত্র-পাত্রীর জীবনধারাকে প্রভাবিতও করে থাকে। যেমন ‘বিপ্লব’ বা ‘সংগ্রাম’-এ শব্দগুলো সময়ের দাবিতে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ ধারণ করতে পারে, যা সে সময়ের ঘটনাযজ্ঞে ঘৃতাহুতি হিসাবেও কাজ করতে সক্ষম। ভাষার ক্ষমতা তাই নিষ্ক্রিয় বর্ণনা-সর্বস্বতা থেকে সক্রিয় বিবর্তন ও সংস্কৃতি বিনির্মাণের উচ্চতায় উন্নীত হয়। আর এ কারণেই একটি গোষ্ঠীর জন্য তার ভাষার অস্তিত্ব বজায় থাকা ও তার বিকাশ অপরিহার্য।
বাংলা একটি প্রতিষ্ঠিত ভাষা। এ ভাষায় প্রায় ২৮ কোটি মানুষ কথা বলে। তবে ভাষাকে অবজ্ঞা করলে, ভাষার গুরুত্বকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে খর্ব করলে, ভাষাটির মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। আর ভাষার মৃত্যু অনিবার্যভাবে ডেকে নিয়ে আসে সংস্কৃতির বিলুপ্তি। ভাষা-মৃত্যুর প্রথম লক্ষণকে ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে ৬০-এর দশকে প্রদত্ত জশুয়া ফিশম্যানের ‘ল্যাংগুয়েজ শিফট থিওরি’ বা ‘ভাষার অপসরণ তত্ত্ব’ দিয়ে। ফিশম্যান বলছেন যে, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা বৈশ্বিক বলের টানে ভাষার ব্যবহারে শিফট লক্ষ করা যায়। এহেন শিফট শুধু প্রত্যক্ষ উপনিবেশ থেকে ঘটবে এমনটি নয়। যে কোনো ভাষাভাষীর মানুষ অভ্যন্তরীণ তাগিদ থেকেও ভাষা ব্যবহারে অনীহা দেখতে শুরু করতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দি বা ইংরেজি প্রিয়তা এ অঞ্চলে বাংলা ব্যবহারে অনাগ্রহের দৃষ্টান্ত ধারণ করে। হালে অনেক বাংলা লেখক পশ্চিম বাংলায় বাংলার চর্চাগত লঘুতায় আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন।
ফেব্রুয়ারির এই ভাষার মাসে তাই আমাদের উপলব্ধিগুলো কী হওয়া জরুরি? আমাদের সংকল্পই বা কী হতে পারে? একটি বিষয় এখন স্পষ্ট যে, ভাষাকে রাষ্ট্রীয় সীমানায় বাঁধা অসম্ভব। বাংলা ভাষা যখন আদি-ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা থেকে উৎসারিত, তখন আমাদের জাতীয় সীমানা দিয়ে একে বেঁধে, এ ভাষার চর্চায় নিয়োজিত লেখকদের ‘বাতিল’ করার প্রক্রিয়া বাতুলতা মাত্র। অন্যদিকে আন্তর্জাতিকতার তাগিদ থেকে বাংলাকে অবহেলা করা, ভাষা অপসরণের বা শিফটের দিকে যে বাংলাকে ঠেলে দেবে না তা বলা যায় না। ইংরেজি ভাষা শেখার প্রায়োগিক গুরুত্ব রয়েছে এবং থাকবে। তবে সে তাগিদ থেকে আমাদের স্বত্তার ধারক বাংলাকে অবহেলা করা সমীচীন নয়। বাংলা ভাষাকে ধর্মীয় ট্যাগ দেওয়া আরেকটি বড় ভুল। বাংলা ভাষার জন্ম বৈদিক হলেও এর বিকাশ ঘটেছে মুঘলদের মুসলিম চর্চায়। আজকের পূর্ণাঙ্গ এ বাংলা ভাষা তাই সব ধর্মের বাংলাদেশিদের। জাতীয় পর্যায়ে বাংলার ব্যবহার তাই কোনো রাজনৈতিক লক্ষ্য চরিতার্থ করার অস্ত্র হওয়া কাম্য নয়। বাংলা এ ভূখণ্ডের মানুষের পরিচিতির অন্যতম স্তম্ভ। এ ভাষা রক্ষার দায়িত্ব তাই আমাদেরই। আমার মায়ের ভাষা বাংলা আমার জীবনস্পন্দনের বহিঃপ্রকাশ, আমার সংস্কৃতির মূর্ত প্রকাশ। বাংলার বিকাশ ও এ ভাষাকে আমাদের পরিচয়ের অন্যতম ধারক হিসাবে পরিগ্রহ করা হোক ২০২৫-এর একুশের প্রতিজ্ঞা।

