
প্রিন্ট: ০৩ এপ্রিল ২০২৫, ১১:৪১ এএম
ভূমিকম্পের প্রবল ঝুঁকিতে দেশ
মুহূর্তেই লাখো মানুষের প্রাণহানির আশঙ্কা
পাকা দালানের ৩৫-৪০ শতাংশ ভূমিকম্প সহনীয় নয় * উচ্চ ঝুঁকিতে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট ও ময়মনসিংহ অঞ্চল
হক ফারুক আহমেদ
প্রকাশ: ৩০ মার্চ ২০২৫, ১২:০০ এএম
প্রিন্ট সংস্করণ
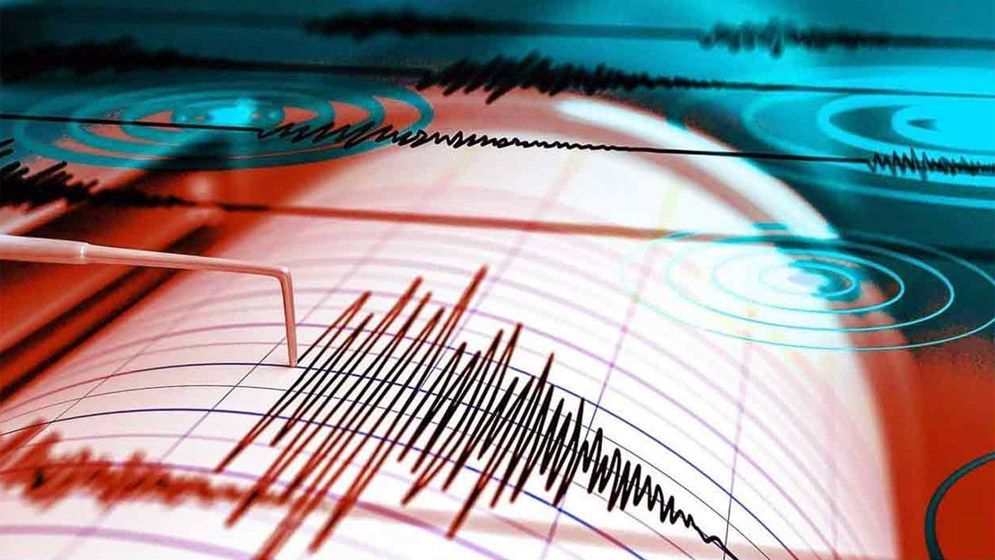
কয়েকদিন পরপরই কেঁপে উঠছে ঢাকাসহ সারা দেশ। এক মাসের মধ্যে ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে পাঁচবার। সবশেষ শুক্রবার দুপুর ১২টা ২১ মিনিটে ভূকম্পন অনুভূত হয়। এদিন মিয়ানমার ও থাইল্যান্ডে শক্তিশালী ভূমিকম্পে হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দেশ বারবার কেঁপে ওঠা বড় ভূমিকম্পের অশনিসংকেত হতে পারে। মিয়ানমারের মতো এখানেও ৭ থেকে ৭.৫ মাত্রার ভূমিকম্প হানা দিতে পারে যে কোনো সময়। তাতে ভয়ংকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। তাৎক্ষণিকভাবে মারা যেতে পারেন কয়েক লাখ মানুষ। এর অন্যতম কারণ-ঝুঁকিতে থাকা ভবনগুলো মেরামত না করা এবং যথাযথ সতর্কতা ব্যবস্থা না নেওয়া। দেশের পাকা দালানের মধ্যে ৩৫-৪০ ভাগ ভূমিকম্প সহনীয় নয়।
বিশেষজ্ঞরা জানান, প্রতি ১০০-১৫০ বছর পরপর ৭ মাত্রার ভূমিকম্প আসে। আর প্রতি ২৫০ থেকে ৩০০ বছর পরপর আসে ৮ মাত্রার ভূমিকম্প। ১৫০ বছরের সাইকেল হিসাবে বাংলাদেশে এখন ৭ মাত্রার ভূমিকম্প হওয়ার আশঙ্কা খুবই জোরালো হয়েছে।
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) পুরকৌশল বিভাগের অধ্যাপক ও বাংলাদেশ আর্থকোয়াক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারি ড. মেহেদী আহমেদ আনসারী যুগান্তরকে বলেন, দুটো থিওরি আছে। ছোট ছোট ভূমিকম্প হলে বড় ভূমিকম্প নাও হতে পারে। আবার বড় ঝাঁকুনির প্রস্তুতি হিসাবে ছোট ছোট ভূমিকম্প হয়ে থাকে। প্রশ্ন হলো আমরা কোনটা বিবেচনায় নিয়ে এগোব? আমাদের তো অবশ্যই সতর্ক পদক্ষেপ নিতে হবে। বড় ভূমিকম্পের প্রস্তুতি যদি নিই তাহলে আমরা ঝুঁকিমুক্ত। কিন্তু আমরা যদি মনে করি ছোট ছোট ভূমিকম্প হচ্ছে, তাই বড় ভূমিকম্প হবে না, আর সত্যিই যদি বড় ভূমিকম্প হয়েই যায় তাহলে যে বিপর্যয় নেমে আসবে তা কল্পনা করাও অসম্ভব।
এ বিশেষজ্ঞ বলেন, তুরস্কে ২০২৩-এর ৬ ফেব্রুয়ারি পরপর দুটি ভূমিকম্প হয়েছে। একটি ৭.৫ এবং আরেকটি ৭.৬ মাত্রার। সেখানকার মূল শহর থেকে ৫০০ কিমি. দূরে একটি শহরেই মারা গেছেন ৫৫ হাজার মানুষ। পাশেই সিরিয়াতে আরেকটি শহরে ১০ হাজার মানুষ মারা গেছেন। কারণ বিল্ডিং কোড না মেনে বিল্ডিং করা হয়েছিল। এরদোগানকে তাদের সাংবাদিকরা তখন শক্তভাবে ধরেছিলেন। টার্কির যে জনঘনত্ব তার চেয়ে ঢাকার জনঘনত্ব ১০-১৫ গুণ বেশি। সে হিসাবে আমাদের প্রাণহানি আরও অনেক বেশি হবে।
ড. মেহেদী আহমেদ আনসারী বলেন, আমরা সাড়ে তিন হাজার ভবনকে ভূমিকম্পে কতটা ঝুঁকিপূর্ণ তা পরীক্ষা করে লাল, আম্বার, হলুদ ও সবুজ হিসাবে চিহ্নত করেছিলাম। তাতে দেশে গার্মেন্টসের পাকা দালানের মধ্যে ৩৫ শতাংশ ভবনকে ঝুঁকিপূর্ণ পেয়েছিলাম। সম্প্রতি দেশের স্কুল বিল্ডিংয়ের মধ্যেও আমরা ৩৫ শতাংশ ভূমিকম্পের জন্য সহনীয় পাইনি। তাতে আমরা ধারণা করতে পারি যে, দেশে মোট পাকা দালানের ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশ ভূমিকম্পের প্রবল ঝুঁকিতে আছে। তিনি বলেন, এ বিষয়ে সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে। জনগণকে সম্পৃক্ত করতে হবে। যার যার ফ্ল্যাট বা বিল্ডিং ইঞ্জিনিয়ারের মাধ্যমে রেক্টিফাই করে নিলেই পরিষ্কার হয়ে যায় যে, কোন কোন বিল্ডিং ভূমিকম্প সহনীয় নয়। সেই রিপোর্ট যথাযথ কর্তৃপক্ষ বা রাজউককে দিলেই কাজটি হয়ে যায়। একটি ফ্ল্যাট রেক্টিফাই করতে ৫০ হাজার টাকার বেশি খরচ হবে না।
ভূতাত্ত্বিক দিক থেকে বাংলাদেশ তিনটি প্লেটের সংযোগস্থলে অবস্থিত। কলম্বো বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায় দেখা যায়, এ অঞ্চলে ভূগর্ভে দুটি প্লেট ধাবিত হচ্ছে। ইন্ডিয়া প্লেট পূর্বদিকে যাচ্ছে। বার্মা (মিয়ানমার) প্লেট পশ্চিমের দিকে আসছে। বার্মা প্লেটের নিচে ইন্ডিয়া প্লেট তলিয়ে যাচ্ছে। এটিকে বলে ‘সাবডাকশান জোন’। জিপিএসে পরিমাণ করে দেখা গেছে, প্রতিবছর ১ মিটার থেকে দেড় মিটার সংকোচন হচ্ছে। সে হিসাবে এখানে ৮.২ থেকে ৯ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্পন হওয়ার শক্তি সঞ্চিত হয়ে আছে। যে কোনো সময় এ ভূমিকম্প হতে পারে।
ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার যুগান্তরকে বলেন, এই মাত্রার ভূমিকম্প হলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে ঢাকা নগরী। অপরিকল্পিত শহর এবং বিল্ডিং কোড মেনে অনেক স্থাপনা নির্মাণ না হওয়ায় এখানকার ১ শতাংশ বিল্ডিংও যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে তাৎক্ষণিকভাবে দুই লাখ লোকের প্রাণহানি ঘটবে। ৫-৭ লাখ মানুষ বিভিন্ন বিল্ডিংয়ে আটকা পড়বে। পরবর্তী সময়ে খাদ্যাভাব, অগ্নিকাণ্ডসহ নানা কারণে তাদেরও একটি বড় অংশের মারা যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।
এদিকে ২০০৮ সালে হাইকোর্টের নির্দেশে দেশে ভূমিকম্প হলে তার জন্য প্রস্তুতি কেমন-এ বিষয়ে একটি কমিটি করে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়। সেই কমিটি এখন কাজ করছে। হাইকোর্টের আরেক নির্দেশনায় ভূমিকম্প হলে পরিস্থিতি কীভাবে সামাল দেওয়া হবে, কী কী যন্ত্রপাতি আছে, নগরীকে কীভাবে আবার আবাসযোগ্য করা হবে-সেসব বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এসব বিষয়ে এরই মধ্যে দুটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। বর্তমানে ১২ কোটি টাকার আরেকটি প্রকল্প চলমান আছে। এসব প্রকল্পের মাধ্যমে ফায়ার সার্ভিস, সিভিল ডিফেন্স, আর্মড ফোর্সেস ডিভিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়। জানা যায়, দেশে এখন যে লেডার আছে, তা দিয়ে ২০তলা পর্যন্ত ওঠা যায়। ৬২ হাজারের টার্গেট নিয়ে এখন পর্যন্ত ৪৮ হাজার আরবান ভলান্টিয়ারকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে ভূমিকম্পের মতো দুর্যোগ হলে মানুষকে সেবা দেওয়ার জন্য।
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের পরিচালক (এমআইএম) নিতাই চন্দ্র দে সরকার যুগান্তরকে বলেন, যে কোনো সময় বড় ধরনের ভূমিকম্প হতে পারে-বিষয়টি অনেক আগে থেকেই বলা হয়েছে। আমরা সে বিবেচনায় রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট, তাৎক্ষণিকভাবে কী করা উচিত-সেসব বিষয়ে পরিকল্পনা করেছি। ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেটসহ রংপুর, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, নারায়ণগঞ্জের জন্য রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট করা হয়েছে।
এদিকে মিয়ানমার ও থাইল্যান্ডে ভূমিকম্পের পর বাংলাদেশেও ভূমিকম্পের আশঙ্কা রয়েছে বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স। বিশেষত চট্টগ্রাম, সিলেট, ময়মনসিংহ ও ঢাকা অঞ্চল উচ্চঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। শনিবার এক বিজ্ঞপ্তিতে সংস্থাটি দেশে ভূমিকম্প মোকাবিলায় সব পর্যায়ে পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ ও সচেতনতা তৈরির জন্য ৯টি বিষয়ে সতর্কতা জারি করেছে। সংস্থাটি বলেছে, বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড ২০২০ অনুযায়ী ভূমিকম্প প্রতিরোধী ভবন নির্মাণ করতে হবে। ঝুঁকিপূর্ণ ও পুরোনো ভবনগুলোর সংস্কার ও শক্তিশালী করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। সব বহুতল ও বাণিজ্যিক ভবনে অগ্নিপ্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। ইউটিলিটি সার্ভিস যেমন গ্যাস, পানি ও বিদ্যুতের লাইনের সঠিকতা নিশ্চিত করতে হবে। ভূমিকম্প চলাকালীন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি পর্যায়ে বিভিন্ন করণীয় সম্পর্কে নিয়মিত মহড়া অনুশীলন ও প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। জরুরি টেলিফোন নম্বর যেমন ফায়ার সার্ভিস, অ্যাম্বুলেন্স, পুলিশ, হাসাপাতাল ও অন্যান্য জরুরি নম্বর ব্যক্তিগত পর্যায়ের পাশাপাশি সব ভবন বা স্থাপনায় সংরক্ষণ এবং তা দৃশ্যমান স্থানে লিখে রাখতে হবে।






-67ee67f9e60f0.jpg)

-67ee670f4b240.jpg)
-67ee663ac549a.jpg)

-67ee6528a41cd.jpg)




