
প্রিন্ট: ১৭ এপ্রিল ২০২৫, ০১:৫৮ পিএম
বাংলা সনের কথা
আবদুল হাই শিকদার
প্রকাশ: ১৪ এপ্রিল ২০২৫, ১২:০০ এএম
প্রিন্ট সংস্করণ
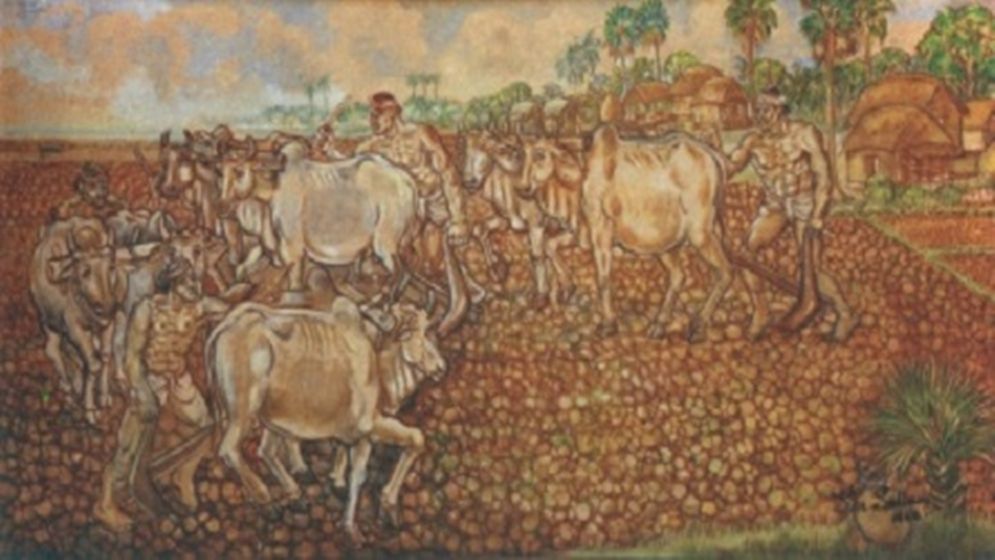
আরও পড়ুন
আমাদের জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি তথা জনজীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ বাংলা সন। বাংলা সনের জন্মের পেছনের রাজনীতি, অর্থনীতি ও কৃষকদের ফসল থেকে খাজনা আদায়ের লক্ষ্য জড়িত থাকলেও ধীরে ধীরে বাংলা সন আমাদের আবেগের স্থান দখল করে নিয়েছে। কৃষকদের জীর্ণ কুটির থেকে বাংলা সন এখন নাগরিক পান্তা-ইলিশ, শোভাযাত্রা, ফ্যাশনভূষিত হয়ে উঠেছে। ব্যবহারিক জীবনে বাংলা সন পাত্তা না পেলেও পহেলা বৈশাখে নাগরিকরা উৎসবে মেতে ওঠেন।
আমরা বাংলা সন নিয়ে উৎসব করি। আনন্দ করি। খানাপিনা করি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমাদের অবিমৃশ্যকারিতার জন্য, উদাসীনতার জন্য, এই বাংলা সনের জনক, প্রতিষ্ঠাতা ও সংস্কারকদের স্মরণ করি না। মিডিয়াও শিকড়ের সন্ধান দিতে রাখেনি কার্যকর ভূমিকা। সেজন্য শুরুতেই শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি সম্রাট আকবর, আমির ফতেহউল্লাহ সিরাজী, সম্রাট শাহজাহান ও ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহকে। তাদের কাছে আমাদের অশেষ ঋণ। তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা থেকেই তো বাংলা সন আজকের পৃথিবীর সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পেরেছে।
দুই
ফ্যাসিস্ট শাসকরা ইতিহাস নিয়ে যত পানি ঘোলা করেছে, ইতিহাসের নামে দলীয় ডগমা প্রচারের জন্য যত অখাদ্য উৎপাদন করেছে, তেমনটি বাংলা সনের বেলায় না হলেও নির্ভরশীল গবেষণাগ্রন্থের সংখ্যা খুবই সামান্য। এ সামান্য ক্ষেত্রে অসামান্য দ্যুতি বিস্তার করেছে অধ্যাপক আবূ তালিবের ‘বাংলা সনের জন্মকথা’, মোবারক আলী খানের ‘বাংলা সনের জন্মকথা’ এবং শামসুজ্জামান খান সম্পাদিত ‘বাংলা সন ও তার ঐতিহ্য’। আর সবার ওপরে আছে ঐতিহাসিক, মনীষী আবুল ফজলের ‘আকবারনামা’ ও আইন-ই-আকবরী।
বাংলা সন সম্পর্কে মোবারক আলী খান বলেন, ‘বাংলা সন পুরাণ কাহিনির Marmaid নামক সেই প্রাণীটির মতো, যার দেহের নিম্নাংশ মাছের মতো, ঊর্ধ্বাংশ সুন্দরী রমণীর মতো।’ বাংলা সনও তাই। তার ভিত্তি হিজরি সনের ওপর অথচ আকৃতি শকাব্দ শ্রেণির সৌর সনেরই মতো।
অধ্যাপক আবূ তালিব বলেন, ‘বাংলা ও হিজরি সন মূলত একই সন এবং একই সময়ে (৬২২ খ্রি.) একই উৎস থেকে উৎসারিত। শুধু যে হিজরি সনের সঙ্গে বিশ্বনবির হিজরতের স্মৃতিবিজড়িত তাই নয়, বাংলা সনের ইতিহাসের সঙ্গেও তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। বস্তুত হিজরি সনের একটা শাখারূপেই বাংলা সনের প্রতিষ্ঠা হয়েছে।’ মনে রাখা জরুরি, ‘জন্মকালের দিক দিয়ে বাংলা ও হিজরি সন সমবয়সি। অর্থাৎ ৬২২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে উভয়ের শুরু ধরা হয়েছে। এ বছর বিশ্বনবি হজরত মুহাম্মদ (সা.) কুরাইশদের অত্যাচারে জন্মভূমি মক্কা থেকে মদিনায় আশ্রয় নেন। এ গমনকে হিজরত বলা হয়। হিজরতের স্মৃতি রক্ষার্থে সনের প্রচলন করা হয় বলে একে হিজরি সন বলা হয়। হিজরতের ৯৬৩ বছর পর দিল্লির সম্রাট আকবর সিংহাসনে আরোহণ করেন। সম্রাটের সিংহাসন আরোহণের স্মৃতির সঙ্গে যুক্ত করে বাংলা সনের প্রতিষ্ঠা করা হয়। তাই এ সন একাধারে রাসুল্লাহর হিজরত (৬২২ খ্রি.) এবং আকবরের সিংহাসন আরোহণের (১৫৫৬) স্মারক হিসাবে উল্লেখযোগ্য। সম্রাট আকবরের সিংহাসন আরোহণের কাল হলো ৯৬৩ হিজরি অর্থাৎ ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দ। তাহলে দেখা যাচ্ছে, জন্মকাল থেকেই বাংলা সন খ্রিষ্টীয় সন থেকে ৫৯৩ বছরের অনুজ। তাই খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৫৯৩ বিয়োগ করলে বাংলা সন মেলে।
আজকের প্রজন্ম তো বটেই, প্রবীণদেরও হয়তো জানা নেই বাংলা সনের আগেও এ দেশে বেশ কয়েকটি সন প্রচলিত ছিল। এর অন্যতম ছিল লক্ষণাব্ধ, প্রগনাতি সন, মঘী সন, বিষ্ণুপুরী সন, সর্বসিদ্ধ সন, মিলিক সন, ত্রিপুরাব্দ ও চৈতন্যাব্দ সন।
আবার বাংলায় ফসলের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে খাজনা আদায়ের জন্য সম্রাট আকবর যে বাংলা সনেরই পত্তন করেন তা নয়। তিনি উড়িষ্যার জন্য আমলী সন, বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের জন্য বিলায়তী সন এবং মহারাষ্ট্রের জন্য সুরসন প্রবর্তন করেন। এ সনগুলোকেও ফসলি সনই বলা হয়। যেমন বাংলা সনকে বলা হয়।
বাংলা সনের আগে রাজস্ব আদায়ের ঝামেলা মেটানোর জন্য সম্রাট ‘ইলাহী সন’ নামে আরও একটা সন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু সেটা চলেনি। বিরক্ত সম্রাট চাইলেন ত্রুটিমুক্ত বিজ্ঞানসম্মত সন। যা জাতিধর্মনির্বিশেষে সবার জন্য আদর্শ হবে। বাংলা সন সম্রাটের প্রত্যাশা পূরণ করেছিল। কারণ বাংলা হিজরি থেকে উৎসারিত হলেও সে হিজরি নয়। আবার এর গঠন প্রক্রিয়ার সঙ্গে শকাব্দের মিল থাকলেও এটা শকাব্দ নয়। শকাব্দের সঙ্গে এর সম্পর্ক শুধু এটুকুই, এর মাস ও দিনের নাম সেখান থেকেই গৃহীত হয়েছে।
তিন
চাঁদ ও সূর্যকেন্দ্রিক সনের জটিলতা নিরসন এবং কৃষকের কাছ থেকে খাজনা আদায়ের সুবিধার্থে, তাদের ক্লেশ দূর করার জন্য অবশেষে সম্রাট আকবর শাহী ফরমান জারি করলেন, ‘যেহেতু ভারতে প্রচলিত সনগুলো সৌর পদ্ধতির এবং তার মাসগুলো চান্দ্র পদ্ধতির, তাই আমার নির্দেশ এই প্রস্তাবিত সনটি যেন পূর্ণাঙ্গ সৌর পদ্ধতির হয়।’ আকবরের এ আদেশের ওপর ভিত্তি করে শুরু হলো নতুন একটি সৌরসন সৃষ্টির কাজ।
সম্রাট এই সন সৃষ্টির জন্য খুঁজছিলেন যোগ্য মানুষ। সেই মানুষ হলেন সেই সময়কার ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী মহাপণ্ডিত আমির ফতেহউল্লাহ সিরাজী। সিরাজী ছিলেন বিজাপুরের সুলতানের সভাসদ। আকবর তাকে টেনে নেন নিজের কাছে। পরবর্তীকালে তার নবরত্ন সভার পরামর্শ মোতাবেক তার হাতেই বাংলা সন প্রবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেন সম্রাট ১৫৮৪ খ্রিষ্টাব্দে।
সিরাজী পাণ্ডিত্য সম্পর্কে ঐতিহাসিক আবুল ফজল লিখেছেন, ‘যদি এমন দুর্ঘটনা ঘটে যে, দেশের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো বিনষ্ট হয় আর সিরাজী সাহেব জীবিত থাকেন, তাহলে তিনি একাই তার পুনর্গঠন করতে সক্ষম হবেন।’ অধ্যাপক আবূ তালিব বলেন, ‘এহেন সিরাজী সাহেব রাজদরবারে এসে সম্রাটের নির্দেশে শুধু নবতর ইলাহী সনই প্রতিষ্ঠা করেন না, তিনি আদর্শ বাংলা সনসহ আরও কতিপয় নবতর সৌরসনের প্রতিষ্ঠা করেন।’ সবই ছিল ফসলি সন।
চার
আমির ফতেহউল্লাহ সিরাজীর প্রয়াসে বাংলার জন্য প্রবর্তিত হলো আজকের বাংলা সন। বাংলা সন প্রবর্তিত হয় ১৫৮৪ খ্রিষ্টাব্দে। প্রথম নাম তারিখ-ই-ইলাহী। ১৫৮৪ খ্রিষ্টাব্দের ১১ মার্চ এর নামকরণ করা হয় বংলা সন।
বাংলা সন গণনা শুরু হয় ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ৫ নভেম্বর থেকে। ২য় পানিপথের যুদ্ধে হিমুর বিরুদ্ধে আকবরের বিজয়কে স্মরণীয় করে রাখতে। একই সঙ্গে সম্রাটের সিংহাসন আরোহনের দিনটিকেও। সিরাজী হিজরি সনকে মডেল হিসাবে নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন। সেজন্য ৯৬৩ হিজরির মহররম মাস থেকে বাংলা বর্ষের ৯৬৩ অব্দের সূত্রপাত হয়। হিজরি মহররমের সঙ্গে বৈশাখের মিল থাকার জন্য প্রচলিত শকাব্দের চৈত্র মাসকে বাতিল করে বৈশাখকে করা হয় প্রথম মাস। আজ ৪৪৫ বছর পর হিজরি সনে বঙ্গাব্দের পার্থক্য দাঁড়াল ১৪ বছর।
যাত্রা শুরুর সময়ে গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারের সঙ্গে পার্থক্য ছিল ৫৯৩ বছর। অর্থাৎ বাংলা সনের সঙ্গে ৫৯৩ যোগ করলেও পাওয়া যাবে খ্রিষ্টাব্দ।
শুরুতে বাংলা মাসের ৩০ দিনের ৩০টা নাম ছিল। নামগুলো মনে রাখা ছিল কষ্টকর। এগিয়ে আসেন সম্রাট শাহজাহান। তিনি তার সময়ে বাংলা পঞ্জিকা সংস্কারে প্রথমবারের মতো হাত দেন। একজন পর্তুগিজ পণ্ডিতের সহায়তায় দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা সাপেক্ষে প্রতিটি মাসকে ৪টি ভাগ করে সূচনা করা হয় সপ্তাহের। প্রতিটি সপ্তাহ ৭ দিন। গ্রেগরিয়ান পদ্ধতিতে দিনগুলোর নামও ঠিক করা হয়। যেমন ঝঁহ থেকে রোববার। গড়ড়হ থেকে সোমবার ইত্যাদি।
সূচনালগ্নে মাসগুলোর নাম ছিল খোরদাদ, মেহের, শাহরিয়ার, ইসকান্দ এ রকমের। শাহজাহান পরে বিভিন্ন তারকা ও গ্রন্থের নাম থেকে শকাব্দ স্টাইলে মাসগুলোর নাম রাখেন বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ইত্যাদি।
বাংলা পঞ্জিকায় শাহজাহান যে যে বিপুল পরিবর্তন এনেছিলেন তাই চলে আসছিল শতকের পর শতক। বাংলা বর্ষপঞ্জি যদিও আমাদের নিজস্ব; কিন্তু বিশ্ব চলে খ্রিষ্টাব্দের পথ ধরে। বাংলা সনকে তার সঙ্গে সংগতি রাখা দরকার হয়ে পড়ে। বিশেষ করে লিপইয়ার ঝামেলা দূর করার এবং বাংলা সনকে যুগোপযোগী করার ভাবনা থেকেই ১৯৬৬ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকার ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর নেতৃত্বে গঠন করে দ্বিতীয় সংস্কার কমিটি। বাংলা সনের বর্তমান রূপটি এ কমিটিরই অবদান-যা এখন আমরা মেনে চলছি।
পহেলা বৈশাখ বাংলা নববর্ষের সূচনা করেছিলেন সম্রাট আকবর। তিনিই এ উৎসবের প্রতিষ্ঠাতা, সম্রাটই নির্ধারণ করে দেন শেষ চৈত্র হবে খাজনা পরিশোধের। ১ বৈশাখ দেশের মানুষ উৎসব করবে। হবে হালখাতা, জমে উঠবে মেলা, খেলা, নানাবিধ প্রদর্শনী। এর সঙ্গে যুক্ত হয় নানান লোকজ উপাদান, যেমন পুণ্যাহ, গাজনের গান, ঢোপবাড়ি খেলা, ভাড়াভুড়া খেলা, ঘোড়দৌড়, সঙখেলা, বারোয়ারী জারী ও তরকারী লাগানোর মতো বিষয়গুলো।
সম্রাট আকবর শুয়ে আছেন ফতেহপুর সিক্রিতে। সম্রাট শাহজাহানের কবর আগ্রার তাজমহলে। আর বাংলা সনের জনক শুয়ে আছেন আজকের নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায়। বাংলাকে ভালোবেসে এ দেশকে শেষ শয্যার জন্য বেছে নিয়েছিলেন সিরাজী। পরে স্থানটির নাম রাখা হয় ফতেহউল্লাহ। যা আজ ‘ফতুল্লা’য় নিমজ্জিত হয়েছে। তবে মাজারটি নিয়ে ভিন্নমতও আছে।
ড. শহীদুল্লাহর কবরটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদুল্লাহ হল প্রাঙ্গণে; বারো ভুঁইয়া নেতা বীর ঈসা খানের পুত্র মুসা খানের মসজিদ ও কবরের পাশে।
অবাক ব্যাপার, বাংলা সন আমরা উদযাপন করি, সভা-সেমিনার, শোভাযাত্রা, মেলা-সবই করি চারুকলা, শিল্পকলা, বাংলা একাডেমি, ছায়ানট এবং সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়-সব রঙিন হয়ে যায় উৎসবে। কিন্তু ভুলেও কেউ কখনো আকবর, সিরাজী, শাহজাহান কিংবা ড. শহীদুল্লাহর নামটি নেন না।
আবার ড. শহীদুল্লাহর সংস্কারকৃত ক্যালেন্ডার বিশ্বজুড়ে গৃহীত হলেও ভারতীয় বাঙালিরা এটা মানে না। তারা আঁকড়ে আছে শাহজাহানের জমানা। আর শকাব্দ।
তবে এ কথাও ঠিক, মুখে যতই আবেগ ঘনীভূত হোক, হৃদয় যতই উদ্বেল হোক, বাংলাদেশের বাঙালি ও ভারতীয় বাঙালি কেউই দৈনন্দিন জীবনে বাংলা সনকে অনুসরণ করে না। সেখানে একচ্ছত্র আধিপত্য খ্রিষ্টাব্দের।
