ইতিহাসের দর্শন : ভুয়া বনাম আসল ইতিহাস
আমীর খসরু
প্রকাশ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, ১২:০০ এএম
প্রিন্ট সংস্করণ
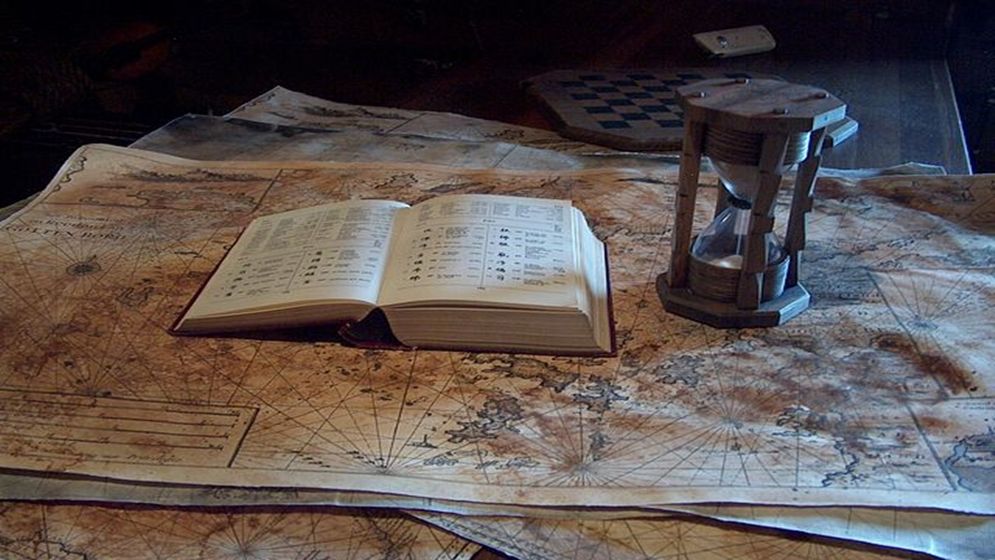
বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকটের স্বরূপ সন্ধানের প্রশ্নটির উত্তর এভাবেও দেওয়া যায়-অস্বাভাবিক পথে ‘রাজা যায়, রাজা আসে’। কিন্তু সংকট কি শুধুই একমাত্রিক? একমাত্রিক সংকটের বহুমাত্রিকতাই বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকটকে জটিল পরিস্থিতির দিকে নিয়ে গেছে। দায়ী কারা এবং সংকটগুলোর স্বরূপ অনুসন্ধান নির্মোহভাবে কখনোই করা হয়নি-অর্থাৎ হতে দেওয়া হয়নি। ইতিহাস প্রবহমান নদীর মতো। খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০ বছর আগে জ্ঞানী হিরাক্লিটাস বলেছিলেন, No one can step into the same river twice অর্থাৎ একই ঘটনা একইভাবে দ্বিতীয়বার ঘটবে না। এটাই হচ্ছে ইতিহাসের প্রথম পাঠ। বাংলাদেশের সংকটটি শুরু এখান থেকেই। ইতিহাসের গতিপথ জোরজবরদস্তিমূলকভাবে দখল করা হয়েছে অথবা গতিপথকে যে যার মতো পরিবর্তনে নিরন্তর চেষ্টা করেছে বা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে ইতিহাস-যা আর ইতিহাস থাকেনি। হয়ে গেছে ‘ব্যক্তিবিশেষের বীরত্বগাথা’ অথবা ‘ব্যক্তিগত পুঁথিপাঠ’।
এখানে সামগ্রিকতা নেই, সাধারণের সংযুক্তি নেই, আমরা নেই, আছে ব্যক্তি এবং ব্যক্তিবর্গ। ব্যক্তিগত পুঁথিপাঠের সংকটটি তৈরি করেছে-বিকলাঙ্গ এক ইতিহাসচর্চার। আগেই বলেছি, ইতিহাস প্রবহমান নদীর মতো, একে বাধা দিলে নদী নিজস্ব গতিপথ তৈরি করে অথবা শুকিয়ে যায়। বাংলাদেশের ইতিহাসচর্চাকেও সে পথে পরিচালনার যে সংকট, তা সৃষ্টি করেছে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সর্বোপরি পুরো সমাজ ও রাষ্ট্রের সংকটের। আর কখনোই স্বরূপ-সন্ধানকে বা এমন প্রচেষ্টাকে কখনোই সম্পন্ন হতে দেওয়া হয়নি। স্বাধীন ইতিহাসচর্চা ও ইতিহাসের দর্শনকে বাধাগ্রস্ত করে এমন একটি সমাজ তৈরি করা হয়েছে, যা সমাজেরই সৃষ্টি রাষ্ট্রকেও বিপন্ন করে তুলেছে। সমাজ যদি বিপন্ন-বিপদগ্রস্ত হয়, তবে রাষ্ট্র ওই গতিতেই বিপন্ন ও বিপদগ্রস্ত হতে বাধ্য। কারণ সমাজ রাষ্ট্র্র তৈরি করে-এর বিপরীতটি কখনোই নয়।
কী কারণে বাংলাদেশের সংকট তা পরে ধারাবাহিকভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হবে। তবে এর আগে ইতিহাস যে রাজা-রানী বা যুদ্ধের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, রাজা যায়, রাজা আসে’র মধ্যেই আবদ্ধ, তা নয়। ইতিহাসচর্চা ও ইতিহাসের দর্শন সম্পর্কে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমাদের প্রকৃত সত্য জানার ভিত্তি ও দিকটি সম্পর্কে জানতে হবে। দার্শনিক ফ্রেডরিক হেগেল-এর ব্যাখ্যা হচ্ছে, ইতিহাস হচ্ছে একটি সংগঠিত প্রমাণভিত্তিক উপস্থাপনা-যা ইতিহাস থেকে শেখার ভিত্তিভূমি তৈরিতে সহায়তা করে। (স্ট্যানফোর্ড এনসাইক্লোপেডিয়া অব ফিলোসফি)। হেগেলের ইতিহাস সম্পর্কে আরেকটি ব্যাখ্যা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। হেগেলের মত, ইতিহাস হচ্ছে-আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের মধ্যে স্বাধীনতার সত্যিকার বাস্তবায়ন। তিনি বলছেন, ইতিহাস হচ্ছে বিকাশের যৌক্তিক পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া এবং যারা যুক্তিসঙ্গতভাবে ইতিহাসকে দেখতে ইচ্ছুক-তাদের বোঝানো-যাতে সামগ্রিকভাবে, সুস্পষ্ট উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামগ্রিকতাকে যুক্ত করা যায়। আর এটি হবে ন্যায়নিষ্ঠ ও সততার সঙ্গে। (Philosophy of history : David Duquette : Oxford : 30 October, 2019)।
যে প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছিল, অর্থাৎ ইতিহাস কি রাজা-রানিসহ তাদেরই কীর্তিগাথা? না কখনোই না। জন-ইতহাসবিদ হাওয়ার্ড জিন-এর ‘এ পিপল্স হিস্ট্রি অব দ্য ইউনাইটেড স্টেইটসের প্রথম অধ্যায় অর্থাৎ কলম্বাস, দ্য ইন্ডিয়ানস অ্যান্ড হিউম্যান প্রগ্রেস অধ্যায়ে বলেছেন, যে কোনো দেশের ইতিহাস একটি পরিবারের ইতিহাস হিসাবেই তৈরি হয়; আর স্বার্থের ভয়ংকর দ্বন্দ্ব লুকিয়ে রাখা হয়। জিন বলছেন, ‘ইতিহাস লেখা হয়-বিজয়ী, সরকার, কূটনীতিক এবং নেতাদের দৃষ্টিকোণ থেকে। কিন্তু আসল ইতিহাস হচ্ছে, পরাজিত, নিপীড়িত, বঞ্চিত মানুষের জীবনগাথা। হাওয়ার্ড জিন বলছেন, অতীত বা ইতিহাস নিয়ে মিথ্যাচার করা তেমন একটা কঠিন কাজ নয়। আবার অপছন্দের মন্তব্য না শোনার জন্য সত্যিকে আড়াল করাও সহজ’।
তাহলে সত্য ইতিহাস কী? হাওয়ার্ড জিন বলছেন, ‘দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে, যাকে লজ্জাজনক মনে করা হয়, সেই লজ্জাজনক ইতিহাসকে সামনে আসতে দেওয়া হয়নি। দেখতে চাই না বলে আড়াল করে রাখা হয়েছে। এজন্যই আমরা ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে পারিনি। একই ভুল বারবার করা হচ্ছে। ন্যক্কারজনক ইতিহাসগুলোতে ইতিহাসবিদদের কম মনোযোগ দেওয়া বা কম গুরুত্ব দেওয়ার কুফল এটাই। সমস্যা হলো, মানুষ রাজনীতিকরা প্রেসের কথায় যতটা বিশ্বাস করে, এর চেয়ে কম করে একজন ইতিহাসবিদের কথায়।...আগ্রাসন, যুদ্ধ, গণহত্যার নাম দেওয়া হয়েছে প্রগতি। কারণ, ইতিহাস লিখেছে কলম্বাসের মতো আগ্রাসনকারী, সরকার, বীর আর নেতারা।...একজনের অবস্থা বা ভাবনাকে কোনোভাবেই ইতিহাস বলা যায় না, সবাইকে মিলেই ইতিহাস রচিত হয়। হেনরি কিসিঞ্জার তার প্রথম বই ‘অ্যা ওয়ার্ল্ড রিপোর্ট’-এ কিসিঞ্জার বলেছিলেন, ‘ইতিহাস হলো একটা পুরো দেশের স্মৃতি, কোনো ব্যক্তিবিশেষের নয়।’ ... একটা দেশ বা জাতির ইতিহাস মানে ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায়ের ইতিহাস নয়। একটা দেশের ইতিহাসের অর্থ হচ্ছে সেই দেশের সবার ইতিহাস; সব সম্প্রদায়; মালিক এবং দাসের ইতিহাস, পুঁজিপতি আর শ্রমিকের, সবল ও দুর্বলের, নারী-পুরুষ সবার ইতিহাস; দ্বন্দ্ব আর যুদ্ধের এ পৃথিবীতে শুধু বিজয়ীদের চোখে, তথাকথিত উন্নত বা অভিজাতদের চোখে ইতিহাসকে দেখা উচিত নয়। পরাজিতদের, আক্রান্তদের চোখেও দেখতে হবে; তাহলে অনেক অবিশ্বাস্য-অজানা বিষয় জানা যাবে, সামনেও চলে আসবে (হাওয়ার্ড জিন; এ পিপলস হিস্ট্রি অব দি ইউনাইটেড স্টেটস; অঙ্কুর প্রকাশনী; মে, ২০২৪; পৃঃ ৩৪-৩৬)।
এখানে মহান দার্শনিক ও সমাজতত্ত্ববিদ ইবনে খালদুন-এর ব্যাখ্যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। ইবনে খালদুন নিখুঁত রাষ্ট্রব্যবস্থার কথা বলেছেন একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে, তার বিখ্যাত গ্রন্থ আল-মুকাদ্দিমায়। খালদুন বলেছেন, “ধর্মীয় আইন বা কেউ পরকালে যাবেন বলে ন্যায় বা কল্যাণের প্রশ্নটি নয়। রাষ্ট্র একেবারেই নিখুঁত হবে তা-ও নয়। তবে, ন্যায়বিচার ও জনকল্যাণের জন্য একটি নিখুঁত রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রয়োজন। খালদুন মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন-যে রাষ্ট্র অত্যাচারী, জনসম্পত্তি কেড়ে নেয় এবং মানুষের অধিকার হরণ করে এমন রাষ্ট্র হচ্ছে ‘নিকৃষ্ট এবং অতিশয় খারাপ’। তিনি মনে করেন, একজন শাসকের পক্ষে ভালোবাসা এবং ভীত হওয়া উভয়ই সম্ভব না হলে-শাসক ভয়কে আলিঙ্গন করে তাকেই বেছে নেবে। কারণ, ভয় রাষ্ট্রের মধ্যে অনেক নেতিবাচক প্রভাব তৈরি করে।” (ইবনে খালদুন; আল-মুকাদ্দিমা; অনুবাদ-গোলাম সামদানী কোরায়শী; বাংলা সংস্করণ-২ খণ্ড; দিব্যপ্রকাশ; ফেব্রুয়ারি, ২০১৫)।
ইবনে খালদুন জনস্বার্থকামী, সর্বজনের সরকার ও রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে মানুষের জীবন-মৃত্যুর তুলনা করেছেন। তিনি বলছেন, রাষ্ট্রব্যবস্থার জীবনকাল রয়েছে ব্যক্তিদের মতো এবং প্রতিটি রাষ্ট্রের শেষ পর্যন্ত পতন ঘটবে।
কারণ, রাষ্ট্র সঠিক না হলে অসীম ক্ষমতা এবং মাত্রাহীন বিলাসিতা তাদের বিভ্রান্ত করে। অবশেষে রাষ্ট্রের সরকার নাগরিকদের ওপর কর আরোপ এবং সম্পত্তির মালিকানার অধিকারের ওপর অবিচার শুরু করে। এ অন্যায় পরিস্থিতি বা চক্র ওই রাষ্ট্র বা সভ্যতাকে ধ্বংস করে। আর এটি চলতে থাকে ক্রমাগতভাবে এবং চক্রাকারে। ইবনে খালদুন ইতিহাস সম্পর্কে একজন সমাজবিজ্ঞানী হিসাবে নির্মোহভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি হয়তো ইতিহাসের জনক হেরোডোটাস-এর দৃষ্টিভঙ্গি এবং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ গ্রহণ করেছিলেন। হেরোডোটাস-এর ইতিহাস সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে, ইতিহাস হলো নিয়মানুসারে পরীক্ষিত নানা তথ্যের সমাহার। প্রায় একই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে খালদুন বলছেন, ইতিহাস রচিত হয় বহু উৎস এবং অনেক বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করে। অবশ্য এর জন্য সর্বাত্মক চিন্তা এবং সত্যের কাছাকাছি যাতে পৌঁছানো যায়, কোনো ভুলত্রুটি যাতে না হয়, সে চেষ্টাটি করতে হবে। এ পদ্ধতিতে এবং পরম্পরা থেকে যেসব নীতি তৈরি হয়েছে, তার পরিষ্কার ধারণা যদি না থাকে এবং তুলনামূলক মূল্যায়ন যদি না করা যায়, তাহলে সে প্রচেষ্টা হোঁচট খাবে, পিছলে পড়বে এবং সত্যের পথ থেকে ইতিহাস বিচ্যুত হবে। (যশোবন্ত সিংহ; জিন্না, ভারত, দেশভাগ, স্বাধীনতা; আনন্দ পাবলিশার্স; কলকাতা, নভেম্বর, ২০০৯; পৃ. ৫)।
ইতিহাসের নানা ধরন এবং স্বরূপ নিয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে; কিন্তু ইতিহাসের সবই যে সহি বা সত্য, তা নয়। সবাই জানে বিষয়টি ভুল, কিন্তু লোককাহিনি এ ক্ষেত্রে বড় হয়ে ওঠে। এছাড়াও ধর্ম যে ইতিহাসের নির্ধারক সে বিষয়টিও আমাদের বিবেচনায় নিতে হবে। ইতিহাসবিদ অধ্যাপক রমিলা থাপার ইতিহাসকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকে। রমিলা থাপার বলছেন সোমনাথ মন্দিরের কথা। আর এ সোমনাথ মন্দির-খুবই পবিত্র হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে। অধ্যাপক রমিলা থাপার বলছেন, উত্তর ভারতে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত এসব কাহিনি বিজয়ের মহাকাব্য এবং প্রতিরোধের মহাকাব্য নামে, যা কিছুই থেকে থাকুক না কেন, উভয়কেই নাকচ করে দেয়। যত লোক তুর্কো-ফারসি ভাষ্য কিংবা রাজপুত মহাকাব্যগুলোকে সত্যনিষ্ঠ মনে করে, তাদের চেয়ে বেশিসংখ্যক মানুষ লোককাহিনিগুলোতে বিশ্বাস করে, মুখে মুখে প্রচলিত কাহিনিগুলো ঘটনাবলীর ব্যাপারে তাদের নিজস্ব ভাষ্য প্রদান করে, একইসঙ্গে অনেকের বক্তব্য নিজের মধ্যে টেনে নেওয়ায় এবং এ ধরনের কোনো সমাজ প্রতিষ্ঠা তার প্রধান উদ্বেগ নয়। এসব নথিপত্রে চিত্রিত সম্পর্কটি হিন্দু ও মুসলিম স্বার্থ হিসাবে অভিহিত সাধারণ শ্রেণির মাধ্যমে নির্ধারিত নয়। এগুলো আরও সুনির্দিষ্ট স্বার্থের আলোকে ভিন্নতা পায় এবং এগুলোর জাতিগত অবস্থান, অর্থনৈতিক উদ্বেগ, ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা ও সামাজিক মর্যাদাসহ অনেক পরিচিতি আকৃষ্ট করে। এসব পরিচিতিকে হিন্দু বা মুসলিম কোনো একক ধর্মে নামিয়ে আনা হলে অনেক কণ্ঠকে নির্বাক করে দেয়। এটি আসলে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে বিভাজন ঘটিয়েছে। আমরা জানতে চাইতে পারি, কীভাবে ও কখন এ ধরনের দ্বি-বিভাজন দানা বেঁধেছিল? এটা কি অন্যান্য ভাষ্যকে পাশাপাশি না রেখে আধুনিক ইতিহাসবিদদের একগুচ্ছ ভাষ্য খুব বেশি মাত্রায় আক্ষরিক অর্থে পাঠ করার কারণে ঘটেছে।...এটি আসলে ভাষ্যকারদের লেখা ১৯ ও ২০ শতকের ইতিহাসবিদরা বিরামহীনভাবে বারবার ব্যবহার করেছেন। এটি দি হিস্টোরি অব ইন্ডিয়া অ্যাজ টোল্ড বাই ইটস ওন হিস্টোরিয়ান্স-এর সম্পাদকদের অভিমতেও প্রতিফলিত হয়েছে। (রমিলা থাপার; সোমনাথ-এক ইতিহাসের অনেক ভাষ্য; বাংলায় ভাষান্তর মোহাম্মদ হাসান শরীফ; আবিষ্কার প্রকাশনী; ফেব্রুয়ারি, ২০২৫; পৃঃ ১৮১)
এসব ব্যাখ্যার আলোকে বলা যায়, বাংলাদেশের সহি ও সত্যিকার ইতিহাস ছিনতাই বা বেহাত হয়ে গেছে। ইতিহাসের গতিরোধ করা হয়েছে বারবার। আর এর মধ্য দিয়ে শাসকবর্গ সৃষ্টি করতে চেয়েছে এবং কিছুটা পেরেছেও-ভিন্ন একটি প্রজন্ম, যারা সত্যিকার ইতিহাস করতে পারবে না বা ভুলে যাবে সব। তারা ইতিহাস ‘গিলবে’-ইতিহাস জানবে না। ইতিহাসকে জোর করে খাওয়ানোকে ইতিহাসবিদ মেরি গ্লাবার বলছেন, ‘জাল অথবা ফেক ইতিহাস’-এর প্রজন্ম হিসাবে। জাল ইতিহাস রাজনীতিকে, মানুষের চিন্তা-মনন ও সামগ্রিকভাবে রাজনীতির বিকলাঙ্গ রূপকেই বাস্তবে আসল রূপ বলে ভাবতে হবে-এমন উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে এবং চলছে। এ কারণে বারবার সত্যিকার ইতিহাসকে হত্যা করা হয়েছে-ব্যক্তি, দলীয় বা গোষ্ঠীগত কারণে। কয়েকটি দৃষ্টিভঙ্গি এ কারণে উল্লেখযোগ্য বাংলাদেশের ক্ষেত্রে।
বাংলাদেশের ইতিহাসের শুরু কি ২৬ মার্চ কারও স্বাধীনতা ঘোষণা বা প্রোক্লামেশনের মধ্য দিয়ে, ৭ মার্চ ১৯৭১-এর জনসমাবেশে বক্তৃতা, ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১, ১৯৭৫-এর পট পরিবর্তনের মাধ্যমে, ১৯৫৭’র মওলানা ভাসানীর পশ্চিম পাকিস্তানকে শেষ বিদায় জানানোর মাধ্যমে, না ১৯৪৭ সালের পাকিস্তান সৃষ্টির মাধ্যমে? আসলে এ দেশের রয়েছে হাজার হাজার বছরের অস্তিত্ব ও ইতিহাস। স্বাধীনতার জন্য এ দেশের কৃষক বিদ্রোহ আছে, ফকির-সন্ন্যাসীসহ শতাধিক বিদ্রোহ আছে, অসংখ্য মানুষের জীবনদান এবং হাজারে হাজারে সাধারণ মানুষের আত্মাহুতি। সাধারণের ইতিহাস কখনোই ইতিহাস হয়ে ওঠে না বলেই গত ৫ বা ৬ দশকের বাংলাদেশের ‘হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালির’ দাবির মধ্য দিয়ে যে বৈপরীত্যের সৃষ্টি হয়েছে, সেটাই হচ্ছে সংকটের স্বরূপ, রাজনীতির মেরুকরণ বা বিভক্তির সৃষ্টি। স্বাধীনতার ঘোষণা বা মুক্তিযুদ্ধের প্রোক্লামেশন কে দিয়েছেন, সেসব বিতর্ক ও মহাবিভক্তির, মেরূকরণের সৃষ্টি করেছে-যা আখেরে বাংলাদেশের রাজনীতি ও ইতিহাসচর্চাকে ক্ষতিগ্রস্ত করাসহ পুরো দেশটির যারপরনাই ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
সঠিক ও সত্যিকার ইতিহাসচর্চা এ কারণেই বাধাগ্রস্ত বা গোঁজামিলের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ কি বাংলাদেশের আপামর জনগণের না কোনো দলের, এটা কি অন্য কোনো দেশের দয়ার দান এসব ইতিহাসগত প্রশ্নের মীমাংসা না করে যে কোনো রাজনৈতিক বন্দোবস্ত বা কাঠামো নির্মাণ টিকে থাকবে না, রাজা আসে, রাজা যায়-এর ইতিহাস হিসাবেই থেকে যাবে। এ বিবেচনা সামনে রেখে এবং স্থির-দৃঢ় মীমাংসার সামগ্রিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা না গেলে সংকট থেকে যাবে এবং বেড়ে যাবে।
বাংলাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সংকট নিরসনের জন্য এবং স্বাধীন-সার্বভৌমভাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর ভিত্তিভূমি তৈরির জন্য এ উদ্যোগটি নিতান্তই জরুরি। এখানে ইতিহাসচর্চার আরেকটি দিক আলোচনা জরুরি। আর তা হচ্ছে-প্রত্যেকটি মানুষই ইতিহাসের মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠে বা মানুষ ইতিহাসবেষ্টিত। তারা ইতিহাস শিখুক বা শিখতে আগ্রহী হোক, শাসকবর্গ তা চায় না। আরেকটি বিষয় জরুরি, তা হচ্ছে সমাজ এবং রাজনীতির বিষয়টির ক্ষেত্রে ইতিহাস অনিবার্য ভূমিকা পালন করে। এটি শুধু স্কুল-কলেজ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যেই আবদ্ধ নয় অথবা যারা ইতিহাবিদ তাদের বা ইতিহাসনির্ভর নাটক, সিনেমার বিষয়বস্তু নয়। সঠিক ইতিহাসের সহজলভ্যতা একান্তভাবে জরুরি। তবে সমাজের চিন্তার, বুদ্ধিবৃত্তি, স্বাধীন মতামত প্রকাশ বাধাগ্রস্ত হলে ইতিহাস যেমন বাধাগ্রস্ত হবে, দেশটির রাজনীতিও তেমনি বাধাগ্রস্ত হতে বাধ্য। আর এতে বৈকল্য দেখা দেবে-সমাজ, রাজনীতি, রাষ্ট্রসহ সব ক্ষেত্রে। শাসকবর্গ ইতিহাসকে বিকৃত করার জন্য নতুন একটি ধারা তৈরিতে সক্ষম হয়েছে। তা হচ্ছে-‘জনপ্রিয় ইতিহাস’। ইতিহাস হচ্ছে সত্য ও ন্যায়ভিত্তিক। তাকে বিকৃত করার লক্ষ্যে জনপ্রিয় ইতিহাসকে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার অগণতান্ত্রিক, স্বৈরাচারী ও ফ্যাসিস্ট শাসকবর্গ বা তাদের রাষ্ট্রটি অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশেই শুধু এ সমস্যাটি তৈরি হয়েছে বিষয়টি তা নয়-বিশ্বজুড়ে চলছে। তারা ভালো ইতিহাস বা খারাপ ইতিহাস বলে ইতিহাসের বিভাজন তৈরির মধ্য দিয়ে রাজনীতির সংকটকে ক্রমাগত বাড়িয়ে যাচ্ছে। জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির লক্ষ্যেই ‘এ প্রকল্পটি’ হাতে নেওয়া হয়েছে। আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে-জনপ্রিয় ইতিহাস ব্যক্তিবন্দনানির্ভর, সরলীকৃত এবং ইচ্ছাকৃত দোষত্রুটিযুক্ত। জনপ্রিয় ইতিহাসে ব্যক্তির বন্দনা আছে-সর্বজনের লড়াই-সংগ্রাম অনুপস্থিত, মানুষের টিকে থাকার সংগ্রাম, বেঁচে থাকার প্রবল প্রচেষ্টা অনুপস্থিত। শাসকবর্গ এটি ধরেই নেয়, মানুষ অতি সরলীকৃত পথেই যাবে। কিন্তু সঠিক এবং সত্যিকারের ইতিহাস সহজ ও সরলীকৃত পথে চলবে-এটা ধরে নেওয়ার কোনো কারণ নেই। জনপ্রিয় ইতিহাসের নায়ক সময় পরিক্রমায় আসল রূপে অর্থাৎ ইতিহাসের অ্যান্টি হিরো বা খলনায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে। ইতিহাসের বিকৃতি সাময়িক সংকট সৃষ্টি করলেও চিন্তা-বিবেক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে ইতিহাসের সত্যিকার পাটাতন তৈরি করবে। এ পাটাতন যত শক্ত হবে, সর্বজনের রাজনৈতিক শক্তি তত বেগবান হবে।
ষড়যন্ত্র তত্ত্ব গণতন্ত্রহীন সমাজ ও রাষ্ট্রে খুবই জনপ্রিয়। সঠিক ও সহি ইতিহাসের বড় শত্রু হচ্ছে এ ষড়যন্ত্র তত্ত্ব। ষড়যন্ত্র তত্ত্ব সর্বজনের মনোজগতে ত্বরিৎ প্রভাব ফেলে। জনপ্রিয় ইতিহাস প্রচার-প্রসারের উর্বরতা ঠিক এখানেই। যারা সর্বজনের মতো এবং ন্যায্যতাভিত্তিক রাজনৈতিক বোঝাপড়ায় শামিল-এ ষড়যন্ত্র তত্ত্বকে মোকাবিলার মধ্য দিয়ে ইতিহাসকে জন-ইতিহাসে রূপান্তর করতে পারার নিরন্তর লড়াই তাদের জারি রাখতে হবে।
বিদ্যমান ইতিহাসের নিজস্ব সংকটটি হচ্ছে-ইতিহাস বিজয়ীর পক্ষে। History is written by the winners অর্থাৎ ইতিহাস বিজয়ীদের দ্বারা লেখা হয়। এ মন্তব্যটির মালিকানা নিয়ে বিরোধ দেখা দেয় পরবর্তীকালে। সাধারণভাবে বলা হয়-মন্তব্যটি উইনস্টন চার্চিলের ১৯৪০ দশকের কোনো এক সময়ের। তবে প্রখ্যাত লেখক-১৯৮৪, Animal Farm-এর লেখক জর্জ অরওয়েল ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে ট্রিবিউন সংবাদপত্রে এ মন্তব্য লিখেছিলেন। অরওয়েল ওই সংবাদপত্রে নিয়মিত কলাম লিখতেন। আগেই বলা হয়েছে, ইতিহাস শাসকবর্গের-সাধারণের জীবনগাথা, সুখ-দুঃখ, জীবন-জীবিকা, তাদের সমাজ, নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা, রাজনীতি, অর্থনীতি সর্বোপরি তাদের কোনো কিছুই ইতিহাসে স্থান পায়নি। বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকটের স্বরূপ অনুসন্ধানের জন্য বিশ্ব পরিসরে এ বয়ান এবং উপলব্ধিগুলো সম্পর্কে জানাশোনা খুবই জরুরি।
কালজয়ী চলচ্চিত্র নির্মাতা-যাকে দার্শনিক না বললে অন্যায় হবে-সেই চার্লি চ্যাপলিন ১৯৪৭ সালে মিস্টার ভার্ডক্স (Monsieur Verdoxu) নামে একটি ব্লাক কমেডি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। যার চিত্রনাট্য ও পরিচালক ছিলেন চ্যাপলিন নিজেই। ছবির মূল চরিত্র মিস্টার ভার্ডক্স দোষীসাব্যস্ত হয়েছিলেন আদালতে একটি হত্যাকাণ্ডের জন্য। বিচারের প্রায় শেষে ভার্ডক্স-এর ডায়ালগটি হচ্ছে-‘প্রসিকিউটর অন্ততঃ স্বীকার করেছেন আমার মস্তিস্ক আছে। হ্যাঁ আছে।...একটি খুন করলে সে খলনায়ক। আর লক্ষ লক্ষ খুনের বিনিময়ে হওয়া যায় মহানায়ক। একজন গণহত্যাকারী হিসাবে বিশ্ব কি এই কাজকে উৎসাহিত করে না? গণহত্যার একমাত্র উদ্দেশ্য কি ধ্বংসাত্মক অস্ত্র নির্মাণ নয়? গণহত্যা কি সন্দেহাতীতভাবে-নারী ও ছোট ছোট শিশুদের টুকরো টুকরো করে ফেলেনি? এবং খুবই বিজ্ঞানসম্মতভাবে করেছে? গণহত্যাকারীর সঙ্গে আমাকে তুলনা করলে বলবো-আমি একজন অপেশাদার।’
ইতিহাস হচ্ছে, গণহত্যাকারী, অত্যাচারী বিজয়ীদের। বোধকরি অনেকেই দ্য ভিঞ্চি কোড চলচ্চিত্রটি দেখেছেন। চলচ্চিত্রটি নির্মিত হয় মার্কিন ঔপন্যাসিক ড্যান ব্রাউন-এর দ্য ভিঞ্চি কোড উপন্যাসটি ভিত্তি করে। উপন্যাসের এক পর্যায়ে বলা হয়-‘ইতিহাস সব সময় বিজয়ীদের দ্বারা লেখা হয়। যখন দুটি সংস্কৃতি, পক্ষ সংঘর্ষে লিপ্ত হয়-পরাজিত নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এবং বিজয়ী ইতিহাসের বইপুস্তক লেখে-যা তাদের নিজস্ব কারণ ও উদ্দেশ্যকে মহিমান্বিত করে এবং বিজয়ীর পক্ষ থেকে শত্রুকে অপমান করা হয়। যেমন নেপোলিয়ন একবার বলেছিলেন-‘ইতিহাস কি? কিছু কল্পকাহিনী মাত্র।’
এত গেল জ্ঞানী ব্যক্তিদের ইতিহাস নিয়ে বয়ান। কিছু ঘটনা বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে-ইতিহাস কিছু খলনায়ককে, নায়ক বানিয়ে দেয়, ইতিহাস মুছে ফেলা বা বিকৃতির মাধ্যমে। আমেরিকা আবিষ্কার নিয়ে জন-ইতিহাসবিদ হাওয়ার্ড জিনের ইতিহাস সম্পর্কে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি মনে হয় কোটি কোটি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছে এবং ভবিষ্যতেও পারবে। হাওয়ার্ড জিন ‘এ পিপলস হিস্ট্রি অব দ্য ইউনাইটেড স্টেটস’ বই-এর প্রথম অধ্যায় ‘কলম্বাস, ইন্ডিয়ান অ্যান্ড হিউম্যান প্রগ্রেস’ অধ্যায়ে কলম্বাসের সমুদ্রজয় সম্পর্কে ভিন্ন এক ইতিহাস-যা কিনা সত্যিকারের ইতিহাস, তা তুলে ধরা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ গোটা আমেরিকান দেশগুলোর শাসকবর্গ ক্রিস্টোফার কলম্বাসকে একজন বিজয়ী হিসাবে চিত্রিত করেছে। হাওয়ার্ড জিন স্পষ্ট করে বলেছেন, কলম্বাস ব্যক্তিগত জীবনের প্রথম দিকে ছিলেন ইতালির জেনোয়ারের এক ব্যবসায়ী অফিসের কেরানি, খণ্ডকালীন তাঁতি এবং একজন দক্ষ নাবিক। প্রথম দফায় তিনটি ছোট জাহাজে করে তিনি তৎকালীন ইন্ডিয়া বা ভারতসহ এশিয়ায় আসতে চেয়েছিলেন সমুদ্রপথে। এর আগে ইউরোপীয়রা বিশেষ করে পর্তুগিজরা এশিয়ায় আসার পথ জেনে গিয়েছিল। কিন্তু তুর্কিরা কন্সটান্টিনোপল ও ভূমধ্যসাগরের পূর্বাঞ্চল দখল করে ইউরোপীয়দের এশিয়ায় আসার পথ নিয়ন্ত্রণে নেয়। ইতালির কলম্বাস তখন স্পেনের হয়ে ভারত এবং এশিয়ায় আসার বিকল্প পথ অনুসন্ধানের লক্ষ্যে তিনটি জাহাজ নিয়ে বিপজ্জনক যাত্রা শুরু করেন। কিন্তু কলম্বাস যতটা সহজ ভেবেছিলেন, বাস্তব তত সহজ ছিল না। কলম্বাসের ছোট্ট জাহাজটি অর্থাৎ শান্তা মারিয়ার সহযাত্রী ছিল ৩৯ জন। দীর্ঘ যাত্রায় ক্লান্ত সবাই। কলম্বাস এশিয়ায় আসতে পারেননি। জীবনে ওই পথে এশিয়ায় আসা তার পক্ষে সম্ভবও ছিল না। কলম্বাস ১৪৯২ সালে ‘আবিষ্কার করলেন আমেরিকা অঞ্চল। একেবারেই অচেনা-অজানা মহাদেশ। স্পেনের সঙ্গে চুক্তি ছিল ভয়ংকর এ সমুদ্র যাত্রায় গন্তব্যে পৌঁছে যে ধনসম্পদ পাওয়া যাবে, তার ১০ শতাংশ পাবে কলম্বাস; আর নতুন জনপদের গভর্নর হবেন তিনি। এছাড়াও আরও তকমা জুটবে তার ভাগ্যে। কিন্তু সমুদ্র যাত্রার এক চতুর্থাংশ পথে তিনি পেয়ে গেলেন একটি দ্বীপ-যেখানে আদিবাসী আরাওয়াকরা বসতি স্থাপন করেছিলেন বহু আগে। কলম্বাস হতাশ হলেন। কিন্তু অপর এক নাবিক রড্রিগো দাবি করলেন, বাহামার দ্বীপটি তিনিই প্রথম দেখেছিলেন। কিন্তু কলম্বাসের দাবির মুখে হেরে গেলেন রড্রিগো। কলম্বাস নামমাত্র পুরস্কার বাবদ বছরে ১ হাজার মুদ্রা পাবেন। কিন্তু পরবর্তীকালে কলম্বাস দাবি করলেন, যে অচেনা-অজানা এলাকা তিনি আবিষ্কার করলেন, সেখানে স্বর্ণখনি আছে। ইতিহাসবিদগণ বলছেন, কলম্বাসের এ দাবির স্বপক্ষে তেমন কোনো প্রমাণাদি ছিল না। তিনি স্রেফ অনুমানের ওপর ভিত্তি করে এমন কাজটি করেছিলেন এই কারণে যে, তার আগের সমুদ্র যাত্রার ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়া। পরবর্তীকালে কলম্বাস নানা অত্যাচার-অনাচার করলেও স্বর্ণের দেখা মিলল না। তিনি পরে বাহামা, কিউবা ও হাইতি থেকে প্রত্যাশিত স্বর্ণ না পেয়ে ওইসব এলাকার আদিবাসীকে বন্দি করে দুটো জাহাজে করে রওয়ানা দিলেন স্পেনের পথে।
এভাবেই ইউরোপে শুরু হয় ভয়াবহ ক্রীতদাস ব্যবসা। এ দাস ব্যবসার জন্য পরবর্তীকালে ইউরোপীয়রা যে অত্যাচার, নির্যাতন, নিপীড়ন চালায়, তা শুনলে যে কারও গা শিউরে উঠবে। হাওয়ার্ড জিন বলছেন, ‘এভাবেই ৫শ’ বছর আগে শুরু হয়েছিল আমেরিকায় ইউরোপীয়দের ইতিহাস। কিন্তু এখন আমরা যখন ছোট ছোট শিশুদের যে ইতিহাস পড়তে দেওয়া হয়-সেখানে আছে কলম্বাসের বিজয়ের গল্প। সে ইতিহাসে কোনো দাসত্ব নেই, কোনো রক্তপাতের কথা নেই; শুধু বীরত্বপূর্ণ সমুদ্র অভিযানের ইতিহাস। কলম্বাস মহানায়ক। মার্কিনি দুনিয়ায় আজও কলম্বাসের আমেরিকা বিজয়ের দিবসও পালন করা হয়-যেখানে অন্য চরিত্রের কলম্বাস অনুপস্থিত। হাওয়ার্ড জিন আরেকজন ইতিহাসবিদ স্যামুয়েল এলিয়ট মরিসনের উদ্ধৃতি দিয়ে বলছেন, ‘কলম্বাস ও তার সঙ্গীরা দাসত্ব আর হত্যার যে পদ্ধতি অনুসরণ করেছিল, সেটি গণহত্যা ছাড়া আর কিছু নয়’। কলম্বাসদের এ গণহত্যাকে শাসকবর্গ নাম দিয়েছে-হিউম্যান প্রগ্রেস বা মানবজাতির প্রগতি হিসাবে। আর কলম্বাস হয়ে উঠেছেন ‘প্রগতির মহানায়ক’। অথচ এ আমেরিকাই নিজেদের দেশে আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চল এবং ইউরোপীয় গরিব দেশগুলো থেকে কালো মানুষদের বন্দি করে সীমাহীন নির্যাতন-নিপীড়ন করে ক্রীতদাসে পরিণত করে এবং শুরু হয় রমরমা দাসত্ব ব্যবসা। আর এ ব্যবসায়ীরা সমাজে প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। বিভিন্ন হিসাবে দেখা গেছে, কোটি কোটি ক্রীতদাসকে আমেরিকায় আসতে বাধ্য করা হয়েছিল।
হিস্ট্রি ডট কম-এর সম্পাদক এক দীর্ঘ নিবন্ধে দেখিয়েছেন, মিলিয়ন মিলিয়ন আফ্রিকান ক্রীতদাস মার্কিন আমেরিকার উন্নয়নে যথেষ্ট অবদান রেখেছিলেন এবং স্বাধীনতার পরে আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে বাধ্যতামূলক শ্রম দিতে অত্যাচার করা হচ্ছিল। আমেরিকান ও ইউরোপীয় ক্রীতদাস ব্যবসায়ীরা কমপক্ষে এক কোটি ২৫ লাখ আফ্রিকার ক্রীতদাসকে ওই অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকা থেকে আমেরিকায় যেতে বাধ্য করেছিল। ক্রীতদাস ব্যবসায়ীরা কতজন ক্রীতদাসকে নিয়ে এসেছিল, তার সঠিক কোনো হিসাব এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। খুব সতর্ক যে হিসাব পাওয়া যাচ্ছে, তাতে বলা হচ্ছে, ওই এক কোটি ২৫ লাখের মধ্যে এক কোটি ৭ লাখ ক্রীতদাস আমেরিকা পর্যন্ত পৌঁছাতে পেরেছিলেন। বাকিরা নিশ্চয়ই মৃত্যুবরণ বা হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছিলেন। নিশ্চয়ই মৃতের প্রকৃত সংখ্যা অনেক অনেক গুণে বেশি হবে। তাই এ হত্যা কি গণহত্যা নয়? যে হত্যা-নির্যাতন করা হয়েছিল তা কোন মানবিক প্রগতি? ক্রীতদাসদের এ কালো কাহিনি বা অধ্যায়টি নিয়ে শাসকগোষ্ঠী যত বেশি পারে তত বেশি চুপচাপ থাকে এবং অন্যদেরও মুখ বন্ধ করতে চায়, ইতিহাস পালটে দেয়।
আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, কুন্তা কিন্তের কথা। আফ্রিকান ক্রীতদাস কুন্তা কিন্তের ক্রীতদাস হয়ে আমেরিকায় শিকলবন্দি করে নিয়ে আসার ওপরে নির্ভর করে একটি বাস্তবভিত্তিক কাহিনি নিয়ে উন্যাস লেখেন অ্যালেক্স হ্যালি-‘Roots : The Saga of an American Family’। উপন্যাসটি ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত হয়। পরে টেলিভিশনে এ নিয়ে ধারাবাহিকভাবে একটি চলচ্চিত্র প্রচারিত হয়। কিন্তু এ নিয়ে আর তেমন কোনো লেখালেখি, নাটক, চলচ্চিত্র আর নির্মিত হয়নি। সম্ভবত আর হতে দেওয়া হয়নি। কিন্তু কুন্তা কিন্তেদের জন্য কোনো দিবস নেই, কোনো স্মরণসভা নেই। আছে কালো-সাদার বৈষম্য, ধনী-গরিবের অসম পার্থক্য, নিগ্রহ, ঘৃণা। এ কুন্তা কিন্তেদের ক্রীতদাস হওয়ার নির্মমতার বিষয়টি ইতিহাসকে হত্যা করার মধ্য দিয়ে সর্বজনকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ ১৭৭৫ থেকে ১৭৮৩ সাল পর্যন্ত আমেরিকার বিপ্লবী যুদ্ধে ৫ হাজার কালো ক্রীতদাস যোদ্ধা আমেরিকার পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন। একই কাজ করেছি ইউরোপীয় দেশগুলো। তারাও স্বীকার করতে নারাজ ক্রীতদাস ব্যবসা ও নির্যাতন-নিপীড়ন, অত্যাচার সম্পর্কে। এভাবেই ইতিহাসকে হত্যা করা হয়, নিয়ন্ত্রণ করা হয়-ইতিহাস, মানুষের মস্তিষ্ক এবং স্মরণশক্তি।
লেখক : গবেষক। ‘সংকটে গণতন্ত্র’ ও ‘সামরিক শাসন এবং বাংলাদেশের অনুন্নয়ন’ গ্রন্থের লেখক



