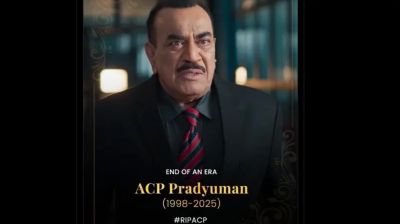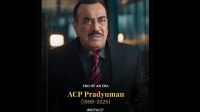প্রিন্ট: ০৬ এপ্রিল ২০২৫, ০৬:১৫ পিএম
রিজার্ভ বৃদ্ধির প্রয়াস অব্যাহত রাখতে হবে
ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী
প্রকাশ: ২৭ জুন ২০২৪, ১২:০০ এএম
প্রিন্ট সংস্করণ

সম্প্রতি দেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কিছুটা বেড়েছে। ২১ জুন গণমাধ্যমে প্রকাশিত বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যানুযায়ী, পবিত্র ঈদুল আজহার আগে ১২ জুন দেশে মোট রিজার্ভ ছিল ২ হাজার ৪৫২ কোটি মার্কিন ডলার। এক সপ্তাহের ব্যবধানে ২৬ কোটি ডলার বৃদ্ধি পেয়ে ১৯ জুন পর্যন্ত রিজার্ভ হয়েছে ২ হাজার ৪৭৮ কোটি ডলার। একই সময়ে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) হিসাব পদ্ধতি বিপিএম-৬ অনুসারে রিজার্ভ বেড়েছে ৩১ কোটি ৮২ লাখ ডলার। জুনের শুরুতে বিপিএম-৬ হিসাবে রিজার্ভ ছিল ১ হাজার ৮৭২ কোটি ডলার। এ হিসাব পদ্ধতি অনুযায়ী ১২ ও ১৯ জুন রিজার্ভ বেড়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ১ হাজার ৯২০ কোটি ৯৭ লাখ ডলার এবং ১ হাজার ৯৫২ কোটি ৭৯ লাখ ডলার। এছাড়া মের শুরুতে মোট রিজার্ভ ছিল ২ হাজার ৫৩৭ কোটি ডলার। দ্বিতীয় সপ্তাহে আমদানি বিল বাবদ রিজার্ভ থেকে এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নকে (আকু) ১৬৩ কোটি ডলার পরিশোধ করা হয়। ফলে ১৫ মে রিজার্ভ ২ হাজার ৩৯০ কোটি ডলারে নেমে আসে। ওই সময়ে বিপিএম-৬ অনুযায়ী রিজার্ভের পরিমাণ হয় ১ হাজার ৮৪২ কোটি ডলার। পরবর্তী পাঁচ সপ্তাহে রিজার্ভ বৃদ্ধির প্রবণতা আশাজাগানিয়া পর্যায়ে পৌঁছে।
এটি সর্বজনবিদিত যে, একটি দেশের আমদানি ব্যয় মেটানো, বাজেট বাস্তবায়ন, বৃহৎ প্রকল্পে অর্থের জোগান, বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ, আর্থিক বিপর্যয় মোকাবিলা, স্থানীয় মুদ্রার অবমূল্যায়ন রোধ, মুদ্রানীতি শক্তিশালীকরণসহ নানামুখী অর্থনৈতিক কর্মযজ্ঞে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অর্থনীতিবিদদের মতে, কোনো দেশে তিন মাসের মোট আমদানি ব্যয় মেটানোর মতো বৈদেশিক মুদ্রার মজুত থাকলে তা মোটামুটি নিরাপদ। আবার দীর্ঘদিন ধরে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ জমে থাকাও অর্থনীতির জন্য সুখকর নয়। অতিরিক্ত রিজার্ভ অর্থনীতি স্থবির হয়ে পড়া এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের গতি আশানুরূপ না হওয়াকেই ইঙ্গিত করে। দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধান খাত হচ্ছে-রপ্তানি আয়, প্রবাসীদের রেমিট্যান্স প্রবাহ, দাতা সংস্থা বা সহযোগী রাষ্ট্রের ঋণ-অনুদান ইত্যাদি।
বিশ্বব্যাংকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ১৯৭২ সালে মজুত স্বর্ণসহ সদ্য স্বাধীন যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল মাত্র ২৭ কোটি ৪ লাখ মার্কিন ডলার। ২০০০ সালের পর থেকে দেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধির দৃশ্যপট স্পষ্ট হতে থাকে। ২০০১-০২ অর্থবছরে ১৫০ কোটি ডলারের রিজার্ভের বিপরীতে ২০০৬-০৭ অর্থবছরে রিজার্ভ ৫০০ কোটি ডলারে উন্নীত হয়। ২০১২-১৩ অর্থবছর ছিল বাংলাদেশের রিজার্ভের ইতিহাসে স্মরণীয় বছর। ওই বছর রিজার্ভ ১৫০০ কোটি ডলারে উন্নীত হয়। ২০১৪ সালে বাংলাদেশ ২০০০ কোটি ডলারের রিজার্ভের মাইলফলক স্পর্শ করে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে রিজার্ভ দাঁড়ায় ২৫০০ কোটি ডলার এবং পরের বছরই তা ৩০০০ কোটি ডলারে উঠে যায়। এ হিসাবে মাত্র দুই বছরের ব্যবধানে বাংলাদেশের রিজার্ভ বাড়ে ১০০০ কোটি ডলার। পরবর্তীকালে ২০১৯-২০ অর্থবছরে রিজার্ভ ৩৬০০ কোটি ডলারে উপনীত হয়। করোনা মহামারির মধ্যেই ২০২১ সালের আগস্টে বাংলাদেশের রিজার্ভ উঠে যায় ৪৮০০ কোটি ডলারে। এখন পর্যন্ত এটিই বাংলাদেশের রিজার্ভের সর্বোচ্চ রেকর্ড।
কিন্তু কোভিড-পরবর্তী অর্থনৈতিক কার্যক্রমের স্বাভাবিক গতিশীলতা এবং রাশিয়া- ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানিসহ সব ধরনের পণ্যের মূল্য কয়েকগুণ বৃদ্ধি পায়। বেশি দামে পণ্য ক্রয়ে আমদানি ব্যয় বাড়লে রিজার্ভ কমতে শুরু করে। এরপর আর ঊর্ধ্বমুখী হয়নি রিজার্ভের পরিমাণ। করোনা-পরবর্তী সময় থেকে শুরু করে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, গাজা-ইসরাইল যুদ্ধ, ডলার সংকট, উন্নত বিশ্বের নীতি সুদহার বৃদ্ধিসহ নানা কারণে বিশ্ব অর্থব্যবস্থা এখনো টালমাটাল। প্রতিনিয়ত অস্ত্র ও জ্বালানির ব্যবহার এবং অনুৎপাদনশীল খাতে বিশ্বব্যাপী অসম বিনিয়োগ এক ধরনের নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি তৈরি করেছে। একদিকে উন্নত বিশ্বে অর্থের অপচয় এবং অন্যদিকে অনুন্নত বিশ্ব খাদ্য সংকটে নিপতিত। বিশেষ করে গাজা বা ফিলিস্তিনের গণমানুষের খাদ্যের আকুতিতে বা দুর্ভিক্ষ অবস্থায় পুরো বিশ্বের সভ্যসমাজ মর্মাহত। এতসব কঠিন চ্যালেঞ্জের মধ্যেও রিজার্ভ বৃদ্ধিতে আমাদের সরকার অপ্রয়োজনীয় আমদানি ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স পাঠানোকে উৎসাহিত করতে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ এবং রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখাসহ বেশকিছু পদক্ষেপ নেয়। বাজেটোত্তর সংবাদ সম্মেলনে মাননীয় অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়াতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।
আইএমএফ থেকে দ্রুত ঋণের অর্থছাড় এবং গৃহীত উদ্যোগের ফলে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার তহবিল বাড়বে। এতে অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ এ সূচকটির শক্তিশালী হওয়ার বার্তা মিলছে। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কারেন্সি সোয়াপ বা ডলার বন্ধক রাখা সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে। এরপর থেকে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো তারল্য সংকট মেটাতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে ডলার জমা রেখে টাকা ধার নেওয়া শুরু করে। ফেব্রুয়ারির মধ্যে এ প্রক্রিয়ায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকে ১২টি বাণিজ্যিক ব্যাংক ৫৮ কোটি ৮০ লাখ ডলার জমা রেখেছে। এর বিপরীতে এসব ব্যাংক টাকা ধার নিয়েছে ৬ হাজার কোটি টাকা। ব্যাংকসংশ্লিষ্টদের মতে, রেমিট্যান্স ও রপ্তানি কিছুটা বেড়েছে। একই সঙ্গে বেড়েছে আমদানিও। তবে রিজার্ভের পতন ঠেকানোর নেপথ্যে সোয়াপই মুখ্য ভূমিকা রাখছে। সাধারণত যাদের রেমিট্যান্স বেশি আসছে এবং যেসব ব্যাংকের তারল্যের সংকট রয়েছে, তারাই সোয়াপ করছে।
প্রসঙ্গত, সিপিডির সম্মানিত ফেলো গণমাধ্যমে জানিয়েছেন, ‘এই পদ্ধতির ফলে উভয়পক্ষের একটি অপশন বেড়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভ বাড়াতে ডলার প্রয়োজন আর ব্যাংকগুলোর বিনিয়োগ বাড়াতে দরকার টাকা। এখন যেসব ব্যাংকের কাছে অতিরিক্ত ডলার জমা থাকবে, তারা টাকা এনে বিনিয়োগ করবে। আবার যখন প্রয়োজন হবে টাকা জমা দিয়ে ডলার আনতে পারবে। তবে এ পদ্ধতি বর্তমানে খুব বেশি কাজে আসবে না। কারণ ব্যাংকের হাতে অতিরিক্ত ডলার আছে বলে মনে হয় না। অনেক ব্যাংক ডলার সংকটে এলসি খুলতে সমস্যায় পড়ছে।’
সর্বশেষ গত ৮ মে বাংলাদেশ ব্যাংক এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ক্রলিং পেগ পদ্ধতি চালু করেছে। এ পদ্ধতিতে ব্যাংকগুলোকে প্রায় ১১৭ টাকায় মার্কিন ডলার ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি দিয়েছে। এ ক্রলিং পেগ পদ্ধতি রিজার্ভ পুনর্গঠনে সহায়তা করবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে। পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (পিআরআই) নির্বাহী পরিচালক গণমাধ্যমে দেওয়া বক্তব্যে বলেছেন, ‘নতুন পদ্ধতির সফলতা নির্ভর করবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কতটুকু দক্ষতার সঙ্গে ও সফলভাবে তা বাস্তবায়ন করতে পারে তার ওপর। এদেশে বিভিন্ন সময় নতুন নতুন পদ্ধতি চালু করা হয়। কিন্তু সেগুলো যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হয় না। নীতিমালাটি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশ ব্যাংক নতুন উদ্যোগের প্রত্যাশিত ফল পেতে ছয় থেকে নয় মাস সময় লাগতে পারে।’ উল্লেখ্য, ক্রলিং পেগ হচ্ছে দেশীয় মুদ্রার সঙ্গে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার সমন্বয়ের একটি পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে মুদ্রার বিনিময় হারকে একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ওঠানামা করার সুযোগ দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে মুদ্রার দরের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন সীমা নির্ধারণ করা থাকে। ফলে মুদ্রাহার একবারে খুব বেশি বাড়তে পারে না, আবার কমতেও পারে না।
২০ জুন গণমাধ্যমে প্রকাশিত ওয়ার্ল্ড গোল্ড কাউন্সিলের (ডব্লিউজিসি) বার্ষিক জরিপের তথ্যমতে, বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভে ডলারের পরিমাণ কমে গিয়ে বাড়ছে সোনার পরিমাণ। এতদিন উদীয়মান অর্থনীতির দেশগুলোর মধ্যে এ প্রবণতা থাকলেও বর্তমানে উন্নত দেশগুলোও সেই পথে হাঁটছে। জরিপে অংশ নেওয়া বিশ্বের ধনী দেশগুলোর প্রায় ৬০ শতাংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ধারণা, আগামী পাঁচ বছরে তাদের মজুতে সোনার পরিমাণ অনেকটাই বাড়বে। গত বছর এমন ধারণা পোষণ করেছিল ৩৮ শতাংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংক। ওই জরিপ প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, বিশ্বের ধনী দেশগুলোর মধ্যে ৫৬ শতাংশ দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনুমান বৈশ্বিক রিজার্ভে সামষ্টিকভাবে মার্কিন ডলারের আধিপত্য কমবে। আগের বছর এমন বক্তব্য দিয়েছিল ৪৬ শতাংশ দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক। বিপরীতে উদীয়মান অর্থনীতির দেশগুলোর ৬৪ শতাংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ মতের পক্ষে রায় দেয়।
বিশ্লেষকদের অভিমত-চলতি বছর সোনার দাম বৃদ্ধির পেছনে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর এই সোনা মজুতের সম্পর্ক রয়েছে। মূলত রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক রাশিয়ার বিপুল পরিমাণ অর্থ জব্দ করার ফলস্বরূপ এ প্রবণতা বাড়ছে। পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র ডলারের বিনিময় হার বাড়িয়ে আমদানিকারক দেশগুলোকে যেভাবে বিপদে ফেলছে, সেই অভিজ্ঞতা থেকেও অনেক দেশ স্বর্ণ মজুতের দিকে ঝুঁকছে। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো তাদের রিজার্ভ বহুমুখী করছে। সার্বিক পর্যালোচনায় এটুকু বলা যায়, রিজার্ভ বৃদ্ধির নানামুখী প্রচেষ্টা দেশেও চলমান রয়েছে। ব্যয় সংকোচনে অধিকতর পরিকল্পিত পন্থা অনুসরণ করা হলে রিজার্ভ সমৃদ্ধির পথে এগোবে। মোদ্দা কথা, বৈদেশিক মুদ্রায় আয়-ব্যয়ে ভারসাম্য রক্ষায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকসহ সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর দক্ষ উদ্যোগ আবশ্যক।
ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী : শিক্ষাবিদ; সাবেক উপাচার্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়