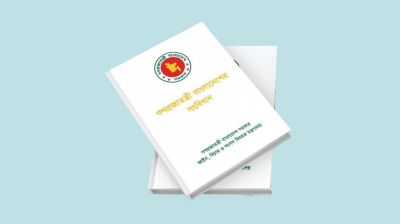প্রিন্ট: ০৪ এপ্রিল ২০২৫, ১১:০১ এএম
ড. আবু সাইয়িদ
প্রকাশ: ১৯ জুলাই ২০২৩, ১২:০০ এএম
প্রিন্ট সংস্করণ
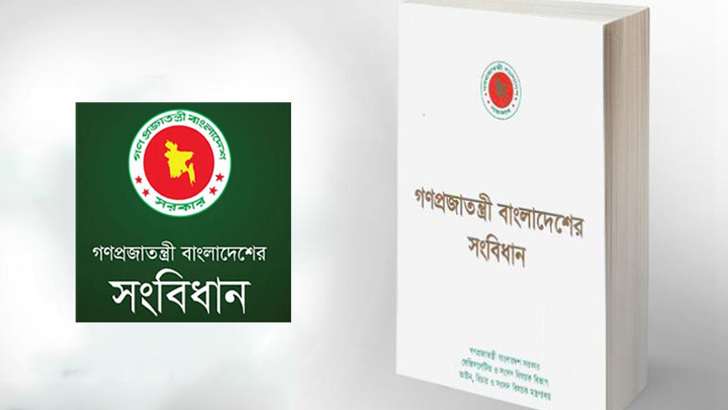
হাজার বছর ধরে লড়াই-সংগ্রাম করে আমরা স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছি। অঙ্গীকার ছিল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে একটি শোষণমুক্ত ও অসাম্প্রদায়িক সমাজ নির্মাণের। ‘আমরা’ অর্থাৎ জনগণ রাষ্ট্রের সব ক্ষমতার মালিক। সেই ক্ষমতার পরম অভিব্যক্তি প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন। সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকার গঠন করে।
আমাদের অভিজ্ঞতা হলো, কোনো দলীয় সরকারের অধীনে যত নির্বাচন হয়েছে, কোনো নির্বাচনকেই সুষ্ঠু বলে ধরা যায় না। এমনকি ’৭৩ সালের নির্বাচন নিয়েও মৃদু প্রশ্ন রয়েছে।’ ৭৫-পরবর্তী মার্শাল ল’র অধীনে যত নির্বাচন হয়েছে তা ছিল জনগণের সঙ্গে এক ধরনের ছলচাতুরী। ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর এরশাদ পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হন।
১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি তার অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বিএনপি বিজয়ী হয়। আওয়ামী লীগ বিরোধী দল হিসাবে সংসদে আসন গ্রহণ করে। ১৯৯৪ সালের ডিসেম্বরে আওয়ামী লীগের সব সংসদ-সদস্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে একযোগে স্পিকারের কাছে পদত্যাগ করেন। আওয়ামী লীগের জোরালো বক্তব্য ছিল, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া সুষ্ঠু নির্বাচন হয় না। ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি বিএনপি দলীয়ভাবে নির্বাচনের ঘোষণা দিলে সব রাজনৈতিক দল ওই নির্বাচন বর্জন করে। কিন্তু ১৫ ফেব্রুয়ারি যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তার আয়ু ছিল মাত্র ১১ কার্যদিবস। ওই সংসদে তত্ত্বাবধায়ক সরকার আইন পাশ হয়। ১৯৯৬ সালের ১২ জুন বিচারপতি হাবিবুর রহমানের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে জয়ী হয়ে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে। ২০০১ সালের ১ অক্টোবর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি লতিফুর রহমানের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বিএনপিসহ চারদলীয় জোট জয়লাভ করে। আওয়ামী লীগ ওই নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করে।
২০০২ সাল থেকে দেশে ধর্মান্ধ জঙ্গিবাদীদের উত্থান ঘটে এবং নাশকতায় জনজীবনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। জঙ্গি ‘বাংলাভাইয়ের’ উত্থান ঘটে। ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট জঙ্গি গ্রুপ শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগ নেতাদের প্রাণনাশের লক্ষ্যে গ্রেনেড হামলা চালায়। এ বীভৎস ঘটনায় ২৩ জন নিহত ও শত শত নেতাকর্মী আহত হন। এরপর সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ এএমএস কিবরিয়াকে হত্যা করা হয়। ২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট সারা দেশে একযোগে জেএমবি গ্রুপ বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়। ২০০৬ সালে রাস্তায় সংঘর্ষ অব্যাহত থাকে। তারপরের ইতিহাস ভিন্নরূপ। লগি-বৈঠা নিয়ে আওয়ামী লীগ মিছিল করে। জামায়াত বাধা দিলে সংঘর্ষ হয়। অরাজক পরিস্থিতির কারণে দেশে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়। ২০০৭ সালের ১২ জানুয়ারি ড. ফখরুদ্দীন আহমেদ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নিযুক্ত হন। এ সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে জয়ী হয়ে আওয়ামী লীগ ২০০৯ সালের ৬ জানুয়ারি সরকার গঠন করে।
এরপর দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের চিত্র কেমন ছিল তা দেখা যাক। ২০১৪ সালের নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ অর্থাৎ ১৫৩ প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। ৫২ শতাংশ ভোটার ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হন। এ নির্বাচন ছিল প্রহসন ও অগ্রহণযোগ্য। সরকার থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল, এটি নিয়ম রক্ষার নির্বাচন। নির্বাচনের পর এ প্রতিশ্রুতি পালিত হয়নি। ২০১৮ সালের নির্বাচনের কথা ধরা যাক। এ নির্বাচনকে ‘নিশিরাতের ভোট চুরি’র নির্বাচন বলে অনেককেই বলতে শোনা যায়। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও ছিল যন্ত্রণাদায়ক।
সংঘর্ষ নয় সংলাপ : এরূপ রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে জাতীয় নির্বাচন আরও জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। সরকারি দল বলছে, সংবিধান অনুযায়ী ‘বর্তমান সরকার ও সংবিধানের অধীনেই নির্বাচন।’ বিরোধী পক্ষ নির্দলীয় সরকারের দাবি তুলেছে। এ অবস্থায় সংবিধানের মধ্যে থেকে বিশেষজ্ঞরা একটি সমঝোতামূলক ফর্মুলা বের করতে পারেন কিনা তা দেখার জন্য জাতি সাগ্রহে তাকিয়ে আছে। এক্ষেত্রে আমার মতো নগণ্য ব্যক্তির অভিমত হলো, দুটি পক্ষই এমন ব্যবস্থা ও পরিবেশ সৃষ্টি করবে যেন ‘উইন-উইন’ মনোভাবে তুষ্টি বোধ করতে পারে। পরিবেশ সৃষ্টির দায়ভার সরকারের। সরকারের সদিচ্ছার কার্যকর বহিঃপ্রকাশ হিসাবে বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াসহ নেতাকর্মীদের ওপর মিথ্যা, গায়েবি মামলা, মামলায় আটক, গ্রেফতার ও সব নিপীড়নমূলক হয়রানি বন্ধ করা হবে আশু করণীয়। তাহলেই পারস্পরিক আস্থা, বিশ্বাস, সংলাপ ও সমঝোতার বাতাবরণ সৃষ্টি হবে।
সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কীভাবে : ক. বাংলাদেশে সংসদ নেতা অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী যেমন আছেন, সংসদ উপনেতাও আছেন। ‘The Leader of the house and the deputy leader are elected by a majority of the members of the parliament.’ দুজনই সংসদ কর্তৃক নির্বাচিত। সংবিধানের ৫৮(৪) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, সংসদ নেতা অর্থাৎ ‘প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করিলে বা স্বীয় পদে বহাল না থাকিলে মন্ত্রীদের প্রত্যেকে পদত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।’ সংসদ নেতার অবর্তমানে সংসদ উপনেতা প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন এবং শপথ নেবেন। সংসদ ভেঙে দেবেন। কিন্তু পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী না হওয়া পর্যন্ত তিনি স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। অতঃপর ওই প্রধানমন্ত্রী ১৯৯৬ সালের Rules of Business অনুযায়ী 3B(i) অনুসারে দেশের সৎ, বিবেকবান ও দক্ষ ব্যক্তিদের মধ্য থেকে সরকারি জোট ও বিরোধী জোটের সম্মতিতে প্রয়োজনীয় উপদেষ্টা নিয়োগ দেবেন। নির্বাচনকালীন ওই প্রধানমন্ত্রী উপদেষ্টা পরিষদে সভাপতিত্ব করবেন। রুটিনওয়ার্ক করবেন। উপদেষ্টারা সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে যথাযথ পদক্ষেপ নেবেন। খ. সংবিধানের ৭২ (১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, রাষ্ট্রপতি সরকারি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে সংসদ আহ্বান করতে পারবেন, স্থগিত করতে পারবেন ও ভঙ্গ করতে পারবেন। গ. সংবিধানের ১৪১ক। (১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, ‘অভ্যন্তরীণ গোলযোগের দ্বারা বাংলাদেশ বা উহার যে কোনো অংশের নিরাপত্তা বা অর্থনৈতিক জীবন বিপদের সম্মুখীন, তাহা হইলে তিনি (রাষ্ট্রপতি) জরুরি-অবস্থা ঘোষণা করতে পারিবেন।’ দুক্ষেত্রেই প্রধানমন্ত্রী প্রতিস্বাক্ষর করবেন। ঘ. সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করতে রিভিউ করতে পারেন।
নির্বাচন কমিশন : সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য গ্রহণযোগ্য ও দক্ষ একটি নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন অপরিহার্য। সেটি কীভাবে হতে পারে। ক্ষমতাসীন জোট ও আন্দোলনরত জোট সমঝোতার ভিত্তিতে প্রধান নির্বাচন কমিশন ও কমিশনারদের নিয়োগ প্রদানের জন্য রাষ্ট্রপতি বরাবর তাদের নাম পেশ করবে। রাষ্ট্রপতি তাদের নিয়োগ দেবেন। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ১৯৯৫ সালের ২৭ মে যখন বিরোধী দলে ছিলেন, তখন তিনি যথার্থভাবে দাবি তুলেছিলেন, প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিয়োগে বিরোধী দলের সঙ্গে আলোচনা করা হয়নি। তখন তার দাবির পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার পদত্যাগ করেন। বর্তমানে সেই রীতি অনুসরণ করা যেতে পারে। ভারতে নির্বাচন কমিশন নিয়োগের ক্ষেত্রে বিরোধী দলের সঙ্গে আলোচনার রীতি আছে। এক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন সংবিধানের ১১৯ (১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, ‘রাষ্ট্রপতি পদের ও সংসদের নির্বাচনের জন্য ‘ভোটার-তালিকা প্রস্তুতকরণের তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ এবং অনুরূপ নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত থাকিবে।’ ভারতের সংবিধানে ‘নিয়ন্ত্রণ’ শব্দটি বিদ্যমান, যা আমাদের সংবিধানে ১১৯(১)-এ যুক্ত আছে। বাংলাদেশ সংবিধানের ১১৮ (৪) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, ‘নির্বাচন কমিশন দায়িত্বপালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকিবেন এবং কেবল এই সংবিধান ও আইনের অধীন হইবেন।’ ভারতের সুপ্রিমকোর্টের রায় অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশেও তাই। সুষ্ঠু নির্র্বাচনের স্বার্থে যথাযোগ্য বিধিবিধান তৈরি ও কঠোরভাবে প্রয়োগ করবেন।
আমাদের মনে রাখতে হবে, ‘বাবার বাবা আছে, তারও দাদা আছে।’ জনগণ সার্বভৌম। ‘Will of the people is supreme। প্রয়োজনে দেশের অখণ্ডতা, জনজীবনের নিরাপত্তা ও সুষ্ঠু ভোট প্রদানের অবাধ স্বাধীনতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ‘ডকট্রিন অফ নেসেসিটি’র দ্বারস্থ হতে হবে। নইলে বর্তমান অবস্থায় ‘তালগাছটি আমার’ দুটি তীব্র ধাবমান শক্তির সংঘর্ষে যে ‘বজ্রপাত’ হবে, তাতে তালগাছটি চৌচির হয়ে যেতে পারে। দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হয়ে ব্যক্তিস্বার্থ ও দলীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে জনস্বার্থে জাগ্রত বিবেকের জয় হোক-এ কামনা করি।
ড. আবু সাইয়িদ : সাবেক তথ্য প্রতিমন্ত্রী