নতুন শিক্ষাক্রমে গুণগত শিক্ষা ও বুদ্ধির বিকাশ
সৈয়দ মো. গোলাম ফারুক
প্রকাশ: ১৩ জুন ২০২২, ১২:০০ এএম
প্রিন্ট সংস্করণ
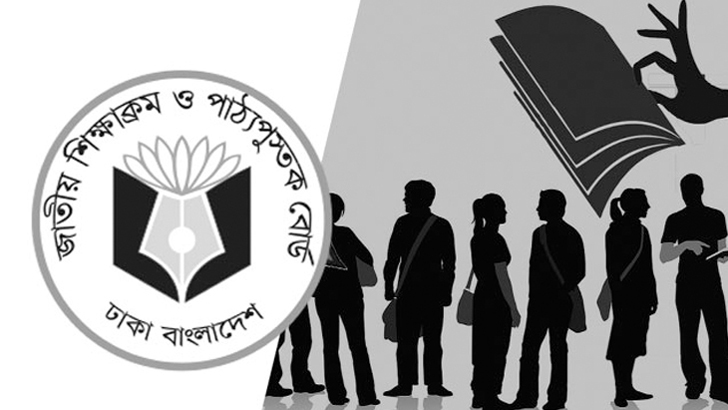
গুণগত শিক্ষা ও বুদ্ধি আসলে একে অপরের পরিপূরক। বুদ্ধি না থাকলে গুণগত শিক্ষা অর্জন সম্ভব নয়, আবার শিক্ষার্থীদের গুণগত শিক্ষা দিতে পারার অর্থই হচ্ছে তাদের আরও বেশি বুদ্ধিমান করে তোলা। সাধারণ শিক্ষাও বুদ্ধি বাড়ায়। আমরা যদি জেমস ফ্লিনের গবেষণা যেটা ‘ফ্লিন ইফেক্ট’ নামে পরিচিত সেটা দেখি, তাহলে দেখব অন্তত ১৯৪৭ সাল থেকে মানুষের বুদ্ধি দ্রুত বাড়ছে। হিসাব করে দেখা গেছে, এ সময়ের একজন টিনএজার যদি ১৯৫০ সালে আইকিউ টেস্ট দিত, তাহলে সে ১১৮ নম্বর পেত; আবার ওই একই পরীক্ষার্থী যদি ১৯১০ সালে পরীক্ষা দিত, তাহলে সে পেত ১৩০ নম্বর। সেই হিসাবে এখনকার একজন সাধারণ মানুষ ১৯১০ সালের ৯৮ শতাংশ মানুষের চাইতে বেশি বুদ্ধিমান।
বুদ্ধি বৃদ্ধির সঙ্গে শিক্ষার হারের সম্পর্ক আছে। বুদ্ধি বিশেষজ্ঞদের ধারণা, বুদ্ধি বাড়ার কারণ হচ্ছে, বৈজ্ঞানিক চশমা দিয়ে পৃথিবী দেখার প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়া। মানুষ এ বৈজ্ঞানিক চশমা মূলত স্কুল থেকেই পায়। বিংশ শতাব্দীর প্রায় পুরোটাজুড়ে শুধু যে বাচ্চাদের স্কুলে পাঠানোর প্রবণতা বেড়েছে তা নয়, ওদের এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি সময় সেখানে থাকতে হচ্ছে। যেমন ১৯০০ সালে আমেরিকানরা স্কুলে যেত চার থেকে সাত বছর এবং সেটা বাধ্যতামূলকও ছিল না। এখন সময়টাও বেড়েছে এবং তা বাধ্যতামূলকও করা হয়েছে।
শিক্ষার্থীরা যে এখন কেবল বেশি বেশি স্কুলে যাচ্ছে আর বেশি সময় স্কুলে থাকছে তাই নয়, শিক্ষায় গুণগত কিছু পরিবর্তনও এসেছে। আগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘শেষের কবিতার’ নবকৃষ্ণের মতো শিক্ষার্থীদের পড়তে হতো বিস্তর আর বুঝতে হতো অল্প। এ ক্ষেত্রেও অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে। এখনকার সব শিক্ষার্থী যে একেবারে শিক্ষার প্রতিটি ধাপ যথা ‘জ্ঞান’, ‘অনুধাবন’, ‘প্রয়োগ’, ‘সংশ্লেষণ’, ‘বিশ্লেষণ’ ও ‘সৃষ্টি’র স্তরগুলো একে একে পার হয়ে যাচ্ছে তা নয়। তবে অনেকেই যে অন্তত এর দ্বিতীয় ধাপ অর্থাৎ ‘অনুধাবন’ পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে সেটি নিশ্চিত করেই বলা যায়।
২০২৩ সাল থেকে নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা যে গুণগত শিক্ষার দিকে যাচ্ছি, তার লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীরা যেন ‘অনুধাবনে’ আটকে না থেকে একেবারে ষষ্ঠ ধাপ অর্থাৎ ‘সৃষ্টি’ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে সেই ব্যবস্থা করা। তা করতে হলে শিক্ষার্থীদের শুধু বৈজ্ঞানিক চশমা দিয়ে দিলে হবে না। তাদের বুদ্ধি বাড়ানোর জন্য আরও কিছু করতে হবে। সেই প্রসঙ্গে আসছি, তার আগে বুদ্ধি কীভাবে গুণগত শিক্ষায় প্রভাব ফেলে সেই বিষয়ে একটু আলোচনা করি।
গুণগত শিক্ষার একটা খুব বড় উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীদের সফট স্কিল যেমন সৃষ্টিশীলতা, সূক্ষ্ম চিন্তন দক্ষতা, খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা, নৈতিকতা, অন্যের মতো করে অনুভব করা, সহযোগিতা ইত্যাদিতে দক্ষ করে তোলা। এখানে সৃষ্টিশীল হতে হলে, সূক্ষ্ম চিন্তা করতে হলে, কিংবা খাপ খাইয়ে নিতে হলে যে বুদ্ধি লাগবে তা এমনিতেই বোঝা যায়। কিন্তু নৈতিক হতে হলে কিংবা অন্যের মন বুঝে তাকে সহযোগিতা করতে হলেও কি বুদ্ধি লাগবে? লাগবে, কারণ কিছু মূল্যবোধকে শুধু অন্ধভাবে অনুসরণ করলেই মানুষ নৈতিক হয় না। নৈতিক হতে হলে তাকে তার বাস্তবতা এবং তার নিজের আবেগকে বুঝতে হয়, এবং সেগুলোর সঙ্গে মূল্যবোধের একটা ঐকতান তৈরি করতে হয়। সেটা বুদ্ধি ছাড়া সম্ভব নয়। একইভাবে সহজাত দক্ষতায় আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব কিংবা একটা নির্দিষ্ট বৃত্তের বাইরে গিয়ে অন্য একজন মানুষের সহমর্মী হয়ে তার পাশে দাঁড়ানো কঠিন। এমনকি প্লেটোর মতো দার্শনিকের পক্ষেও এ বৃত্তটা খুব বেশি বড় করা সম্ভব হয়নি। প্লেটোর আগে গ্রিকদের সহমর্মিতার বৃত্ত নগর রাষ্ট্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। প্লেটো এ বৃত্তটি একটু বাড়িয়েছেন এই উপদেশ দিয়ে যে, কোনো গ্রিকের অন্য গ্রিকদের ওপর হামলা করা বা অন্য গ্রিকদের দাস বানানো উচিত নয়। তবে যারা গ্রিক নয়, তাদের হত্যা করা বা দাস বানানো দোষের কিছু নয়। তারপর একটা সময় এলো যখন ইউরোপিয়ানরা অন্য ইউরোপিয়ানদের দাস বানানো বন্ধ করে দিল; কিন্তু কেউ যদি আফ্রিকান হতো তাকে দাস বানাতে কোনো অসুবিধা ছিল না।
বুদ্ধির সঙ্গে যে সহমর্মিতার সম্পর্ক আছে, সেটা বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ এডাম স্মিথও লক্ষ করেছিলেন। তিনি তার বই ‘দি থিওরি অব মরাল সেন্টিমেন্টসে’ একটি হাইপোথেটিক্যাল অবস্থার কথা কল্পনা করেছেন। ধরুন আপনি জানলেন যে, একটা ভূমিকম্পে ১০০ মিলিয়ন চাইনিজ মারা গেছে। আপনি কী করবেন? আপনি হয়তো একটু দুঃখ প্রকাশ করবেন। মৃত ব্যক্তিদের জন্য হয়তো আপনার একটু খারাপ লাগবে। আপনি হয়তো একটা চেক লিখে তাদের একটু সাহায্য করার চেষ্টা করবেন। ব্যস এটুকুই। আপনি হয়তো এরপর আপনার কাজে ফিরে যাবেন। রাতের খাবার খেয়ে, একটু পায়চারি করে বিছানায় শুয়ে একটা রোমান্টিক বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়বেন। কিন্তু অনেক দূরে এত বড় একটা ঘটনা না ঘটে যদি আপনার নিজের জীবনে একটা ছোট্ট দুর্ঘটনা ঘটত? যেমন আপনার যদি একটা আঙুল কাটা যেত? তাহলে কি আপনি সবকিছু এত সহজে ভুলে যেতে পারতেন? এডাম স্মিথ বিষয়টিকে আর একটু অন্যভাবে দেখার চেষ্টা করলেন। ধরা যাক, আপনাকে দুটো অপশন দেওয়া হলো। ভূমিকম্পে লাখ লাখ মানুষ মারা যাওয়া আর আপনার একটা আঙুল কাটা যাওয়া। আপনি কোনটা বেছে নেবেন? স্মিথের ধারণা আপনি ঠিক নৈতিক কাজটিই করবেন। কিন্তু সেটি আপনি বুদ্ধি দিয়ে করবেন, সহজাত সহমর্মিতার বোধ দিয়ে নয়।
বোঝাই যাচ্ছে, গুণগত শিক্ষা অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিমান হতে হবে। কিন্তু প্রথাগত অঙ্ক, বিজ্ঞান বা অন্যান্য বিষয় পড়িয়ে ওদের কেবল এক ধরনের বুদ্ধিমত্তায় পরিবর্তন আনা সম্ভব, অন্যগুলো নয়। মানুষের বুদ্ধির আরও অনেক মাত্রা আছে। হার্ভার্ডের মনোবিজ্ঞানী হাওয়ার্ড গার্ডনার দাবি করেছেন, মানুষের অন্তত সাত রকম বুদ্ধি আছে, ভাষিক, সাংগিতিক, গাণিতিক, স্থানিক, কাইনেস্থেটিক, অন্তঃসম্পর্কীয় এবং আন্তঃসম্পর্কীয়। গার্ডনারের মতে এগুলো কম বেশি স্বাধীন, একটার ওপর আরেকটি নির্ভরশীল নয় এবং কোনোটাই অন্যটির চাইতে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। শিক্ষার্থীদের একেক জনের বুদ্ধি একেক ক্ষেত্রে বেশি থাকে। সেটি বুঝে ব্যবস্থা নিতে পারলেই তাদের বুদ্ধি দ্রুত বিকশিত হয়। এখনকার মতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যদি কেবল এক ধরনের বুদ্ধিচর্চা অব্যাহত থাকে, তাহলে শুধু অল্প কিছু শিক্ষার্থীর বুদ্ধিমত্তায় পরিবর্তন আসবে, অন্যরা পিছিয়ে পড়বে।
আশার কথা, নতুন শিক্ষাক্রমে উল্লিখিত সাত রকমের বুদ্ধির প্রতিটিকে বিকশিত ও শানিত করার বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে যেসব স্কুলে পাইলটিং চলছে, সেখানকার শিক্ষার্থীরা এখন খুব আনন্দ ও আগ্রহের সঙ্গে এসব বুদ্ধি চর্চায় নিমগ্ন। আগে মূলত ভাষিক ও গাণিতিক বুদ্ধিচর্চার সুযোগ ছিল। ফলে যেসব শিক্ষার্থীর এসব ক্ষেত্রে আগ্রহ ছিল, তারাই আনন্দ পেত বা ভালো করত, অন্যরা মনমরা হয়ে কষ্টে-সৃষ্টে পরীক্ষার বৈতরণী পার হতো। নতুন শিক্ষাক্রমে সবাই যেহেতু নিজের পছন্দমতো বুদ্ধিচর্চার সুযোগ পাবে, এখন ওইসব ক্লাসে এমন কাউকে পাওয়া দুষ্কর যে, স্কুলে যেতে কিংবা স্কুলে আরও বেশি সময় থাকতে চাইবে না। আশা করা যাচ্ছে, শিক্ষার্থীদের দিক থেকে নতুন শিক্ষাক্রমের কোনো সমস্যা থাকবে না। সমস্যা হবে শিক্ষক প্রশিক্ষণে। এ বছরের মধ্যে প্রায় সাড়ে চার লাখ শিক্ষককে অন্তত প্রাথমিক পর্যায়ের প্রশিক্ষণ তো দিতেই হবে, সামনের বছরও এ প্রশিক্ষণের কার্যক্রমটি অব্যাহত রেখে তাদের চৌকস করে তুলতে হবে। সেটি হলেই আমরা আসলে আমাদের শিক্ষার্থীদের বুদ্ধির বিকাশ ও গুণগত শিক্ষা অর্জনের পথ খুঁজে পেলাম কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারব।
সৈয়দ মো. গোলাম ফারুক : মাউশির সাবেক মহাপরিচালক, অধ্যাপক, ফলিত ভাষাতত্ত্ববিদ



