আসনে ও বসনে, মোরা এ কী বাঁধনে!
ড. সাখাওয়াৎ আনসারী
প্রকাশ: ২৯ ডিসেম্বর ২০১৯, ১২:০০ এএম
প্রিন্ট সংস্করণ
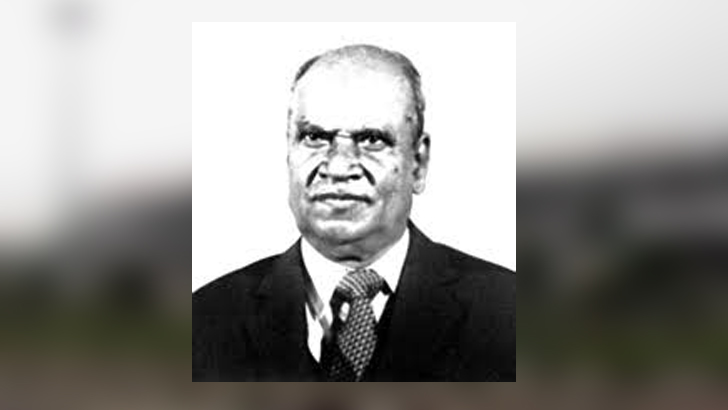
১৯৮১ সাল। বিচারপতি আবদুস সাত্তার তখন রাষ্ট্রপতি। ধামরাই হার্ডিঞ্জ উচ্চবিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত এক জনসভায় তিনি প্রধান অতিথি হিসেবে ভাষণ দেবেন। জনসভার আগের দিন কৌতূহলী হয়ে মাঠে গিয়ে দেখলাম, বিপুল কারুকার্যময় বিশালাকৃতির এক চেয়ার, যেটি অন্য সব চেয়ার থেকে ভিন্ন।
শুনলাম, চেয়ারটি আনা হয়েছে পঁচিশ মাইল দূরবর্তী ঢাকা শহর থেকে। পরের দিনের অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি সেটিতে বসবেন। কৌতূহলীদের কাউকে কাউকে চেয়ারটিকে স্পর্শ করে ধন্য হতে দেখলাম। দু-একজনকে দেখলাম এদিক-সেদিক তাকিয়ে নাক দিয়ে সেটিকে শুঁকতেও; রাষ্ট্রপতির চেয়ার বলে কথা!
দায়িত্বের অংশ হিসেবে বছরদুয়েক আগে যেতে হয়েছিল গোপালগঞ্জে; বঙ্গবন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়ে। আমাকে পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ আয়োজন করে এক সেমিনারের। আমি ছিলাম মূল বক্তা; বিষয়- ‘আবশ্যকীয় সর্বক্ষেত্রে বাংলা প্রচলনের সমস্যা ও করণীয়’। মঞ্চে রক্ষিত কয়েকটি চেয়ার, সব একই ধরনের। শুধু একটি চেয়ার ভিন্ন ধরনের, বৃহদাকৃতির; অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির জন্য। আকস্মিকভাবে জরুরি কাজ পড়ে যাওয়াতে ঢাকার পথে রওনা হওয়ায় ভিসি সেমিনারে উপস্থিত হতে পারলেন না। সেই অবস্থায় আয়োজক পক্ষ আমাকে ওই চেয়ারটিতে বসতে অনুরোধ জানালে আমি সবিনয় অপরাগতা প্রকাশ করি। আয়োজকরা বহু পীড়াপীড়ি করলেন। আমিও নাছোড়বান্দা। অবশেষে চেয়ারটি মঞ্চ থেকে সরিয়ে ফেলা হল; আমিও অসাধারণত্ববর্জিত সাধারণ চেয়ারেই বসলাম।
প্রাচীনকালে রাজা-বাদশাহরা সিংহাসনে বসতেন। এখন সিংহাসন নেই সত্য; কিন্তু ওই উচ্চাসনগুলো কি সিংহাসনেরই ধারাবাহিকতা নয়? এখন রাজতন্ত্র নেই। ওই আসনগুলো তো রাজতন্ত্রেরই স্মৃতিধারক, মানুষে মানুষে বৈষম্যসূচক। আমরা যদি বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন সংবিধানের ওপর দৃষ্টিনিক্ষেপ করি, তাহলে দেখব; মৌলিক অধিকার ভাগের ২৭ অনুচ্ছেদে সুস্পষ্ট ঘোষণা আছে- ‘সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান।’ সব নাগরিকের জন্য সামাজিক সাম্য নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য বলে ঘোষণা আছে সংবিধানের প্রস্তাবনা অংশে। মানুষে মানুষে সামাজিক অসাম্য বিলোপের জন্য রাষ্ট্রকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব দেয়া আছে এরই রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ভাগের ১৯ অনুচ্ছেদে। স্বাধীনতার আটচল্লিশ বছর পরও কি এমনটাই চলতে থাকবে?
নানা সভাস্থল-অনুষ্ঠানস্থল-দফতরে উচ্চাসনে যেমন বসেন মান্যবর রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রী-স্পিকার-মন্ত্রী-বিচারপতিরা, তেমনি বসেন প্রধান অতিথি-সভাপতিরাও। আদালতগুলোতে যে হাকিমরা বসেন, সে আদালতগুলো অধস্তন-ঊর্ধ্বতন যা-ই হোক না কেন, সেখানে সাধারণত মঞ্চ থাকেই। উচ্চমঞ্চে স্থাপিত আসন হওয়া সত্ত্বেও সেগুলো ন্যায়াসন। আইন বিজ্ঞানে বহুল প্রচলিত রয়েছে এমন একটি কথা যে, যিনি বিচারপ্রার্থী হবেন তাকে অবশ্যই পরিচ্ছন্ন হাতে আসতে হবে। বিচারপ্রার্থীকেই যদি এমন হতে হয়, তাহলে যিনি বিচার পরিচালনার মাধ্যমে ন্যায় ও সাম্য প্রতিষ্ঠা করবেন, তাকে কি মানুষ ন্যায় ও সাম্যের অংশীদার হিসেবে দেখতে চাইবে না? আমরা সবিনয় উল্লেখ করতে চাই, আমাদের বক্তব্য কোনো বিশেষ ব্যক্তিকে নিয়ে নয়। দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা প্রথার বিরুদ্ধে, ঔপনিবেশিক দাসত্বের বিরুদ্ধে, হীন শ্রেণিচেতনার বিরুদ্ধে।
জমিজমা নিবন্ধনের কাজটি যিনি করেন, তিনি সাবরেজিস্টার। এ দেশে সাবরেজিস্টাররাও বসেন উচ্চমঞ্চে স্থাপিত আসনে। হয়তো বা আসনটি শুধু উঁচু হওয়ার কারণেই গ্রামাঞ্চলের একটি বড়সংখ্যক মানুষ এদের ‘হাকিম’ বলেও সম্বোধন করেন, যা সম্পূর্ণই ভ্রান্ত। তাদের কাজের যে প্রকৃতি, তাতে আর দশটি দফতরের মতো চেয়ার-টেবিলই যথেষ্ট। দৃশ্যপ্রকৃতিতে এটি শ্রেণিভেদেরই পরিচায়ক।
রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রীর লালগালিচা সংবর্ধনার নবপ্রথা আশরাফি অবস্থানেরই নিদর্শনবাহী। রাজনৈতিক বিচারে এরা প্রভূত সম্মানী হলেও রাষ্ট্রখ্যাত বা ততোধিকখ্যাত কোনো দার্শনিক-সাহিত্যিক-বিজ্ঞানী-শিল্পী কিন্তু এত গালিচা-সংবর্ধনা পান না; তারা বঞ্চিত হন কুসুমাকীর্ণ সুবাসিত পথে হাঁটারও। তোরণে-তোরণে অভ্যর্থনাপ্রাপ্ত অথবা স্কুলের কোমলমতি বাচ্চাদের দ্বারা বরিত হওয়া রাষ্ট্রনেতা-নেত্রীরা কী সুন্দরভাবেই না শ্রেণি বৈষম্যকে আত্মতৃপ্তির সঙ্গেই লালন করে চলেছেন।
যে কোনো দফতর প্রধান ব্যবহৃত চেয়ারটি তার দর্শন বা সাক্ষাৎপ্রার্থীর চেয়ার থেকে গুণে-মানে উন্নততর। আমরা জানিই না অথবা ভুলে থাকি যে, দর্শনার্থী অতিথি। আর অতিথি বলেই তাদের জন্য নির্ধারিত অধোমানের চেয়ার তাদের অসম্মান ও অপমান করার শামিল। হিন্দুশাস্ত্রে তো অতিথিকে নারায়ণ তথা ভগবান হিসেবেই নির্দেশ করা হয়েছে। লিফটম্যান, গেটম্যানদের জন্য প্রায়ই দফতরপ্রধানরা নির্ধারণ করে দেন টুল; চেয়ার দিলে মালিক-প্রভুর আশরাফ-আতরাফ শ্রেণিভেদটি তো আর অক্ষুণ্ন থাকে না। ব্যক্তিগত গাড়ির মালিকদের দেখি, গাড়ি থামার পর তারা নিশ্চল-নির্ভীকার বসে আছেন; চালক নিজ আসন ছেড়ে ঘুরে এসে গাড়ির দরজা খুলে দিলে তবে মালিক-বাহাদুর ভূমিতে পদসঞ্চার করেন। কোমলাসনের এমনই গুণ।
আসন তো গেল, এবার কথা বসন নিয়ে। আমরা বাঙালি সংস্কৃতির কথা বলি, নিজস্ব কৃষ্টি-ঐতিহ্য-শেকড়ের কথা বলি; কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তা কি ধারণ করি? এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যে সমাবর্তন হয়, সেখানে ছাত্র-শিক্ষক থেকে শুরু করে সমাবর্তন বক্তা-ভিসি-আচার্য গাউন পরেন। এগুলো ইউরোপিয়ান নারীদের সেমিজ জাতীয় বহিঃপরিচ্ছদ বা ইউরোপিয়ান ব্যারন-শেরিফদের আলখেল্লা বিশেষ। প্রাচীন গ্রিক-রোমান উচ্চপদাধিকারী যোদ্ধাসহ নানা ব্যক্তি এ ধরনের পোশাক পরতেন। একুশ শতকের আধুনিক যুগে এসে আমরা পরসংস্কৃতির ধারক এ উদ্ভট পোশাকটি পরে যাচ্ছি। এটি এমনই এক পোশাক, যে পোশাকের একটিতেই ঢুকে পড়া যায় জনাদশেক। আর মাথায় টুপির (শিরস্ত্রাণ) কী ছিরি! আরও রয়েছে নানা ঝোলা-ঝাল্লা। এ প্রসঙ্গে আমরা স্মরণ করতে পারি বসন্তোৎসব বা নববর্ষের পোশাক। শান্তিনিকেতনে এ দুই উদযাপনে রবীন্দ্রনাথ ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রচলন করেছিলেন বিশেষ বর্ণের পাঞ্জাবি এবং শাড়ির। আবহমান বাংলার পুরুষ ও নারীর এ দুটি পরিচ্ছদ এখনও সমান চিত্তহরক ও নয়নাভিরাম।
পোশাকের সঙ্গে শ্রেণিভেদটিও নিতান্ত অলক্ষণীয় নয়। সরকারি-বেসরকারি নানা দফতরে নিয়োজিত পিয়ন-গেটম্যান-লিফটম্যান-আয়া-বাবুর্চিদেরও অনেক সময় নির্ধারিত রঙের পোশাক পরতে দেয়া হয়। এ ধরনের পোশাকের মাজেজা হল, কারও যেন বুঝতে অসুবিধা না হয় এরা নিম্নপদস্থ কর্মচারী। বিশেষ পোশাক যদি নির্ধারণ করতেই হয়, তবে তা সবার জন্য হওয়াই কি বাঞ্ছনীয় নয়? সবার জন্য একই পোশাক কি এ কারণেই করা হয় না যে, এতে শ্রেণিভেদটি অপসৃত হয়ে যায়?
কোট-টাইয়ের প্রচলন এ দেশে সম্ভবত ইংরেজদের আগমন থেকেই। বিলেত শীতপ্রধান দেশ বলে সেখানে এ ধরনের গরম বস্ত্রের প্রচলন। বাংলাদেশ শীতপ্রধান দেশ না হওয়া সত্ত্বেও অনেককেই এ দুয়ের প্রতি এতটাই মোহান্ধ দেখি যে, তারা ভাদ্রের তালপাকা গরমেও এগুলো পরে ঘুরে বেড়ান; কখনও কখনও কোটের নিচে একটি বাচ্চা কোটও পরেন। বাংলাদেশের ভিসিগোষ্ঠী ভিসি পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেন কোট-টাই পরিধানেরও সনদ পেয়ে যান, এগুলো যেন তাদের চর্মাবরণীর মতোই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।
টাই যে এখন ব্যাপক গণমানুষে ছড়িয়ে পড়েছে, তা আমরা চারপাশে হরহামেশাই দেখতে পাই। জীবন বীমা প্রতিনিধি, ওষুধ কোম্পানি প্রতিনিধি, অভিজাত হোটেল-রেস্তোরাঁর খাবার সরবরাহকারী, দূরপাল্লার গণপরিবহন সুপারভাইজারদের মধ্যে এর ব্যাপক ব্যবহার লক্ষণীয়। সেদিন শাহবাগে একজনকে দেখলাম টাই পরে দাঁতের মাজন বিক্রি করছেন। নিজ প্রসঙ্গের অবতারণা করে বলতে হয়, টাই পরা ছেড়েছি প্রায় দু’যুগ হয়। সে সময় থেকেই মনে হতে থাকে যে ‘টাই’ নামের যে গলাবন্ধটি পরি, তা ঔপনিবেশিক দাসত্বের স্মারকরজ্জু নয়তো? তখন থেকেই এ-ও আবিষ্কার করেছিলাম যে, প্রথম জীবনে কেউ কেউ পরলেও একটা সময়ে এসে বিদ্যাসাগর, জগদীশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, গান্ধী, চিত্তরঞ্জন, শেরেবাংলা, ভাসানী, নজরুল, বঙ্গবন্ধুর মতো অনেকেই টাই পরা ছেড়ে দিয়েছিলেন। অনেকে হয়তো কখনই পরেননি। এরাও কি ভেবেছিলেন যে, এটি তারাই এ দেশে বহন করে এনেছিলেন, যারা একশ’ নব্বই বছর ধরে এ দেশের মানুষকে শাসন, শোষণ ও নির্যাতন করেছিলেন?
কাউকে আঘাত করা এ লেখার উদ্দেশ্য নয়। এ লেখার উদ্দেশ্য একটিই- আসনে ও বসনে যে শ্রেণিভেদ এবং পরসংস্কৃতিনির্ভরতা, তা যেন আমরা উপলব্ধি করতে পারি। প্রয়োজনে যেন পারি নিজেকে সংশোধন করতেও।
ড. সাখাওয়াৎ আনসারী : অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়



