
প্রিন্ট: ৩০ এপ্রিল ২০২৫, ০৯:১৩ পিএম
চিরবন্ধনে জাপান
মোহাম্মদ আবদুল মজিদ
প্রকাশ: ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯, ১২:০০ এএম
প্রিন্ট সংস্করণ
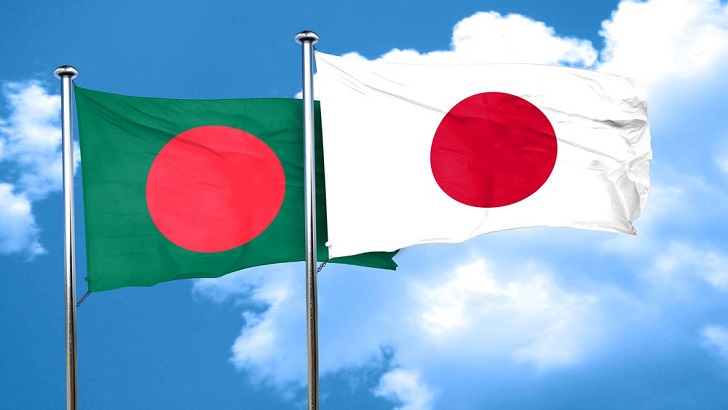
আরও পড়ুন
অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যস্বার্থ দু’দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের আধুনিক পর্যায়ে প্রাধান্য পেলেও বর্তমান সম্পর্কের ভিত্তি সুদীর্ঘ সময়ের গভীরে প্রোথিত। ওইসিডি সদস্য দেশগুলোর মধ্যে শিল্পোন্নত জাপানই সর্বপ্রথম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। ১৯৭২ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার সময় জাপান তখনও মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির প্রভাব বলয়েরই একটি দেশ।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি প্রতিরক্ষা চুক্তির বদৌলতে জাপান ওকিনাওয়া দ্বীপের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ফিরে পায় সে বছর। ১৯৭২ সালেই জাপানের সঙ্গে চীনের দীর্ঘদিনের বিরোধ প্রশমিত হয়ে সিনো-জাপান কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপরীত অবস্থান গ্রহণ করে।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো চীনও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে পাকিস্তানের মিত্র দেশ হিসেবে বিপরীত অবস্থানে ছিল। ঠিক এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে জাপান সরকার ও জনগণের সমর্থন এবং বিজয়ের অব্যবহিত পরে বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের সিদ্ধান্ত নিয়ে জাপান নিঃসন্দেহে তাৎপর্যবাহী ও সুদূরপ্রসারী কূটনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছে।
১৯৭০ সালের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ে অবর্ণনীয় ক্ষয়ক্ষতির সংবাদে এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের জনগণ তাকেশি হায়াকাওয়ার চিন্তাচেতনার কেন্দ্রবিন্দুতে আসে। জাপানের ডায়েটে প্রভাবশালী সদস্য হিসেবে হায়াকাওয়া বাংলাদেশের জনগণের মুক্তি সংগ্রামের প্রতি জাপানি জনগণ ও সরকারের সমর্থন সম্প্রসারণের নেপথ্যে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন।
১৯৭১ সালের মার্চে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে যে নৃশংস হত্যাযজ্ঞ শুরু করে, হায়াকাওয়া তার প্রতি জাপান সরকারের উদ্বেগ প্রকাশ এবং বিশেষ করে জাপানি জনগণের প্রতিবাদ জানানোর প্রেক্ষাপট তৈরিতে সাংগঠনিক উদ্যোগ নেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ জাপানি মিডিয়ায় বিশেষ গুরুত্ব পায়। বাংলাদেশের শরণার্থীদের সাহায্যার্থে অর্থ সংগ্রহ ও মুক্তিযুদ্ধের প্রতি জাপানিদের সমর্থন সমন্বয়ে জাপানের বুদ্ধিজীবী, শিল্পমালিক, শ্রমিক, ছাত্রসমাজকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে ছিলেন তিনি।
সে সময় জাপান প্রবাসী পূর্ব পাকিস্তানিদের প্রয়াস-প্রচেষ্টার সঙ্গেও একাত্ম হয়েছিলেন হায়াকাওয়া। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমেরিকা বলয়ের দেশ হওয়া সত্ত্বেও উন্নত বিশ্বের শিল্প সমৃদ্ধ দেশগুলোর মধ্যে জাপানই প্রথম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়, তারই প্রচেষ্টায় ১৯৭২ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি। স্বীকৃতিদানের এক মাসের মধ্যে ঢাকায় জাপানি দূতাবাসের কার্যক্রম শুরু হয় এবং ১৩-১৪ মার্চ হায়াকাওয়ার নেতৃত্বে তিন সদস্যের জাপানি সংসদীয় প্রতিনিধি দল প্রথম বাংলাদেশ সফরে আসেন।
দেশে ফিরে ২৪ মার্চ প্রধানমন্ত্রী সাতোর কাছে পেশ করা রিপোর্টে তিনি প্রস্তাব রাখেন ক. বাংলাদেশেকে ১০ মিলিয়ন ডলারের জরুরি অনুদান অবিলম্বে প্রদান এবং খ. পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের হিস্যা আদায়ে জাপানের মধ্যস্থতা। তার সুপারিশ অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী সাতোর নির্দেশে ২৮ মার্চ ১৯৭২ সালে জাপান বাংলাদেশে প্রথম অর্থনৈতিক সার্ভে মিশন পাঠায়। ওই বছর ৬ জুন জাপান-বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন এবং কিছুকাল পর জাপান-বাংলাদেশ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হলে হায়াকাওয়া তার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হন এবং আমৃত্যু এর নেতৃত্বে ছিলেন।
১৯৭৩ সালের অক্টোবরে জাপানে বাংলাদেশ থেকে শীর্ষ পর্যায়ের প্রথম সফরের সময় বাংলাদেশ-জাপান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদারের ক্ষেত্রে যে সুযোগ সৃষ্টি হয়, হায়াকাওয়া ছিলেন তার অন্যতম রূপকার। ১৯৭৩ সালের ১৬ ডিসেম্বর হায়াকাওয়া সস্ত্রীক বাংলাদেশ সফরে এলে রাষ্ট্রাচার উপেক্ষা করে বাংলাদেশের সরকারপ্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মন্ত্রিসভার সিনিয়র সদস্যদের নিয়ে পদ্মা গেস্ট হাউসে তার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও সম্মান প্রদর্শনে আসার ঘটনাটিকে জাপান-বাংলাদেশের মধ্যে সুদূরপ্রসারী সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার সোপান বলে হায়াকাওয়া তার আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন।
১৯৭৬ সালের ১৬ মার্চ বাংলাদেশ সরকারের আমন্ত্রণে ৮ সদস্যের জাপানি প্রতিনিধি দলের বাংলাদেশ সফরে নেতৃত্ব দেন হায়াকাওয়া। ১৯৭৭ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর ঢাকায় জাপান এয়ারলাইন্সের বিমান হাইজ্যাক ঘটনার সফল নিষ্পত্তিতে বাংলাদেশ সরকার ও জনগণের সার্বিক সহযোগিতার প্রতি জাপানের সরকার ও জনগণের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে ২৭ অক্টোবর জাপান সরকারের বিশেষ দূত হিসেবে হায়াকাওয়া চতুর্থবারের মতো বাংলাদেশ সফর করেন এবং সে বছর ১৬ ডিসেম্বর জাপান বাংলাদেশকে একটি বোয়িং ৭৭৭ উপহার দেয়।
১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানেই মূলত জাপানি বিনিয়োগ ও ব্যবসায়িক যোগাযোগ প্রসার লাভ করে। ঢাকা শহরের কেন্দ্রস্থলে শান্তিনগরে জাপানি কনস্যুলার অফিস ছিল পূর্ব পাকিস্তানে জাপানি ব্যবসা-বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক ভাব বিনিময়ের জন্য নিবেদিত। এ অফিসের উদ্যোগে ঢাকায় ষাটের দশকে জাপানি ফুল সাজানোর উৎসব ‘ইকেবানা’সহ নানা অনুষ্ঠান আয়োজিত হতো।
ঢাকার রাস্তায় টয়োটা গাড়ির চলাচল শুরু হয় সে সময়। ৬০-এর দশকেই শাহবাগে জাপানি রেস্তোরাঁ ‘সাকুরা’ স্থাপিত হয় এবং সেখানে খাবার হিসেবে টেম্পুরা ও শুশি বেশ জনপ্রিয়তা পায়। বাওয়ানিদের ইস্টার্ন কেমিক্যালসে জাপানি ইঞ্জিনিয়ারদের উপস্থিতি, ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানা ও চট্টগ্রাম ইস্পাত কারখানায় জাপানি বিনিয়োগ ও অংশগ্রহণ ছিল সে সময়কার বড় ঘটনা।
বাংলাদেশ-জাপানের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের একটি বড় অনুষঙ্গ হল, বিগত সাতচল্লিশ বছরে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের প্রসারতা। এ কথা প্রণিধানযোগ্য যে, আধুনিক পর্যায়ে দু’দেশের সম্পর্কের গভীরতা এবং গতি-প্রকৃতিতে অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং বাংলাদেশ-জাপান দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের উত্থান-পতন বিশেষ নির্দেশক হিসেবে কাজ করেছে।
আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পর জাপান সরকার বাংলাদেশের যুদ্ধবিদ্ধস্ত অর্থনীতি পুনর্গঠনে এগিয়ে আসে। বাংলাদেশে জাপানি বাণিজ্য ও সে সুবাদে বিনিয়োগে জাপানিরা বরাবরই আগ্রহ দেখিয়ে এসেছে। জাপানই হচ্ছে এশিয়ায় বাংলাদেশের রফতানি বাণিজ্যের অন্যতম গন্তব্যস্থল। আবার জাপানি পণ্য বাংলাদেশের আমদানি বাণিজ্যের সিংহভাগ দখল করে আছে।
জাপানের সঙ্গে বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক কোনো বাণিজ্য চুক্তি না থাকলেও দু’দেশের মধ্যে বাণিজ্য চলে মুক্তবাজার নীতিতে এবং গ্যাট ও অধুনা ডব্লিউটিও নিয়ন্ত্রিত অনুশাসন অনুসারে। বাংলাদেশের পণ্য জাপানের বাজারে প্রবেশে ৩৮টি স্বল্পোন্নত দেশের মতো জিএসপি সুবিধা পেয়ে থাকে। জাপান এক্সটারনাল ট্রেড অর্গানাইজেশন (জেট্রো) জাপানে বাংলাদেশি পণ্যের বাজার সৃষ্টিতে নানা টেকনিক্যাল অ্যাসিসট্যান্স দিয়ে থাকে।
বাংলাদেশের হিমায়িত চিংড়ি জাপানের বাজারে বেশ জনপ্রিয়তা পেলেও যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের তুলনায় মূল্যকাঠামো ভিন্নতর হওয়ায় জাপানে বাংলাদেশি চিংড়ির সরবরাহ কমছে। জাপানিরা এখন প্রক্রিয়াজাত চিংড়ির দিকে ঝুঁকছে। বাংলাদেশ থেকে রেডিমেড গার্মেন্টসের চাহিদা থাকলেও সরবরাহ সময় বেশি লাগার দরুন জাপানে তৈরি পোশাকের প্রবেশ আশানুরূপ হচ্ছে না।
জাপানের বাজারে বাংলাদেশ অন্যতম চামড়া সরবরাহকারী দেশ; বিশেষ করে বাংলাদেশের ছাগলের চামড়ার বেশ কদর জাপানের বাজারে। বাংলাদেশের চা ‘দ্য স্টার অব বেঙ্গল’ ব্র্যান্ড নামে জাপানের বাজারে ঠাঁই পেয়েছে। জাপান-বাংলাদেশ বাণিজ্য প্রসারের ক্ষেত্রে জাপান চেম্বার অব কমার্স, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বারস অব কমার্স (এফবিসিসিআই) এবং সাম্প্রতিক কালে সংগঠিত বাংলাদেশ-জাপান চেম্বার অব কমার্স-এর ভূমিকা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।
বাংলাদেশের ইপিজেডগুলোয় জাপানি বিনিয়োগ বাড়ছে আর সে সুবাদে জাপানে বাংলাদেশের রফতানি বাড়ছে। ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ-জাপান যৌথ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সহযোগিতা কমিটি আত্মপ্রকাশের পর দু’দেশের সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে গঠনমূলক ও ফলপ্রসূ যোগাযোগের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়।
বাংলাদেশে জাপানি বিনিয়োগের সিংহভাগ এসেছে রাসায়নিক সেক্টরের (৫৭ শতাংশ) পর টেক্সটাইল সেক্টরের (১৬ শতাংশ) স্থান, তারপর মেটাল প্রডাক্টস (১৩ শতাংশ), ইলেকট্রনিক্স (১১ শতাংশ) এবং অন্যান্য (৩ শতাংশ)। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাস তুলনামূলকভাবে কম দামে পাওয়ার ফলে রাসায়নিক সার প্রস্তুতে এর সহজ জোগান সম্ভব হয়েছে।
বাংলাদেশের প্রাগ্রসরমান গার্মেন্টস শিল্পের পশ্চাৎ সংযোগ হিসেবে টেক্সটাইল সেক্টরে জাপানি বিনিয়োগ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষাপটে জাপানের নিশিমেন, টয়োবো কর্পোরেশন এবং বাংলাদেশের এ কে খান গ্রুপ ইন্টারন্যাশনাল মিলস প্রজেক্ট স্থাপনের একটি উদ্যোগ এবং ১৫০ মিলিয়নের মারুবেনী-এসারের আরেকটি বড় প্রকল্প (কোল্ড রোল স্টিল মিলস লি.) দীর্ঘদিন ধরে বাস্তবায়নের অপেক্ষায়।
১৯৯৫ সালে জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা) দ্য স্টাডি অন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট অন চিটাগং রিজিওন ইন দ্য পিপলস রিপাবলিক অব বাংলাদেশ নামে একটি বিশেষ সমীক্ষা বাংলাদেশ সরকারের কাছে পেশ করে। এ প্রতিবেদনে বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে স্পেশাল ইকোনমিক জোনগুলো গঠনের পরামর্শ প্রদান করা হয়। সমীক্ষায় ২৫ বছর মেয়াদি একটি বিনিয়োগ মহাপরিকল্পনা উপস্থাপন করা হয়; যার মধ্যে কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ পাড়ে জাপানিদের জন্য একটি বিশেষ রফতানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল, গভীর সমুদ্রে আধুনিক কনটেইনার সুবিধাসংবলিত সমুদ্রবন্দর এবং চট্টগ্রামে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হয়।
চট্টগ্রাম এবং চট্টগ্রাম সংলগ্ন এলাকা ঘিরে শিল্প বেষ্টনী গড়ে তুলতে পারলে সিঙ্গাপুর, ব্যাংকক ও চট্টগ্রামকে নিয়ে একটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রায়াঙ্গেল গঠিত হতে পারে বলে প্রতিবেদনে অভিমত প্রকাশ করা হয়। ইতিমধ্যে চট্টগ্রামে শুধু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জাপানি সহায়তায়। জাপানিদের জন্য ইকোনমিক জোন প্রতিষ্ঠায় জাপানিদের আগ্রহ আয়োজনে টানাপোড়েন সৃষ্টি হয় চট্টগ্রামের অদূরে কোরীয় বিনিয়োগকারীদের জন্য বিশেষ ইপিজেড প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের বিতর্কিত ভূমিকার কারণে। সম্প্রতি জাপানিদের আহ্বান জানানো হয়েছে চট্টগ্রামে সমুদ্রবন্দর এলাকায় পরিত্যক্ত বৃহৎ শিল্প ইউনিটে জাপানিদের জন্য বিশেষ শিল্পাঞ্চল গড়ে তুলতে।
মোহাম্মদ আবদুল মজিদ : সাবেক সচিব, এনবিআরের সাবেক চেয়ারম্যান
