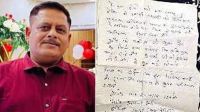প্রিন্ট: ১৩ এপ্রিল ২০২৫, ১১:৪৮ এএম
প্রবল চাহিদার বিপরীতে রেল কেন জনবান্ধব হতে পারল না
অমিত রায় চৌধুরী
প্রকাশ: ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮, ১২:০০ এএম
প্রিন্ট সংস্করণ

ছবি: সংগৃহীত
উন্নত যোগাযোগ কাঠামো যে কোনো আধুনিক রাষ্ট্রের এক নির্ণায়ক চরিত্রের লক্ষণ। অগ্রসর রাষ্ট্রব্যবস্থায় উৎপাদন ও বণ্টন প্রক্রিয়াকে সাবলীল রাখতে পরিবহন শিল্পের চটুল ও লাগসই প্রয়োগ নিঃসন্দেহে দেশীয় সক্ষমতার প্রতিফলক, সমৃদ্ধির চিহ্ন।
ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতই একটি জনগোষ্ঠীর চাহিদা, রুচি ও জীবনচর্চার আদল নির্মাণ করে। উপকূলীয় এ অঞ্চলের মানুষ প্রাকৃতিক ও ঐতিহ্যগত কারণেই চলাচলের বৃহত্তম মাধ্যম হিসেবে ভরসা রেখে এসেছে নৌপথে।
শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্য প্রসারের পথ বেয়েই মানুষের জীবনমানে যে ইতিবাচক রূপান্তর ঘটেছে, তাই আবার নাগরিকের দৈনন্দিনতায় বিবর্তন ঘটিয়েছে; সড়ক, রেল বা আকাশ- যাত্রী বা পণ্য পরিবহনে নতুন ক্ষেত্র উন্মোচন করেছে।
বিশ্বের বিভিন্ন দেশ তাদের নিজস্ব সামর্থ্য, কৃষ্টি, সংস্কৃতি অথবা ভৌগোলিক সুবিধা অনুযায়ী বিদ্যমান বিকল্পগুলোর মধ্য থেকে অগ্রাধিকার নির্বাচন করে। অবশেষে বিদ্যমান ব্যবস্থাগুলোকে বহাল রাখার পাশাপাশি স্থানীয় বাস্তবতায় সর্বাধিক মানানসই ও লাভজনক বিকল্পটির যথাসাধ্য উন্নয়ন ও আধুনিকায়নে দেশের সর্বোচ্চ মনোযোগ ও সামর্থ্য বিনিয়োজিত হয়।
বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সামূহিক কল্যাণই সেখানে মুখ্য। টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনায় জাতীয় স্বার্থই প্রাধান্য পাবে- এটিই কাক্সিক্ষত। বর্ধনশীল জনসংখ্যা, বিকাশমান অর্থনীতি, নৌপথের সীমাবদ্ধতা ও সড়ক ব্যবস্থাপনার বিপন্ন দশা আমলে নিলে বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় রেলসেবার গুরুত্ব ও কার্যকারিতার বিষয়টি অনিবার্যভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।
জর্জ স্টিফেনশনের বাষ্প ইঞ্জিন আবিষ্কারের পর ১৮২৫ সালে ব্রিটেনে রেলওয়ে পরিষেবা চালু হয়। পৃথিবীর আলোকিত গোলার্ধ অর্থাৎ ইউরোপ ও আমেরিকায় রেলসেবা পৌঁছে যায় তড়িৎগতিতে। সৌভাগ্যের বিষয় হল- বাংলা তথা তদানীন্তন ভারতবর্ষে রেলসেবা চালুর জন্য বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয়নি।
১৮৪৪ সালে ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ে নামে একটি প্রতিষ্ঠান কয়লা বহনের জন্য পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া থেকে রানীগঞ্জ পর্যন্ত সর্বপ্রথম রেলপথ নির্মাণের পরিকল্পনা করে। ১৮৫২ সালে কলকাতা থেকে সুন্দরবন হয়ে গঙ্গার পূর্বপাড় এবং পরবর্তীকালে ঢাকা পর্যন্ত রেললাইন সম্প্রসারিত করার পরিকল্পনা নেয়া হয়। তবে কার্যত ১৮৬২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর ইবিআর কলকাতা-রানাঘাট পর্যন্ত ৭৩ কিমি. রেললাইন স্থাপন করে; যা ব্রিটিশ বাংলায় রেলের শুভ সূচনা।
এরই ধারাবাহিকতায় দু’মাস পর ১৮৬২ সালের ১৫ নভেম্বরে বর্তমান বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমারেখায় দর্শনা-জগতি রুটে ৫৩.১১ কিমি. ব্রডগেজ রেললাইন প্রথম চালু হয়। ৯ বছর পর ১৮৭১ সালের ১ জানুয়ারি এ রেলপথটি জগতি থেকে গোয়ালন্দ পর্যন্ত সম্প্রসারিত করে ঢাকা-কলকাতার মধ্যে রেল সংযোগ স্থাপন করা হয়। আর তখনই বাংলাদেশের পরিবহন ব্যবস্থার ইতিহাসে নতুন যুগের সূচনা ঘটে।
দেশ বিভাগের পর তদানীন্তন ইস্ট বেঙ্গল রেলওয়ে ২,৬০৬.৫৯ কিমি. রেলপথ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়। ভারত বিভক্তির আগে উত্তরবঙ্গ ও আসামের সঙ্গে কলকাতার যোগাযোগ নিশ্চিত করার জন্য ১৯১৫ সালে হার্ডিঞ্জ ব্রিজ স্থাপন করা হয়। ১৯৩৭ সালে ঢাকা ও চট্টগ্রামের মধ্যে যোগাযোগের জন্য মেঘনা ব্রিজ চালু হয়।
পাকিস্তান শাসনামলে রেল ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য উল্লেখযোগ্য কোনো পদক্ষেপ দৃশ্যমান হয় না। দেশ বিভাগের ফলে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া দর্শনা-যশোর পর্যন্ত ৬৯.২৩ কিমি. ব্রডগেজ সিঙ্গল্ লাইন, ঢাকা-টঙ্গী, চট্টগ্রাম-মীরেরসরাই ডাব্ল লাইন, রূপসা-বাগেরহাট ৩২ কিমি. মিটারগেজ রেলকে ব্রডগেজে রূপান্তর এবং সিলেটে ১৮.৫১ কিমি. রোপওয়ে নির্মাণ ছাড়া পাকিস্তান আমলে রেলপথে তেমন কোনো ইতিবাচক পরিবর্তন হয়নি।
পক্ষান্তরে আবদুলপুর থেকে পার্বতীপুর পর্যন্ত প্রলম্বিত ডাবল লাইন পাকিস্তান রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ কেন অপসারণ করে সিঙ্গল্ লাইনে রূপান্তর করল- তা বোধগম্য নয়। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন এ দেশের অসংখ্য সড়ক ও রেলসেতু ধ্বংস করে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে পর্যুদস্ত করে ফেলা হয়।
এ আগ্রাসী ধ্বংসযজ্ঞের হাত থেকে ঐতিহাসিক হার্ডিঞ্জ ব্রিজও রেহাই পায়নি। যদিও স্বাধীনতার অব্যবহিত পরই ভারতের সহায়তায় বঙ্গবন্ধু রেল যোগাযোগের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ সেতুটি অস্বাভাবিক দ্রুততায় মেরামত করে ফেলতে সক্ষম হন।
অস্বীকার করার উপায় নেই যে, রেলপথের মৌলিক কাঠামো তৈরি হয় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে; যা বাংলাদেশের আধুনিক রেলওয়ে নেটওয়ার্কের ভিত্তিভূমি। স্বাধীন বাংলাদেশ সাকুল্যে ২,৮৫৮.৭৩ কিমি. রেলপথ ও ৪৬৬টি রেলস্টেশন পরম্পরা সূত্রে লাভ করে।
যদিও ব্রিটিশ ও পাকিস্তান শাসনামলে নিরাপদ, সাশ্রয়ী ও দ্রুত যাতায়াতের জন্য রেলপথ সাধারণ মানুষের নির্ভরতার প্রতীকে পরিণত হয়েছিল। তবে এ কথাও সত্যি যে, দেশ বিভাগের আগে ভারত ও পাকিস্তানে রেল ব্যবস্থার ইতিহাস, ক্রমবিকাশ, জনবিন্যাস একইরকম হওয়া সত্ত্বেও বিভাগোত্তরকালে দুটি দেশে রেলের সেবামান ও চরিত্র বিচারে বৈপরীত্য লক্ষণীয়।
ভারতে রেলের সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন ঘটে বিস্ময়কর দ্রুততায় ও ব্যাপকতায়। কলকাতা শহরে প্রায় দেড় কোটি মানুষ ৩০০ কিমি. পথ পাড়ি দিয়ে প্রতিদিন অফিস করে রাতে নিজগৃহে ফিরে যায়- মহানগরীর যানজট, দূষণ নিরসনে অথবা সার্বিক পরিবেশের ওপর চাপ কমাতে রেল ব্যবস্থাপনা কীভাবে ভূমিকা রাখছে এ চিত্র থেকে তা পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়।
শুধু পরিবেশবান্ধব দ্রুতিময়, সুলভ ও নিরাপদ পরিবহন হিসেবে নয়, ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, ফেডারেল রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে সংযোগ স্থাপন, রাষ্ট্রীয় একতা, অখণ্ডতা ও দেশপ্রেমের চেতনা বিস্তারে রেল ভূমিকা রেখে চলেছে।
বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম রেল পরিষেবা হিসেবে ভারতীয় রেলকে ‘ট্রান্সপোর্ট লাইফলাইন অব দি নেশন’ বলা হয়। রেলওয়ে নেটওয়ার্কের গোড়াপত্তন একই সময় হলেও আমাদের দেশে কেন এ ব্যবস্থাটি সাধারণের দোরগোড়ায় স্বছন্দে পৌঁছতে পারল না- তা ফিরে দেখার প্রয়োজন আছে।
অনস্বীকার্য যে, বৃহত্তর পরিসরে ব্যক্তিমালিকানায় পরিচালিত নৌ ও সড়কে আজ নিরাপত্তা ও ব্যবস্থাপনার ইস্যুটি প্রশ্নবিদ্ধ, এসব পরিবহন ব্যবস্থার ওপর মানুষের আস্থা ক্রমশ নিুগামী। অথচ রাষ্ট্রায়ত্ত রেলপথে মানুষের আগ্রহ ও নির্ভরশীলতার চিত্রটি সম্পূর্ণ বিপরীত।
বিশেষ করে উৎসবের মৌসুমে রেলের টিকিটের জন্য সারা রাত সারিবদ্ধ মানুষকে যখন রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষায় অথবা ট্রেনের ছাদে, কিংবা কামরায় দাঁড়িয়ে এমনকি শৌচাগারেও নিশ্চিত আশ্রয় খুঁজে নিতে দেখা যায়, তখন স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে তাহলে কি এই অপরিহার্য জনপরিবহনকে ইচ্ছাকৃতভাবে উপেক্ষা-অবহেলার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হয়েছে?
তবে কার স্বার্থে কালোত্তীর্ণ এই রেলসেবা আজ ক্ষয়িষ্ণুতা, অদক্ষতা ও দুর্নীতি-লুটপাটের চারণভূমিতে পরিণত হল, কোন অদৃশ্য কারসাজিতে শাখা লাইনগুলো আজ উৎপাটিত- তা অবশ্যই অনুসন্ধানের দাবি রাখে। রেল যোগাযোগের পরিকল্পিত পরিকাঠামো থাকার পরও জনসংখ্যায় ভারাক্রান্ত উদীয়মান অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে বিকাশমান বাংলাদেশ কেন রেল ব্যবস্থার উন্নয়নে উদ্যোগী হল না- তা কৌতূহলের বিষয়বস্তু।
রেলের বিকল্প হিসেবে যদি দুর্নীতি-লুটপাটের পরিচিত উৎস সড়কপথকে পরিবহন সেবার রাজ্যে মনোপলি দেয়া হয় তবে এ নীতি ও পরিকল্পনার পেছনে অন্তত দেশপ্রেম যে কাজ করেনি, তা সহজেই অনুমেয়।
আর বৈষয়িক লালসাই যে এ পথের সন্ধান দিয়েছে- এ বিষয়েও কোনো সন্দেহ থাকে না। গণতান্ত্রিক শাসনের অনুপস্থিতিতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চক্রান্তে রেলওয়ের স্বাভাবিক গতি ও ছন্দে বিঘ্ন সৃষ্টির সব পরিকল্পিত আয়োজন চোখে পড়ে। রেল ব্যবস্থাকে অদক্ষ, দুর্নীতিগ্রস্ত ও অকার্যকর করে সুপরিকল্পিত উপায়ে সড়ক পরিবহনের কাছে সাধারণ মানুষকে জিম্মি করে ফেলাই উদ্দেশ্য ছিল কিনা ভেবে দেখতে হবে।
অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, আশি ও নব্বইয়ের দশকে যখন গোটা পৃথিবীতে সড়ক, নৌ বা আকাশপথের চেয়ে রেলপথকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হচ্ছিল, ঠিক এমন সময় আমাদের দেশে ৩০০ কিমি. শাখা লাইন বন্ধ করে দেয়া হল। বলা যায় শুধু ব্রিটিশ ভারতে নয়, এমনকি পাকিস্তান আমলেও রেল ব্যবস্থার প্রতি এমন তাচ্ছিল্য ও উপেক্ষা দেখা যায়নি।
শতাব্দীপ্রাচীন শাখা লাইনগুলোকে রাতারাতি বন্ধ করে দিয়ে একদা তিল তিল করে গড়ে ওঠা রেলপথ সন্নিহিত সমৃদ্ধ জনপদগুলোকে অনগ্রসর, পশ্চাদপদ অঞ্চলে পরিণত করে ফেলা হল- যা এক কথায় নজিরবিহীন, সামাজিক ন্যায়বিচার বা সুষম উন্নয়নের সঙ্গে কখনও সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এ ক্ষেত্রে রূপসা-বাগেরহাট রুটের ৩২ কিমি. লাইনটি উল্লেখযোগ্য।
খুলনা বিভাগের সঙ্গে বাগেরহাট হয়ে যে শাখাটি মোংলা বন্দর বা বৃহত্তর বরিশালের সঙ্গে যুক্ত হতে পারত তাকে কেন বন্ধ করে দেয়া হল তা বোধগম্য নয়। সাধারণ মানুষের জন্য কেবল অনিবার্য ফলাফলটিই অবশিষ্ট থাকল। আমরা একটি সমৃদ্ধ, আলোকিত জনপদকে বিপর্যস্ত, অন্ধকার, অনগ্রসর জনপদে রূপান্তর প্রক্রিয়ার কালসাক্ষী হয়ে গেলাম। শাখা বন্ধের অজুহাত দাঁড় করানো হল।
দেখানো হল রেলপথ অলাভজনক। প্রথমত রাষ্ট্রীয় সেবা কখনও লাভ-ক্ষতি বিচার করে না। দ্বিতীয়ত দুর্বল ও অদক্ষ ব্যবস্থাপনাই কেবল যে কোনো প্রতিষ্ঠানের ক্ষতিকে উসকে দেয়। তৃতীয়ত রেল বিলুপ্তির পর রেলের কোটি কোটি টাকার সম্পদ যেভাবে লুট হয়েছে, মূল্যবান জমি যেভাবে অবৈধ দখলদারের কবলে গেছে তা বর্ণনাতীত। পরিসংখ্যান বলছে অবৈধ দখলকারীদের কাছে রেলের যে সম্পদ আছে তার পরিমাণ ৪,৯৩১ একর।
ব্রিটিশ আমলে রেল নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে বলা যায় ২০০৮ সালের পর প্রথমবারের মতো রেলের আধুনিকায়ন, নতুন রেললাইন নির্মাণ, সম্প্রসারণ, প্রযুক্তি সংযোজন, নতুন ইঞ্জিন কোচ ক্রয়, বন্দর থেকে বন্দরে রেল যোগাযোগ সৃষ্টি এবং ট্রান্সশিপমেন্ট এড়ানোর জন্য পদ্মা ও বঙ্গবন্ধু সেতুতে রেল সংযোগ প্রদানের মতো মেগা প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে।
বিগত ১০ বছরে সরকার ৯৫ হাজার কোটি টাকা প্রকল্পের বিপরীতে ইতিমধ্যে ৫০ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করেছে। বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও বন্ধুপ্রতিম দেশ রেলের উন্নয়নে আমাদের ঋণ সহায়তা করে থাকে। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস, প্রকল্পের কাজ সঠিক সময়ে শেষ করতে না পারায় শুধু সম্ভাব্য ব্যয়ের আকার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে তা নয়, এডিবির মতো প্রতিষ্ঠান সময়মতো ব্যয় করতে না পারায় ৪৮০ কোটি টাকা প্রত্যাহার করে নিয়েছে।
সুতরাং দক্ষতা বৃদ্ধি ও ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা আনতে না পারলে রাষ্ট্রের সাধু উদ্যোগগুলো সাফল্যের মুখ দেখবে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ খুলনা শিপইয়ার্ডের কথা বলা যায়। কেবল ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব বাংলাদেশ নৌবাহিনীর হাতে দেয়ায় লোকসানি প্রতিষ্ঠানটি লাভের মুখ দেখেছে। দেশীয় প্রযুক্তিতে উৎপাদিত জাহাজ বিদেশে রফতানিযোগ্য হয়েছে।
বর্তমানে সারা দেশে চলাচলকারী মোট যাত্রীবাহী ট্রেন ৩৫০টি। স্টেশন ৪৬০টি। আন্তঃদেশীয় ট্রেন ৪টি। নদীবহুল এ দেশে রেল চলাচলে প্রধান অন্তরায় ছিল বন্দর, ঘাট; যা ট্রাফিকের স্বাভাবিক ছন্দকে বিপর্যস্ত করে, দীর্ঘ সময়ক্ষেপণ ও ব্যয়বহুলতা পরিবহনের উপযোগিতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।
বঙ্গবন্ধু রেলওয়ে সেতু নির্মাণ ও পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্প ভবিষ্যতে রেলযাত্রাকে নতুন সম্ভাবনার পথ দেখাতে পারে। প্রায় ১ হাজার কিমি. নতুন রেলপথ নির্মাণের কথা শোনা যাচ্ছে।
প্রযুক্তি সহযোগে রেলের সার্বিক আধুনিকায়ন, নতুন ইঞ্জিন-কোচ-যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং সর্বোপরি একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনার আওতায় রেলকে জনবান্ধব করার জন্য কিছু আন্তরিক প্রচেষ্টা চোখে পড়ছে; যার মধ্যে সার্কুলার, মেট্রো, এক্সপ্রেস ওয়ে অন্যতম।
কাশিয়ানী-গোপালগঞ্জ-টুঙ্গিপাড়া, তারাকান্দি-বঙ্গবন্ধু সেতু, ঢাকা-আখাউড়া-লাকসাম-চট্টগ্রাম ডাবল লাইনের কাজ ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। আর মাওয়া হয়ে ঢাকা-যশোর, দোহাজারী-কক্সবাজার, ভাঙ্গা-পায়রা বন্দর, খুলনা-দর্শনা ডাবল লাইনের কাজ দ্রুত সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়।
চট্টগ্রাম বন্দর থেকে মোংলা বন্দর পর্যন্ত রেল যোগাযোগ স্থাপিত হতে যাচ্ছে; যা প্রকারান্তরে ভারত, নেপাল, ভুটান, মিয়ানমারের সঙ্গে যোগাযোগ সৃষ্টি করবে। ট্রান্স এশিয়ান রেলওয়ে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করবে।
বাংলাদেশের সমকালীন চাহিদা ও বিকাশমান অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে এটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যানজটবিধ্বস্ত ঢাকা মহানগরে মেট্রো ও এলিভেটেড রেল নির্মাণের পরিকল্পনা সত্যিই আমাদের কল্পনাবিলাসী করে তোলে।
ঢাকা থেকে দ্রুতগামী ট্রেন যদি খুলনা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, সিলেট এমনকি বরিশালের সঙ্গে যুক্ত করা যায় তাহলে যোগাযোগের ক্ষেত্রে তা হবে একটি বৈপ্লবিক সংস্কার। গোটা বাংলাদেশকে সচল রেল নেটওয়ার্কের মধ্যে নিয়ে আসতে পারলে সেটি আমাদের উন্নয়ন অভিযাত্রায় নতুন মাত্রা যুক্ত করবে।
রেল যোগাযোগকে সময় উপযোগী ও লাভজনক করতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন দক্ষ জনবল ব্যবহার, উন্নত রেল যন্ত্রপাতি, ইঞ্জিন, কোচ এবং মানসম্মত যাত্রীসেবা। যাত্রীর জন্য চাই নিরাপত্তা, গতি, অর্থ ও সময়ের সাশ্রয়। বাংলাদেশ রেলওয়ে যাত্রীর এ চাহিদা পূরণে সক্ষম। বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও সমাজ রেলকে এ যৌক্তিক সহায়তা প্রদানের জন্য সৎ ও অঙ্গীকারাবদ্ধ বলে প্রতীয়মান হয়। প্রয়োজন শুধু রেল ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত ঊর্ধ্বতন আমলা থেকে নিম্নপর্যায়ের কর্মচারীদের সততা, দক্ষতা, শ্রম ও দেশপ্রেম।
রেল আমাদের পাশে আছে শত বছরের যাত্রায়। প্রাত্যহিকতায়, নিরাপত্তায়, নির্ভরতায়। রেলের সঙ্গে জড়িয়ে আছে কত স্মৃতি। প্রেম-বিরহ, আনন্দ-বেদনা, মিলন-বিচ্ছেদ। রেল আছে আমাদের কল্পনায়, ভাবনায়। এক লহমায় আমরা ভেসে যাই দূর অতীতে।
শৈশব, কৈশোর বা প্রমত্ত যৌবনে। জানালায় চোখ রেখে দুরন্ত গতিতে ছুটে চলা প্রকৃতির অনাবৃত সৌন্দর্যের মাঝে হারিয়ে যাওয়া কিংবা অনন্ত এ মহাবিশ্বের উন্মত্ত গতিময়তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে ওঠার রোমাঞ্চকর সুখস্মৃতি। রেল আছে আমাদের জীবনে, আমাদের আবেগে। রবীন্দ্রনাথ থেকে সত্যজিৎ রায়- সবখানে। কবিতা, গান, ছড়া, গল্প কিংবা চলচ্চিত্রের পর্দায়। সব মলিনতা, অবহেলা ঝেড়ে ফেলে এগিয়ে চলুক রেল, আকাঙ্ক্ষার সীমানা ছাড়িয়ে, স্বপ্ন-সম্ভাবনার দিগন্ত ছাপিয়ে।
অমিত রায় চৌধুরী : অধ্যক্ষ, সরকারি ফকিরহাট ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা ডিগ্রি মহাবিদ্যালয়, ফকিরহাট, বাগেরহাট
principalffmmc@gmail.com



-67f5811351741.jpg)




-67fb8d375bd84.jpg)