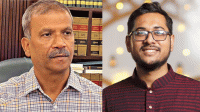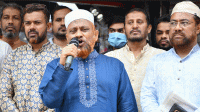প্রিন্ট: ১৯ এপ্রিল ২০২৫, ০৪:৩১ এএম
সুনীল অর্থনীতির কর্মকৌশল বাস্তবায়ন জরুরি
ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী
প্রকাশ: ২৫ এপ্রিল ২০২৪, ১২:০০ এএম
প্রিন্ট সংস্করণ

আরও পড়ুন
পৃথিবী নামক এই গ্রহে জনবহুল ক্ষুদ্র আয়তনের ব-দ্বীপখ্যাত নদীমাতৃক আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি। এর একদিকে রয়েছে সুজলা-সুফলা উর্বর ভূমির সমারোহ; অন্যদিকে বহু নদী বা সমুদ্রের বিশাল জলতরঙ্গের কলতান। স্রষ্টার অপার কৃপায় অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর হয়েও এদেশ বরাবরই ছিল অনগ্রসর জনপদ। কথিত প্রাগ্রসর ঔপনিবেশিক শক্তির শাসন-শোষণ-কূটচাল-নিপীড়ন-নির্যাতনের ফলে এখানে শুধু অনুন্নয়নের ‘উন্নয়ন’ হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে স্বাধীন রাষ্ট্র অর্জনের পর অব্যাহত উন্নয়ন-উদ্যোগ বর্তমান পর্যায়ে দেশকে পৌঁছে দিয়েছে। স্বাধীনতার অব্যবহতি পর বঙ্গবন্ধু অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য জাতিকে ঐক্যবদ্ধভাবে কঠিন সংগ্রামে ব্রতী করেছিলেন। সংবিধানের ১৪৩(১)(খ) অনুচ্ছেদেও বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় জলসীমার অন্তর্ভুক্ত মহাসাগর ও মহিসোপানের খনিজসম্পদের ওপর মালিকানা প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। দেশের সমুদ্র ও সমুদ্রসীমা রক্ষার্থে ১৯৭৪ সালে প্রণয়ন করেন ‘দ্য টেরিটোরিয়াল ওয়াটার্স অ্যান্ড মেরিটাইম জোন্স অ্যাক্ট’। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকারের মেয়াদকালে আইনি প্রক্রিয়ায় সমুদ্র বিজয়ের গৌরব অর্জন করেছে দেশ। মূল ভূখণ্ডের প্রায় ৮২ শতাংশের সমান ১ লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটারেরও বেশি এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দেশের সার্বভৌমত্ব। উন্নত-উন্নয়নশীল বিশ্বে এ ধরনের সামুদ্রিক এলাকার সার্বিক উন্নয়ন অর্থনীতির চাকাকে সচল করে চলছে।
সুনীল অর্থনীতি প্রত্যয়টি বিশ্বব্যাপী বহুল পরিচিত। বেলজিয়ামের অর্থনীতিবিদ গুন্টার পাওলি ১৯৯৪ সালে ব্লু ইকোনমি বা সুনীল অর্থনীতির ধারণা ব্যক্ত করেন। মূলত সুনীল অর্থনীতি হলো সমুদ্রনির্ভর অর্থনীতি। সমুদ্র থেকে আহরণকৃত সম্পদ দেশের অর্থনীতিতে যুক্ত হলে তা সুনীল অর্থনীতি হিসাবে বিবেচিত হয়। সহজ কথায়, সমুদ্রসম্পদ আহরণ ও ব্যবহারে সুপরিকল্পনা সুনীল অর্থনীতির মৌলিক উদ্দেশ্য। আমাদের সবার জানা, চলমান বৈশ্বিক মন্দায় বাংলাদেশও বিপর্যস্ত। প্রাত্যহিক জীবনযাপনে সাধারণ নাগরিকদের দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে সুনীল অর্থনীতির অপার সম্ভাবনার হাতছানি দেশবাসীকে করছে উদ্বেলিত। এ সম্পর্কিত কথাবার্তা বা আলোচনায় নানা ধরনের ইতিবাচক চিন্তাভাবনা শোনা যাচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে। তবে বাস্তবে এর কতটুকু অর্জিত হয়েছে তা বোধগম্য নয়। এ সম্পর্কে দেশবাসীও সম্যক অবগত বলে মনে হয় না। জ্বালানি তেল-গ্যাস ও অন্যান্য সমুদ্রসম্পদ আহরণে পর্যাপ্ত গবেষণা হয়ে থাকে। কিন্তু এসব গবেষণার ফলাফল নিয়ে আগ্রহ বেড়েছে। সুনীল অর্থনীতির প্রতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অধিক মনোযোগ কাম্য।
বিভিন্ন গবেষণায় প্রতিফলিত হয়েছে, বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় রয়েছে চারটি মৎস্যক্ষেত্র। সেখানে ৪৪০ প্রজাতির সামুদ্রিক মাছ, ৩৩৬ প্রজাতির শামুক-ঝিনুক, ৭ প্রজাতির কচ্ছপ, ৫ প্রজাতির লবস্টার, ৩৬ প্রজাতির চিংড়ি, ৩ প্রজাতির তিমি, ১০ প্রজাতির ডলফিন এবং প্রায় ২০০ প্রজাতির সামুদ্রিক ঘাস রয়েছে। আরও রয়েছে ইসপিরুলিনা নামক সবচেয়ে মূল্যবান আগাছা। অপ্রাণিজ সম্পদের মধ্যে রয়েছে খনিজ ও খনিজজাতীয় সম্পদ যেমন-তেল, গ্যাস, চুনাপাথর ইত্যাদি। এ ছাড়া ১৭ ধরনের মূল্যবান খনিজ বালি। যেমন-জিরকন, রুটাইল, সিলিমানাইট, ইলমেনাইট, ম্যাগনেটাইট, গ্যানেট, কায়ানাইট, মোনাজাইট, লিকোক্সিন ইত্যাদি। এগুলোর মধ্যে মোনাজাইট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমুদ্রসৈকতের বালিতে মোট খনিজের মজুত ৪৪ লাখ টন। প্রকৃত সমৃদ্ধ খনিজের পরিমাণ প্রায় ১৭ লাখ ৫০ হাজার টন, যা বঙ্গোপসাগরের ১৩টি স্থানে পাওয়া গেছে। গবেষকরা বাংলাদেশের একান্ত অর্থনৈতিক এলাকায় মেরিন জেনেটিক রিসোর্সের অবস্থান এবং বিবিধ প্রজাতি চিহ্নিত করে অর্থনৈতিক সম্ভাবনা বিশ্লেষণ করেছেন। বাংলাদেশের কিছু প্রজাতির সি-উইডে প্রচুর প্রোটিন আছে, যা ফিশফিড হিসাবে আমদানি করা ফিশ অয়েলের বিকল্প হতে পারে। আবার কিছু প্রজাতি অ্যানিমেল ফিডের মান বৃদ্ধিতে ব্যবহৃত হতে পারে। কসমেটিকে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত উপাদান সদৃশ সি-উইডও অনেক পাওয়া গেছে।
বৈশ্বিক অর্থনীতিতে সুনীল অর্থনীতির নানামাত্রিক অবদান অনস্বীকার্য। বর্তমানে বৈশ্বিক অর্থনীতির প্রায় পাঁচ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের কর্মকাণ্ড হচ্ছে সমুদ্রকে ঘিরে। গণমাধ্যমে প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদ পর্যালোচনায় দেখা যায়, বিশ্বের ৪৩০ কোটিরও বেশি মানুষের ১৫ শতাংশ প্রোটিনের জোগান দিচ্ছে সামুদ্রিক মাছ, উদ্ভিদ ও জীবজন্তু। পৃথিবীর ৩০ শতাংশ গ্যাস ও জ্বালানি তেল সরবরাহ হচ্ছে সমুদ্রতলের বিভিন্ন গ্যাস ও তেলক্ষেত্র থেকে। ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় অর্থনীতির সিংহভাগ সমুদ্রনির্ভর। দ্য জাকার্তা পোস্টে প্রকাশ পাওয়া নিবন্ধের তথ্যমতে, দ্য লমবক ব্লু ইকোনমি বাস্তবায়ন কর্মসূচিতে ৭৭ হাজার ৭০০ নতুন কর্মসংস্থান তৈরির সম্ভাবনা প্রবল। পাশাপাশি প্রতিবছর আয় হবে ১১৪ দশমিক ৮৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। যুক্তরাষ্ট্র ১৯৭৪ সালে তাদের মোট দেশজ উৎপাদনে সুনীল অর্থনীতির অবদান পরিমাপের চেষ্টা চালায়। ২০১৩ সালে দেশটির অর্থনীতিতে সমুদ্র অর্থনীতির অবদান ছিল ৩৫৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা তাদের মোট জিডিপির ২ শতাংশ। অস্ট্রেলিয়া সমুদ্রসম্পদ থেকে বর্তমানে প্রায় ৪৭ দশমিক ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করছে। ২০২৫ সালে অস্ট্রেলিয়া এ খাত থেকে ১০০ বিলিয়ন ডলার আয় করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।
ইতোমধ্যে চীনের অর্থনীতিতে ১ দশমিক ২ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের সামুদ্রিক শিল্প গড়ে উঠেছে। ২০৩৫ সাল নাগাদ চীনের জিডিপিতে সামুদ্রিক খাতের অবদান হবে ১৫ শতাংশ। এ ছাড়া চীন, জাপান, ফিলিপাইনসহ বেশকিছু দেশ ২০০ থেকে ৩০০ বছর আগেই সমুদ্রকেন্দ্রিক অর্থনীতির দিকে মনোনিবেশ করেছিল। ২০১৫ সালে প্রকাশিত ইকোনমিক ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের প্রতিবেদনটি এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। এ প্রতিবেদন মতে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিশ্বের বিভিন্ন উপকূলীয় দেশ ও দ্বীপের সরকারগুলো অর্থনীতির নতুন ফ্রন্ট হিসাবে সমুদ্রসম্পদের দিকে নজর দিতে শুরু করেছে। সমুদ্র অর্থনীতির ওপর ভিত্তি করে দেশের প্রবৃদ্ধির নীতি গ্রহণ করছে। বিশ্বব্যাংকের পরিসংখ্যান মতে, ২০১৫ সালে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সমুদ্র বা নীল অর্থনীতির অবদান ছিল প্রায় ৬ দশমিক ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমান। আয়ের সর্বোচ্চ অংশ আসে পর্যটন ও বিনোদন খাত থেকে, যার পরিমাণ ২৫ শতাংশ। মৎস্য ও যাতায়াত উভয় খাত থেকে আয়ের পরিমাণ ছিল ২২ শতাংশ। গ্যাস ও তেল উত্তোলন থেকে আয় হয় ১৯ শতাংশ। সংশ্লিষ্ট গবেষকদের মতে, ব্লু ইকোনমির চারটি ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করলে বছরে বাংলাদেশের পক্ষে ২ দশমিক ৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করা সম্ভব। এ চারটি সেক্টর হলো-তেল ও গ্যাস উত্তোলন, মৎস্য আহরণ, বন্দর সম্প্রসারণ এবং পর্যটন। এ খাতে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে।
সমুদ্রসম্পদের যথোপযুক্ত ব্যবহারের লক্ষ্যে ২০১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়। এটি দক্ষিণ এশিয়ায় ২য় এবং বিশ্বে ১২তম উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে। ২০১৫ সালে কক্সবাজারে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু করা হয় সমুদ্রবিজ্ঞান বিভাগ। ২০১৭ সালে জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে গঠন করা হয় ব্লু-ইকোনমি সেল। ২০১৮ সালে বাংলাদেশ নৌবাহিনী সদর দপ্তরের সহায়তায় ‘বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব মেরিটাইম রিচার্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট’ (রিমরাড) প্রতিষ্ঠার মূল পরিকল্পনা ছিল সমুদ্র অর্থনীতির সমৃদ্ধকরণ। পর্যাপ্ত গবেষণা, জ্ঞানসৃজন, উপযোগী মানবসম্পদ উৎপাদন এবং সমুদ্রসম্পদের সুরক্ষা-আহরণ-সংরক্ষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন। সমুদ্রসম্পদ সুরক্ষায় ২০১৯ সালে মেরিটাইম জোন অ্যাক্ট প্রণয়ন করা হয়েছে।
বাংলাদেশ সরকার সমুদ্রকে কেন্দ্র করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য ২৬টি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এগুলো হলো-শিপিং, উপকূলীয় শিপিং, সমুদ্রবন্দর, ফেরির মাধ্যমে যাত্রীসেবা, অভ্যন্তরীণ জলপথে পরিবহণ, জাহাজ নির্মাণ, জাহাজ রিসাইক্লিং শিল্প, মৎস্য, সামুদ্রিক জলজ পণ্য, সামুদ্রিক জৈবপ্রযুক্তি, তেল ও গ্যাস, সমুদ্রের লবণ উৎপাদন, মহাসাগরের নবায়নযোগ্য শক্তি, ব্লু-এনার্জি, খনিজসম্পদ (বালি, নুড়ি ও অন্যান্য), সামুদ্রিক জেনেটিক সম্পদ, উপকূলীয় পর্যটন, বিনোদনমূলক জলজ ক্রীড়া, ইয়টিং ও মেরিনস, ক্রুজ পর্যটন, উপকূলীয় সুরক্ষা, কৃত্রিম দ্বীপ, সবুজ উপকূলীয় বেল্ট বা ডেল্টা পরিকল্পনা, মানবসম্পদ, সামুদ্রিক নিরাপত্তা এবং সামুদ্রিক সমষ্টি স্থানিক পরিকল্পনা (এমএসপি) ইত্যাদি।
বঙ্গোপসাগরে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনায় বর্তমানে সাতটি সমুদ্র ব্লকে আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানিগুলো একক ও যৌথভাবে তেল অনুসন্ধানের কাজে নিয়োজিত আছে। ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ মহাপরিকল্পনায় সমুদ্র অর্থনীতিকে যথার্থ অগ্রাধিকার বিবেচনায় পাঁচ ধরনের কর্মকৌশল নির্ধারিত হয়েছে। প্রসঙ্গত, গত ২২ ফেব্রুয়ারি ‘দ্য টেরিটোরিয়াল ওয়াটার্স অ্যান্ড মেরিটাইম জোন্স অ্যাক্ট-১৯৭৪’র সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ‘বাংলাদেশের বিশাল সমুদ্রসীমার সম্পদ ব্যবহার করে দেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি করাই সরকারের লক্ষ্য। আমি নিশ্চিত, সুনীল অর্থনীতি বিকাশের লক্ষ্যে আমরা যেসব বহুমুখী উদ্যোগ ও পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি, তার অবারিত সুফল ভোগ করবে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম।’ সবকিছু বিবেচনা করে সময়ক্ষেপণ না করে সমুদ্রসম্পদ আহরণে পরিকল্পিত কর্মকৌশল কার্যকর করতে আন্তরিক উদ্যোগ জরুরি। সুনীল অর্থনীতির সুফল ভোগের জন্য দেশবাসীর আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা বিপুল।
ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী : শিক্ষাবিদ; সাবেক উপাচার্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়