
প্রিন্ট: ১৬ এপ্রিল ২০২৫, ১২:২২ পিএম
ড. আর এম দেবনাথ
প্রকাশ: ২৫ নভেম্বর ২০২৩, ১২:০০ এএম
প্রিন্ট সংস্করণ

আরও পড়ুন
দুই কাগজে দুই খবর। দুটিই দুশ্চিন্তার, দুটিই খারাপ খবর। এ মুহূর্তে ভালো খবরের মধ্যে আছে-আমন ধান উঠছে। কৃষকরা নতুন ধান ঘরে তুলছেন। ঢাকায় নবান্ন উৎসবও পালিত হয়েছে। ফসলের পূর্বাভাসও ভালো। আর খারাপ খবরের একটি হচ্ছে নির্বাচন সম্পর্কিত। নির্বাচন কমিশন নির্ধারিত নির্বাচনের দিন ৭ জানুয়ারি। তফশিল ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু সবাই মিলে নির্বাচন করবে কিনা তা অনিশ্চিত। আরেকটি খারাপ খবর হচ্ছে হরতাল-অবরোধ। চলছে অবরোধ এবং তা মোটামুটি লাগাতার। ব্যবসায়ী-শিল্পপতিরা বলছেন, দিনে তাদের ৬০০০ কোটি টাকার ক্ষতি হচ্ছে। তারা হরতাল-অবরোধ বন্ধ রাখতে অনুরোধ করেছেন। অর্থনীতিবিদরাও বসে নেই। তারাও হিসাব কষছেন ক্ষতির, লোকসানের। আবার খবরের কাগজগুলো নিয়মিত অর্থনীতি সম্পর্কে খারাপ খবর দিয়ে যাচ্ছে। এসব খবর উৎপাদন, আমদানি, রপ্তানি, রেমিট্যান্স, রাজস্ব, মূল্যস্ফীতি, আবহাওয়া খারাপজনিত ফসলের ক্ষতি ইত্যাদি বিষয়ে। কোথাও শান্তির খবর নেই। মানুষ দূরপাল্লায় যাতায়াত করতে পারছে না। ঢাকায় চলাচলও বিঘ্নিত হচ্ছে। এসব বলা যায় এখন মামুলি খবর। আবার যে খবরের কথা দিয়ে শুরু করেছি তাও মামুলি। কিন্তু এর চরিত্র ও আকার দিন দিন জটিল হচ্ছে। খবর দুটি হচ্ছে ঋণ সম্পর্কিত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্কিত। যুগান্তরের খবরের শিরোনাম হচ্ছে : ‘যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কমছে বৈদেশিক বাণিজ্য’। অনুমাননির্ভর এ খবরের পাশাপাশি আরেকটি খবরের কাগজের খবরের শিরোনাম হচ্ছে ‘১০০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছল বাংলাদেশের বিদেশি ঋণ’। কাগজটির প্রথম সংবাদ এটি। শিরোনাম পড়েই মাথা গরম হয়ে যায়। বলে কী? ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সেপ্টেম্বরের মধ্যেই এ অবস্থা। ওই বছর বাংলাদেশের বিদেশি ঋণস্থিতি ছিল মাত্র ৪১ দশমিক ১৭ বিলিয়ন ডলার। এই কয়েক বছরে তা বেড়ে হয়েছে ১০০ দশমিক ৩০ বিলিয়ন ডলার। এ ঋণের দুটি ভাগ : সরকারি ঋণ এবং বেসরকারি খাতের ব্যবসায়ীদের ঋণ। সরকারের বিদেশি ঋণ হচ্ছে ৭৯ বিলিয়ন ডলার এবং বেসরকারি খাতে বিদেশি ঋণ হচ্ছে ২১ বিলিয়ন ডলার
জনমনে ঋণ নিয়ে নানা প্রশ্নের জন্ম হলেও সরকার এবং বাংলাদেশ ব্যাংক মনে করে আমাদের ঋণসীমা সহনীয় পর্যায়ে আছে। আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের মধ্যে আছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বিদেশি ঋণ ছিল মোট জিডিপির মাত্র ১৫ দশমিক ৫ শতাংশ। আর এখন তা হয়েছে ২২ শতাংশ। সরকার ও সরকারসংশ্লিষ্টরা বলছেন, আমাদের ঋণের স্থিতি সহ্যসীমার মধ্যে আছে; উদ্বেগের কিছু নেই। এ নিয়ে অহেতুক হইচই করার মতো কিছু হয়নি। তবু মন মানে না। কারণ আমরা বাঙালিরা ঋণ সম্পর্কে বড়ই স্পর্শকাতর। ঋণকে আমরা বোঝা মনে করি। মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়ে ছেলেরা বাবার ঋণের সব দায়িত্ব নেয়। তারপর লাশ কবরে যায়। এটা আমাদের বিশ্বাস। ঋণ বড় দায়। একান্ত প্রয়োজন ছাড়া আমরা ঋণ করি না।
এখানে প্রশ্ন আছে। আমরা যেসব প্রকল্পের জন্য ঋণ নিয়েছি, তা নিতান্ত প্রয়োজনীয় প্রকল্প কিনা। দ্বিতীয় প্রশ্ন, প্রকল্পের ব্যয়ের হিসাব ঠিক আছে কিনা। নাকি এক টাকার প্রকল্প আমরা দুই টাকায় করে বিদেশিদের কাছে দুই টাকার ঋণী হয়েছি। এখানে ব্যয়ের গুণগত মান নিয়ে আমাদের প্রশ্ন রয়ে গেছে। অনেকের ধারণা, আমরা অনেক বড় ঋণ না নিলেও পারতাম-সেগুলোর প্রয়োজন ছিল না। কারণ ওই ঋণের টাকা সুদে-আসলে পরিশোধ করতে হবে। করতে হবে সময়সীমার মধ্যে। না করলেই বিপদ। কেউ কেউ বলেন, বড় বড় প্রকল্পের ঋণের ব্যবহার, বেসরকারি খাতের বৈদেশিক ঋণপ্রাপ্তি এবং ব্যবহারের কারণেও আজ আমাদের আইএমএফের কাছে হাত পাততে হয়েছে। এর ফলে অর্থনীতির সব দুর্বলতার চিত্র আজ দেশবাসীর সামনে দৃশ্যমান। স্বাভাবিকভাবে আমরা হয়তো তা কোনোদিন জানতেও পারতাম না। আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের প্রয়োজন ছিল ৪৫-৪৮ বিলিয়ন ডলার। কিন্তু তা আজ আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে ১৫ বিলিয়ন ডলারের মতো। এ খবর আইএমএফের হস্তক্ষেপের কারণে জানতে পেরেছি। আর এক খবরেই সব ভণ্ডুল হওয়ার উপক্রম। আমদানির জন্য প্রয়োজনীয় ডলার নেই। ব্যাংকে ব্যাংকে ডলারের জন্য হাহাকার। ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের কাছে আগে ব্যাংকাররা ছুটতেন ব্যবসার জন্য, এখন ব্যবসায়ীরা ছুটছেন এমডির কাছে। ডলার নেই। রেমিট্যান্স কম, রপ্তানি আশানুরূপ নয়। বৈদেশিক ঋণের প্রবাহ কম। ফলে ডলারের বাজারে ঊর্ধ্বগতি। এ সুযোগে ‘দেশপ্রেমিক’ হুন্ডিওয়ালা বিগ বিজনেস বিদেশ থেকেই ডলার কিনে নিজেদের কাছে রেখে দিচ্ছে। ডলারের এমন সংকট স্বাধীনতার পর ছিল। তখন সদ্য স্বাধীন দেশে কোনো কিছুই গোছানো ছিল না। বহু কষ্টে, শ্রমে, সাধনায় স্বাধীন বাংলাদেশ এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছেছিল। কিন্তু এক ডলার সংকটেই আজ আমরা নাস্তানাবুদ। এর ফল হচ্ছে অভূতপূর্ব মূল্যস্ফীতি। খাদ্য মূল্যস্ফীতি এখন ১২ শতাংশের উপরে। সার্বিক মূল্যস্ফীতি ১০ শতাংশের উপরে। কঠিন পরিস্থিতি। বাংলাদেশে ব্যাংক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের নানা পথ উদ্ভাবন করার চেষ্টা করছে। কিন্তু ফল শূন্য। কবে এর থেকে আমরা মুক্তি পাব তা কেউ জানি না।
প্রশ্ন আরও আছে। এটা তো বর্তমান অবস্থা। কিন্তু আরও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ভবিষ্যতের প্রশ্ন। ঋণের টাকা তো পরিশোধ করতে হবে। আমাদের অনেকের বয়স হয়েছে। অর্থমন্ত্রীসহ অনেক মন্ত্রীরও অনেক বয়স হয়েছে। আমরা বয়স্করা কেউ থাকব না। কিন্তু নতুন প্রজন্মকে ঋণের টাকা পরিশোধ করতে হবে সুদসহ। কেউ টাকা মাফ করবে না। দৃশ্যত মনে হচ্ছে, পরিশোধ করতে হবে গরিবের ছেলেমেয়েদের, অসহায় মধ্যবিত্তের ছেলেমেয়েদের। কারণ ধনাঢ্য ব্যক্তি, অতিধনী ব্যক্তি। উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা, বড় ব্যবসায়ী এবং রাজনীতিকদের ছেলেমেয়েরা দেশে নেই। আমেরিকা, কানাডা, ইউরোপ, দুবাই, মালয়েশিয়া, ব্যাংকক, অস্ট্রেলিয়ায় তারা নিবাস গড়েছেন। ঋণ শোধের ভার তাদের ঘাড়ে পড়বে না। তারা মাঝেমাঝে দেশে এসে ‘পবিত্র একুশে ফেব্রুয়ারি’ উদযাপন করে চলে যাবেন। তাহলে ঋণ পরিশোধ কে করবে? করবে অসহায় নাগরিকরা, যারা বিদেশে ঘরবাড়ি করতে পারবে না। করবে না। কিন্তু প্রশ্ন, কীভাবে তারা করবে?
সরকারের ঘনিষ্ঠজনরা বিষয়টিকে খুবই হালকাভাবে দেখেন। একজন মন্ত্রী তো সেদিন বলেই ফেলেছেন, ডলার আসবে যাবে-দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। আর হরদম মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বোঝানো হচ্ছে, আমাদের আন্তর্জাতিক ঋণ সহ্যসীমার মধ্যে আছে। বহু দেশের ঋণের পরিমাণ জিডিপির ৫০-৬০-৭০ শতাংশ এবং তারও উপরে; আর আমরা মাত্র ২৪ শতাংশ, এটা কিছুই না। অঙ্কে যারা ভালো, তারা একথা বলতেই পারেন। বই পড়ে মুখস্থ পরীক্ষা যারা দেন, তারা একথাই বলবেন। তারা জানেন না ঋণ-জিডিপির অনুপাত নয়, আসল কথা হচ্ছে রাজস্ব। রাজস্ব লাগবে, উদ্বৃত্ত রাজস্ব লাগবে ঋণ পরিশোধ করতে। বিদেশে অর্জিত ডলার লাগবে ঋণ পরিশোধ করতে। ‘বিগ কোশ্চেন’, আমাদের জিডিপি-রাজস্ব অনুপাতের অবস্থা কী? বিগত কয়েক বছরে জিডিপির আকার অনেক বেড়েছে। এর অনুপাতে কি আমাদের রাজস্ব বেড়েছে? ধনী, অতিধনীরা কি ট্যাক্স দেন? বিড়িওয়ালা, জর্দাওয়ালারা যেভাবে ট্যাক্স দেন, সেভাবে কি ‘বিগ বিজনেস হাউজগুলো’ ট্যাক্স দেয়? যদি দিত তাহলে জিডিপি-রাজস্ব অনুপাত এত কম হতো না। ভীষণ লজ্জার বিষয় এটা।
আইএমএফ এসে শর্ত দিচ্ছে। আমরা শর্ত পালন করতে পারছি না। ব্যর্থ হচ্ছি বারবার। কত কথা হচ্ছে রাজস্ব বৃদ্ধির, কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। সবসময় যারা করদাতা, তাদের ওপরই বোঝা বাড়ছে। নতুন করদাতার নামে চলছে হাস্যকর প্রক্রিয়া। যারা করযোগ্য নন, তাদেরও কর দিতে হয়। গরিবের সন্তান বর্তমান অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তাফা কামাল তো বলেই ফেললেন, দেশের সব নাগরিককে কর দিতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এর থেকে আমাদের রেহাই দিলেন। তাহলেই প্রশ্ন, রাজস্ব বৃদ্ধি না করে, রাজস্ব উদ্বৃত্ত না বাড়িয়ে আমরা বৈদেশিক ঋণ কীভাবে পরিশোধ করব? বিরাট প্রশ্ন। এ বিষয়টি কেউ ভাবছেন না। তাহলে কি রপ্তানি বাড়িয়ে, ডলারের জোগান বাড়িয়ে আমরা বৈদেশিক ঋণের টাকা পরিশোধ করব? হ্যাঁ, এটা একটা পন্থা হতে পারে। কিন্তু যুগান্তরের স্টোরি তো ভিন্ন কথা বলছে। আমাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক অংশীদার হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। পণ্য আমদানির উৎস হচ্ছে চীন, এরপর ভারত। তাদেরকে ডলার দিতে হয়। আর ডলার রোজগারের অন্যতম দেশ হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। সেখান থেকে রেমিট্যান্সও আসে বেশি। সেখানে আমাদের রপ্তানি বেশি, আমদানি কম। বস্তুত যুক্তরাষ্ট্র আমাদের স্বাধীনতার বিরোধিতা করলেও এখন আমাদের ব্যবসার লাভজনক উৎস। যুগান্তরের পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশে রেমিট্যান্সের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে ৪৮ দশমিক ৮৫ শতাংশ। এবং এটা ঘটেছে জুলাই-সেপ্টেম্বর পিরিয়ডে। রপ্তানি আয় জুন থেকে জুলাই মাসে কমেছে ৬ কোটি ডলার। সেদেশ থেকে বিনিয়োগও হ্রাস পেয়েছে। এসব নতুন উদ্বেগের খবর। যুক্তরাষ্ট্র আমাদের ডলার দেয়, বাকিদের আমাদেরকে ডলার পরিশোধ করতে হয়। কাজেই এ ধরনের পরিস্থিতি যদি অব্যাহত থাকে, তাহলে ঋণের টাকা পরিশোধ হবে কীভাবে? বলা বাহুল্য, যুক্তরাষ্ট্রের লেজে লেজে আরও দেশ আছে। সেসব দেশের ক্ষেত্রে অবস্থা কী? বিষয়গুলো নিয়ে ভাবা দরকার।
ড. আর এম দেবনাথ : অর্থনীতি বিশ্লেষক; সাবেক শিক্ষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়


-67f9d547e1fa5.jpg)


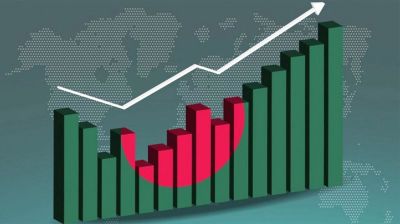




-67ff48bc87951.jpg)


-67ff44ab11026.jpg)


