আগামীতে মূল্যস্ফীতিই হবে অর্থনীতির জন্য বড় চ্যালেঞ্জ
এম এ খালেক
প্রকাশ: ২৯ মার্চ ২০২২, ১২:০০ এএম
প্রিন্ট সংস্করণ
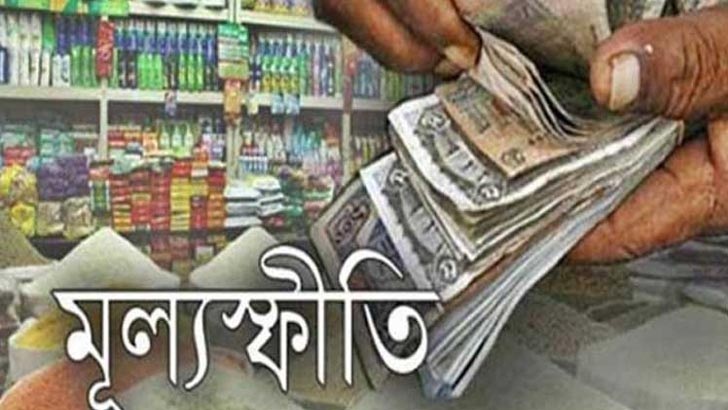
একজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ বলেছেন, আগামীতে করোনা-পরবর্তী বিশ্ব ব্যবস্থায় মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখাটাই হবে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। এটা শুধু কোনো নির্দিষ্ট দেশের জন্য নয় বিশ্ব অর্থনীতির জন্যই কাল হয়ে দাঁড়াতে পারে। বিশ্ব খাদ্য সংস্থার এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, আগামীতে বিশ্বব্যাপী মূল্যস্ফীতির কারণে সামাজিক অস্থিতিশীলতা দেখা দিতে পারে। উল্লেখ্য, ২০০৭ এবং ২০০৮ সালে বিশ্বব্যাপী তীব্র খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছিল। সেই সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে সৃষ্ট মন্দার কারণে বিশ্বব্যাপী খাদ্য পণ্যের জোগান সাংঘাতিকভাবে কমে গিয়েছিল। প্রায় প্রতিটি দেশেই খাদ্যসহ নিত্যপণ্যের মূল্য সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে গিয়েছিল। কোনো কোনো দেশে টাকা নিয়ে বাজারে গিয়ে খাদ্য পণ্য পাওয়া যাচ্ছিল না। আফ্রিকার অনেক দেশে খাদ্য ক্রয় করতে গিয়ে ভোক্তারা সংঘাতে জড়িয়ে পড়েছিল। এতে অনেকেরই প্রাণহানি ঘটেছিল। করোনার কারণে বিশ্বব্যাপী খাদ্য উৎপাদন কমে গেছে। করোনার প্রকোপ বর্তমানে কিছুটা কমে এসেছে। এ অবস্থায় অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। করোনার নতুন ভ্যারিয়েন্ট ছড়িয়ে পড়ায় অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া বিঘ্নিত হয়েছে। এরপর নতুন সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধ। রাশিয়া যে এভাবে ইউক্রেনে সার্বিক আক্রমণ পরিচালনা করবে তা অনেকেই ভাবতেও পারেনি। রুশ বাহিনী ইউক্রেনে ঢুকে পড়ায় বিশ্ব অর্থনীতি মারাত্মকভাবে ঝুঁকির মুখে পড়েছে। ইতোমধ্যেই জ্বালানি তেলের উচ্চ মূল্য আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। যদিও রাশিয়া জ্বালানি তেলের উত্তোলন বাড়িয়ে আন্তর্জাতিক জ্বালানি তেলের বাজার অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছে। জ্বালানি তেলের মূল্য এখন আগের তুলনায় কমেছে। তবে এ অবস্থা কতদিন স্থায়ী হবে তা এখনই নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না।
জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) বলেছে, রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বিশ্বব্যাপী খাদ্য উৎপাদন ও জোগান সাংঘাতিকভাবে কমে যেতে পারে। সংস্থাটি বলেছে, যুদ্ধের কারণে বিশ্বব্যাপী খাদ্যপণ্যের মূল্য ১৫ থেকে ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পেতে পারে। বিশ্বের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় গম রপ্তানিকারক দেশ হচ্ছে রাশিয়া ও ইউক্রেন। তারা মিলিতভাবে আন্তর্জাতিক বাজারে ১৯ শতাংশ যব, ১৪ শতাংশ গম ও ৪ শতাংশ ভুট্টার জোগান দেয়। সামগ্রিকভাবে তারা বিশ্ব খাদ্যশস্যের এক-তৃতীয়াংশ জোগান দেয়। ইউক্রেন বিশ্ব খাদ্য উৎপাদনকারী দেশের তালিকায় উপরের দিকেই রয়েছে। তারা গম রপ্তানিতে প্রথম সারিতে রয়েছে। বিশ্ব খাদ্য সংস্থা বলেছে, যুদ্ধের কারণে আগামী বছর ইউক্রেনের খাদ্য উৎপাদন কমে যাওয়ার নিশ্চিত আশঙ্কা রয়েছে। কারণ যুদ্ধের কারণে তাদের অন্তত ২০ থেকে ৩০ শতাংশ জমি অনাবাদি থেকে যাবে। ইউক্রেনের খাদ্য উৎপাদন হ্রাস পেলে বিশ্বব্যাপী পুষ্টিহীনতা বাড়বে। কারণ বিশ্বের ৫০টি দেশের আমদানিকৃত গমের ৩০ শতাংশ জোগান দেয় রাশিয়া ও ইউক্রেন। যেহেতু দেশ দুটি ট্রেডিশনাল যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে তাই তারা চাইলেও আগের মতো ফসলের আবাদ করতে পারবে না। এ অবস্থায় বিশ্বের পুষ্টিহীন মানুষের সংখ্যা ৮০ লাখ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১ কোটি ৩ লাখে উন্নীত হতে পারে। এ পুষ্টিহীন মানুষের বেশিরভাগই হবে আফ্রিকা এবং এশিয়া অঞ্চলের। যুক্তরাজ্যের মূল্যস্ফীতির হার ৫ শতাংশ অতিক্রম করে গেছে, যা গত ৩০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। যুদ্ধ সহসাই বন্ধ না হলে এ মূল্যস্ফীতির হার ১০ শতাংশ অতিক্রম করে যেতে পারে।
যুদ্ধের কারণে পরিবহণ ব্যয় সাংঘাতিকভাবে বেড়ে গেছে। একটি বহুজাতিক কোম্পানির শীর্ষ নির্বাহী কর্মকর্তার মতে, পরিবহণ ব্যয় অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি। তাদের প্রতিটি গমভর্তি লরির জন্য এখন অতিরিক্ত আড়াই হাজার পাউন্ড ব্যয় করতে হচ্ছে। অল্প কিছু দিনের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ না হলে পরিস্থিতি কোন দিকে যায় তা বলা মুশকিল। তবে অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে যুদ্ধ খুব সহসাই বন্ধ হবে না। রাশিয়া যত সহজে ইউক্রেন দখল করতে পারবে আশা করেছিল বাস্তবে তা হচ্ছে না। জাতীয়তাবাদী চেতনার ধারক ইউক্রেনীয়দের পরাস্ত করা খুব একটা সহজ হবে না। এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তাদের নেতৃত্বাধীন ন্যাটো বাহিনী ইউক্রেনকে অস্ত্র প্রদানসহ নৈতিক সাপোর্ট দিয়ে চলেছে। কাজেই রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হবে বলেই মনে হচ্ছে।
প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এ যুদ্ধের প্রভাব কেমন হতে পারে? বাংলাদেশের সঙ্গে রাশিয়া ও ইউক্রেনের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক খুবই ভালো। আমাদের সঙ্গে তাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক রয়েছে। বাংলাদেশ প্রতিবছর যে বিপুল পরিমাণ গম ও ভুট্টা আমদানি করে তার একটি বড় অংশই আসে এই দুটি দেশ থেকে। আগামীতে বিশ্ববাজারে গমের মূল্য বৃদ্ধি পেলে তার প্রভাব বাংলাদেশকেও মোকাবিলা করতে হবে। বাংলাদেশের বাজার ব্যবস্থাপনা কোনো আদর্শিক নিয়ম মেনে চলছে না। বিশ্বের অধিকাংশ দেশের তুলনায় বাংলাদেশে মজুরির হার কম কিন্তু পণ্য মূল্য অনেক বেশি। এমনকি কোনো কোনো পণ্য আন্তর্জাতিক বাজারের চেয়ে বেশি মূল্যে বিক্রি করা হয়।
সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) তাদের এক প্রতিবেদনে এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। প্রতিবেদনে বিভিন্ন পণ্যমূল্যের একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। বাংলাদেশে যে ডিমের ডজন বিক্রি হয় ১১০ টাকায় সেই একই ডিম যুক্তরাষ্ট্রের ওহাইও অঙ্গরাজ্যে বিক্রি হয় ১০৩ টাকায়। অথচ ঢাকায় একজন শ্রমিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিকদের চেয়ে অনেক কম বেতন পান। ঢাকার একজন শ্রমিকের মাসিক বেতন ১৪৯ মার্কিন ডলার বা ১৩ হাজার টাকা। আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একজন শ্রমিকের বেতন হচ্ছে ৩ হাজার ৯৫৫ মার্কিন ডলার বা ৩ লাখ ৪০ হাজার টাকা। মালয়েশিয়ার এক শহরে ডিমের ডজন মাত্র ৮৬ টাকা। সেখানে একজন শ্রমিকের মাসিক বেতন ৬৬৯ মার্কিন ডলার সমতুল্য ৫৭ হাজার টাকা। ঢাকায় ১৩ হাজার টাকা বেতনধারী একজন শ্রমিককে প্রতি কেজি পেঁয়াজ কিনতে হচ্ছে ৫৫ টাকায়। অথচ সার্বিয়ার ২৯ হাজার টাকা বেতনধারী একজন শ্রমিককে একই পেঁয়াজ কিনতে হচ্ছে ৪১ টাকায়। আজারবাইজানে সাড়ে ২৬ হাজার টাকা বেতনধারী একজন শ্রমিককে একই পেঁয়াজ কিনতে হচ্ছে ৩৭ টাকায়। স্পেনে এক লিটার তরল দুধ কেনা যায় ৬৩ টাকায়, চেক প্রজাতন্ত্রে ৬২ টাকায় এক লিটার দুধ পাওয়া যায়। কিন্তু বাংলাদেশে এক লিটার তরল দুধ কিনতে ব্যয় করতে হয় ৮০ টাকা। বাংলাদেশে এক কেজি গরুর গোশত বিক্রি হচ্ছে ৬৫০ টাকায়। একই গোশত বিশ্ববাজারে বিক্রি হচ্ছে ৪০০ থেকে ৫০০ টাকায়। বাংলাদেশে প্রতিকেজি চিনি বিক্রি হয় ৬৫ থেকে ৭০ টাকায়, অথচ বিশ্ববাজারে চিনির মূল্য তুলনামূলক অনেক কম। বাংলাদেশে প্রতি লিটার ভোজ্যতেল বিক্রি হয় ১৪০ থেকে ১৭০ টাকায়। আর বিশ্ববাজারে তা বিক্রি হচ্ছে ১২০ থেকে ১৪০ টাকা। বাংলাদেশে প্রতি কেজি মিনিকেট চাল বিক্রি হয় ৬০ থেকে ৬৫ টাকায়। আর থাইল্যান্ডে তা বিক্রি হয় ৪০ থেকে ৪৫ টাকায়। অর্থাৎ বাংলাদেশের মানুষ বেতন-ভাতা পান তুলনামূলকভাবে কম কিন্তু পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে তাদের উচ্চ মূল্য দিতে হয়।
একজন মন্ত্রী বলেছেন, বাংলাদেশের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা নাকি গত কয়েক বছরে তিনগুণ বেড়েছে। তিনি কি বাজারে গিয়ে পণ্যমূল্য কখনো যাচাই করেছেন? কারও বেতন-ভাতা বছরে বৃদ্ধি পায় একবার, কিন্তু পণ্যমূল্য বৃদ্ধি পায় বারবার। কারও বেতন যদি ৫০ টাকা বৃদ্ধি পায় আর বাজারে প্রতিটি পণ্যের মূল্য ১০ শতাংশ করে বৃদ্ধি পায় তাহলে তার সেই বেতন বৃদ্ধি কোনো কাজে আসবে না। আবার কারও বেতন-ভাতা বৃদ্ধি না পেলেও কোনো অসুবিধা নেই যদি বাজারে নিত্যপণ্যের মূল্য হ্রাস পায়। কাজেই মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির যে পরিসংখ্যান দেওয়া হচ্ছে তা সঠিক নয়।
করোনার পাশাপাশি ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের কারণে আগামীতে আমাদের মতো দেশগুলোকে আরও ভয়াবহ বিপদে পড়তে হবে। এ বিপদের ভয়াবহতা অনুধাবন করতে হলে রুশ-ইউক্রেনের সঙ্গে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক নিয়ে একটু আলোচনা করা যেতে পারে। আগেই বলা হয়েছে, রাশিয়া ও ইউক্রেনের সঙ্গে বাংলাদেশের চমৎকার দ্বিপাক্ষিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বাংলাদেশ রাশিয়ায় মোট ৬৬ দশমিক ৫৩ কোটি মার্কিন ডলারের পণ্য রপ্তানির বিপরীতে আমদানি করে ৪৬ দশমিক ৬৭ কোটি টাকার পণ্য। একই সময়ে বাংলাদেশ ইউক্রেনে রপ্তানি করে ২ দশমিক ৬৮ কোটি মার্কিন ডলারের পণ্য। আর দেশটি থেকে আমদানি করা হয় ৩১ দশমিক ৯৪ কোটি মার্কিন ডলারের পণ্য। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বাংলাদেশ রাশিয়ায় ৪৮ দশমিক ৭২ কোটি মার্কিন ডলারের পণ্য রপ্তানির বিপরীতে আমদানি করা হয় ৭৭ দশমিক ৩৯ কোটি মার্কিন ডলারের পণ্য। একই সময়ে বাংলাদেশ ইউক্রেনে মোট ২ কোটি মার্কিন ডলারের পণ্য রপ্তানির বিপরীতে আমদানি করে ৫১ দশমিক ৯০ কোটি মার্কিন ডলারের পণ্য।
২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশ রাশিয়ায় ৫৪ দশমিক ৮২ কোটি মার্কিন ডলারের পণ্য রপ্তানির বিপরীতে আমদানি করে ৬৫ দশমিক ২৮ কোটি মার্কিন ডলারের পণ্য। একই সময়ে ইউক্রেনে বাংলাদেশের রপ্তানির পরিমাণ ছিল ২ দশমিক ২৭ কোটি মার্কিন ডলার। আর আমদানি করা হয় ৩৪ দশমিক ২৮ কোটি মার্কিন ডলারের পণ্য। বাংলাদেশ সাধারণত রাশিয়া ও ইউক্রেন থেকে গম, ভুট্টা ইত্যাদি আমদানি করে থাকে। বিপরীতে বাংলাদেশ থেকে তৈরি পোশাক এবং অন্যান্য পোশাক জাতীয় পণ্য রপ্তানি করে। রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে সবচেয়ে উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে আন্তর্জাতিক জ্বালানি তেলের বাজার নিয়ে। কিছু দিন আগে বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি পেলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং আরও কয়েকটি দেশ অর্গানাইজেশন অব পেট্রোলিয়াম এক্সপোর্টিং কান্ট্রিজকে জ্বালানি তেলের উত্তোলন বাড়ানোর জন্য পরামর্শ দিয়েছিল। কিন্তু সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হয়। সে সময় রাশিয়া জ্বালানি তেল উত্তোলন ও রপ্তানি কমিয়ে দিয়েছিল। যুদ্ধের কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের মূল্য ব্যারেলপ্রতি ১২৯ মার্কিন ডলারে উন্নীত হলে রাশিয়া জ্বালানি তেলের উত্তোলন বৃদ্ধি এবং মূল্য হ্রাস করে। ফলে জ্বালানি তেলের মূল্য আবারও ১০০ মার্কিন ডলারের নিচে নেমে আসে। বাংলাদেশকে জ্বালানি তেল এবং গম আমদানি করতে হয়। তাই আগামীতে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের গতি-প্রকৃতির দিকে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে।
এম এ খালেক : অর্থনীতি বিশ্লেষক, সাবেক ব্যাংকার

