
প্রিন্ট: ০১ মে ২০২৫, ০৪:২৬ পিএম
বাংলায় উচ্চশিক্ষা ও বিজ্ঞানচর্চার প্রয়াস আরও বেগবান হোক
ড. রাশিদুল হক
প্রকাশ: ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২, ১২:০০ এএম
প্রিন্ট সংস্করণ
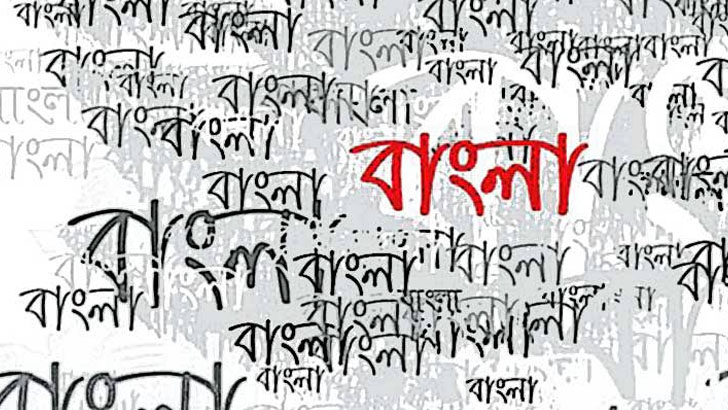
আরও পড়ুন
একটি দেশের মাতৃভাষা তার অহঙ্কার। এ যাবৎ, বিশ্বে ২৫টি ভাষায় সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে এবং তার মধ্যে বাংলা ভাষা একটি। এ ভাষায় কথা বলে প্রায় ২৮ কোটি বাঙালি। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালি বুকের তাজা রক্ত দিয়ে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষায় রূপ দিয়েছিল। একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবেও বিশ্বে স্বীকৃতি পেয়েছে। এমনকি জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা হিসাবে বাংলাকে অন্তর্ভুক্ত করারও দাবি উঠেছে। এরপরও কি দেশে বাংলা ভাষাকে জীবনের সর্বস্তরে আমরা চালু করতে সক্ষম হয়েছি?
বঙ্গবন্ধু সর্বস্তরে বাংলা ভাষা ব্যবহারের বিষয়ে ছিলেন আপসহীন। যে জাতি তার নিজ ভাষায় বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে উন্নত, সে জাতি তত অগ্রগামী। সে জাতি মাথা উঁচু করে সমগ্র বিশ্বে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন ভাষাকে সমুন্নত রাখার সেই সুযোগ করে দিয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার বয়স প্রায় একান্ন বছর। সরকার ও প্রশাসনের সব দাপ্তরিক আদেশ, ঘোষণা বাংলা ভাষায় তৈরি হলেও দেশের সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু করা এখনো সম্ভব হয়নি। উচ্চ আদালতের রায়গুলো এখনো অধিকাংশ ইংরেজিতেই লেখা হয়। আমার প্রশ্ন, দেশের কজন বিচারপ্রার্থী ইংরেজিতে লেখা সেই রায়ে কী বলা হলো, তা বুঝতে পারবেন? আইন-আদালতের ক্ষেত্রে মক্কেলদের ভাষার বাইরে যাওয়াটা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক, এমনকি অগণতান্ত্রিক। যদিও সাবেক প্রধান বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানসহ হাইকোর্টের কয়েকজন বিচারক বিভিন্ন মামলার রায় দিয়েছেন বাংলায়। সম্প্রতি হাইকোর্ট একটি মামলার রায় বাংলায় লিখে ভাষাশহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রশংসিত হয়েছে। সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন বলেছেন, দেশের সুপ্রিমকোর্টের রায় অচিরেই বাংলায় দেওয়া হবে, সেজন্য কাজ চলছে। আদালতের রায় বাংলায় দেওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা হতে পারে বিভিন্ন আইনি পরিভাষা, যেগুলোর যথাযথ প্রতিশব্দ বাংলায় তৈরি হয়নি।
ভাবতে অবাক লাগে, ভাষা আন্দোলনের সাত দশক পরও দেশের উচ্চশিক্ষাঙ্গনসহ অনেক প্রতিষ্ঠানে সেই ইংরেজিপ্রীতি মনোভাব নিয়েই আমরা এখনো বাস করছি। এখনো এ দেশে বিদ্যা, বুদ্ধি এবং কর্মকুশলতার মাপকাঠি দাঁড়িয়ে রয়েছে ইংরেজি বলা বা লেখার কৃতিত্বে। এই তো সেদিন, কোনো একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক/সহকারী অধ্যাপক পদের চাকরি নিয়োগে বেশ কয়েকটি ইন্টারভিউ বোর্ডে সদস্য ছিলাম। ইন্টারভিউ বোর্ডের সবাই প্রার্থীদের ইংরেজিতে প্রশ্ন করেছেন এবং প্রার্থীরাও মনেপ্রাণে চেষ্টা করেছেন শিক্ষকদের খুশি করতে; অথচ শিক্ষক-প্রার্থী সবাই সেখানে বাঙালি। প্রার্থীরা তাদের ইংরেজি ভাষায় কী বলতে চান, তা ভাবার্থে খুব পরিষ্কার নয়। তাদের জন্য আমার দুঃখ হয়। যাই হোক, এ রকম একজন প্রার্থীকে বললাম, তুমি আমার প্রশ্নটি মাতৃভাষায় আমাদের বুঝিয়ে বলো। অনায়াস বাংলায় তার ওই বিষয়টির ওপর উত্তরজ্ঞান বিচারের মাপকাঠিতে সবার কাছে প্রশংসিত হয়েছিল। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার খাতায় যে ছেলে ভালো ইংরেজি লেখে, চাকরির বাজার থেকে বিবাহযোগ্য কন্যার উদ্বিগ্ন পিতামাতা পর্যন্ত সর্বত্র তার আদর আছে। কারণ হচ্ছে, সে স্মার্ট ছেলে। বাঙালি হয়ে শুদ্ধ ভাষায় বাংলা ভালো বলতে পারে না, কিন্তু একটু জিহবা ঘুরিয়ে ঠুকঠাক ইংরেজি বলার অভ্যাস রপ্ত করেছে বেশ। এটা হাস্যকর। সুন্দর করে শুদ্ধ বাংলায় কথা বলাও যে বড় সম্মানের ও যোগ্যতার, মাতৃভাষা না জানলে এ শূন্যতা থেকেই যাবে। নিজের মন থেকে মনের ভাব প্রকাশের সৌন্দর্য হারিয়ে যাবে।
ইংরেজি আমাদের মাতৃভাষা নয়; কিন্তু ইংরেজি আমাদের শিখতে হয়। তাতে আপত্তি নেই, ক্ষোভও নেই-হয়তো লাভই আছে। স্বজাত্যবোধের আধুনিক ধারণা-ইংরেজিতে যাকে বলে ন্যাশনালইজম, তার বেশিটা আমরা পেয়েছি ইংরেজি শিক্ষার ফলে। সারা বিশ্বে যে ভাষাটি দাপটে বিরাজ করছে ও অন্য অনেক ভাষাকে কোণঠাসা করে এগিয়ে চলেছে, সেটি ইংরেজি। রাষ্ট্রপুঞ্জ অনেক ভাষাকে স্বীকৃতি দিলেও তার কাজকর্মের মূল ভাষা ইংরেজি।
ইংরেজি হলো আন্তর্জাতিক লিঙ্গুয়া ফ্রাংকা, যোগাযোগের ভাষা। ফলে ইংরেজির প্রতি ঝোঁক সারা বিশ্বে সর্বত্র বেড়েছে। অনেকে মনে করেন ইংরেজি বিজ্ঞানের ভাষা। এ ছাড়া ইংরেজি বিশ্ব অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণেরও ভাষা। তবে মাতৃভাষা ভালোভাবে শিখে, তার চর্চা অব্যাহত রেখেও ইংরেজি ভালোই শেখা যায়। আমি মনে করি, ইংরেজি শেখার প্রয়োজন আছে; সেখানে তো কারও কোনো বিরোধ নেই। বিদ্যাসাগর থেকে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথ থেকে হুমায়ুন কবিরের জীবন ও কর্ম থেকে আমরা সেটাই তো বুঝতে পেরেছি।
ভাষা মানুষের আত্মবিকাশের পথ সম্প্রসারিত করে। আমরা সবাই জানি, আমরা যদি জটিল ধারণাগুলো বুঝতে চাই, ব্যাখ্যা করতে চাই বা কোনো বিষয়ে সত্যিকারের অনুভূতি প্রকাশ করতে চাই, তাহলে মাতৃভাষার বিকল্প নেই। মাতৃভাষায় শিক্ষার বিষয়টি সব সময় প্রাকৃতিক ও স্বয়ংক্রিয়। এশিয়া, বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়া ও আফ্রিকার অনেক দেশ স্বাধীনতার পরও ঔপনিবেশিক শক্তির ভাষা ব্যবহার করে চলেছে। এটা ঘটছে, কারণ ঔপনিবেশিক শক্তি তাদের নিজস্ব ভাষাকে উচ্চশিক্ষার জন্য ভাষা হিসাবে চালু করেছিল। এমনকি অফিস-আদালতেও ছিল তাই। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে জনসাধারণের ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু উচ্চস্তরে গিয়ে শিক্ষার মাধ্যম হয়েছে একটি বিদেশি ভাষা। বাংলাদেশেও এ রকমটাই ঘটছে এবং স্কুল থেকে আসা ছাত্ররা মাতৃভাষা বাংলা ব্যবহার করে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজি মাধ্যমে একটি অসুবিধাজনক অবস্থানে পড়ে। এমনকি গত শতাব্দীর শেষের দশকগুলোতে ইংরেজি উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হতো চিকিৎসা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও আইনের মতো বিশেষায়িত ক্ষেত্রে।
বর্তমানে সেই চর্চায় পরিবর্তন হয়তো কিছুটা এসেছে, তবে পুরোপুরি নয়। এর অজুহাত হিসাবে দেখানো হয়, আমাদের কাছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে বাংলা ভাষায় এখনো ভালো বই নেই বা বিশেষায়িত বিষয়গুলোতে পরিভাষা সেভাবে এখনো সৃষ্টি হয়নি। এ ছাড়া দেশে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও চিকিৎসা শাস্ত্রে বাংলা ভাষায় ভালো কোনো জার্নালও প্রকাশ হয় না। আমার অভিজ্ঞতা থেকেই একটা উদাহরণ দিচ্ছি। সেটা ২০২১ সালের কথা। দেশের সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মান সম্পর্কিত পরিসংখ্যানমূলক একটি বিজ্ঞানভিত্তিক প্রবন্ধ বাংলা ভাষায় জার্নালের অভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম হইনি। অর্থাৎ দেশে উচ্চশিক্ষার স্তরে বাংলা ভাষাকেন্দ্রিক বিজ্ঞানের প্রসার লাভ আশানুরূপভাবে ঘটেনি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয় নিয়ে জার্নাল প্রকাশনার ব্যাপারে বাংলা একাডেমি ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রধান ভূমিকা থাকা প্রয়োজন। দেখা যাচ্ছে, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয় আগের মতো বিজ্ঞান প্রকাশনায় সক্রিয় ভূমিকা রাখছে না। ওই সংস্থাগুলো আরও বেশি সক্রিয় হলে উচ্চ পর্যায়ে বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তক, বিজ্ঞান সাহিত্য, বিজ্ঞান গবেষণাপত্র প্রকাশনার মাধ্যমে দেশের ছাত্র-শিক্ষক ও গবেষণা কর্মীরা উৎসাহিত ও উপকৃত হতেন।
‘ছেলেবেলা’ গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ তার সেজদাদার উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছিলেন ‘আগে চাই বাংলা ভাষার গাঁথুনি, তার পরে ইংরেজি শেখার পত্তন।’ আমাদের দেশে, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে ভাষা সচেতনতার অভাব প্রকট আকার ধারণ করেছে। সমস্যা হচ্ছে, নতুন প্রজন্ম বাংলা বা ইংরেজি কোনো ভাষাই ভালোভাবে শিখছে না। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রমিত ভাষার ব্যবহার যেন প্রায় নির্বাসিত। তারা বাংলার সঙ্গে ইংরেজি-হিন্দি মিশিয়ে এক জগাখিচুড়ি ভাষার জন্ম দিচ্ছে। এতে ভাষা বিকৃতি ঘটছে চরমভাবে। ফেসবুক-ইন্টারনেটে যোগাযোগের ক্ষেত্রে জন্ম নিচ্ছে এক অদ্ভুত ভাষা। রোমান হরফে বাংলা লেখা হচ্ছে। সেই বাংলার ধরনও আবার বড়ই বিচিত্র। প্রকৃতপক্ষে ভাষা ব্যবহারের সর্বক্ষেত্রেই যেন এক ধরনের বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে।
এটা দুঃখজনক যে, বিজ্ঞানের পরিভাষা এখনো সম্পূর্ণ বাংলা হয়নি। আমরা ইতোমধ্যেই দেখেছি, মাতৃভাষা ব্যবহারে সাফল্য অর্জন করেছে এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ কোরিয়া, চীন ও জাপান। তারা সর্বস্তরে, প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা, এমনকি গবেষণার প্রতিটি ক্ষেত্রে মাতৃভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করে বৈশ্বিক উন্নয়নের শীর্ষ পর্যায়ে পৌঁছেছে। ইউনেস্কোসহ অনেক সংস্থার গবেষণাই তা প্রমাণ করেছে। শিক্ষার সর্বস্তরে মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষার উপকারিতা জানা সত্ত্বেও আমরা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বিজ্ঞানচর্চায় বাংলাকে এখনো গ্রহণ করতে পারছি না।
বাংলা ভাষা একটি ক্রমবর্ধমান ভাষা। তার শব্দভাণ্ডারের বিস্তৃতি ঘটেছে। নতুন নতুন শব্দ আসছে বাংলা ভাষায়। তবে এটা অনস্বীকার্য যে, শব্দভাণ্ডার স্ফীত হলেও বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, আইনি বিষয়সহ বিশেষায়িত বিষয়গুলো এখনো ইংরেজির ওপর নির্ভরশীল। এর অন্যতম কারণ স্বাভাবিকতা ও সহজবোধ্য পরিভাষার অভাব। প্রযুক্তিবিদ্যা, চিকিৎসা শাস্ত্রে ও বিজ্ঞান শিক্ষার উচ্চপর্যায়ে বাংলার প্রচলন প্রাথমিকভাবে কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হলেও মোটেই তা দুরূহ বা দুঃসাধ্য নয়। আইন বিষয়ের ব্যাপারটি আইনবিদরাই ভালো বলতে পারবেন। তবে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান ও সাবেক প্রধান বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান একত্রে প্রণয়ন করেন ‘আইন-শব্দকোষ’, যা আদালতে বাংলায় রায় প্রদান, মুসাবিদা লিখন কিংবা সংসদের বাংলায় আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে একটি সর্বোত্তম গ্রন্থ।
বাংলায় লেখা করোনাভাইরাস সম্পর্কিত আমার সাম্প্রতিক একটি বই লিখতে গিয়ে আমি দেখেছি, কাঠিন্যে ভরা কতসব পরিভাষামূলক শব্দ, যা মোটেই সহজবোধ্য নয়। তা ছাড়া সেগুলো ল্যাটিন শব্দের সঙ্গে আদপে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আমি সেসব ক্ষেত্রে ল্যাটিন শব্দগুলো প্রায় ক্ষেত্রে বাংলা অক্ষরে ব্যবহার করেছি। বহুমূত্র উপসর্গ অনেক রোগের কারণেও হতে পারে-যেমন বিষাদগ্রস্ততা, বর্ধিত ক্যালসিয়াম বা থাইরক্সিন হরমোন, ‘প্রস্টেট গ্রন্থি’র জটিলতা ইত্যাদি। আর ক’জনেই বা ডায়াবেটিস মানে ‘মধুমেহ’ বুঝবে! অথচ বাঙালির মুখে মুখে কিন্তু ডায়াবেটিস, লেখেনও তারা বাংলায় ‘ডায়াবেটিস’। তাই এর পরিভাষা ডায়াবেটিস হওয়াটাই যৌক্তিক। এ রকম আরও অনেক শব্দ: মিউটেশন, ইমিউন সিস্টেম, অ্যান্টিবডি-যা যথাক্রমে পরিব্যক্তি, অনাক্রম্যতন্ত্র, প্রতিরক্ষিকা হিসাবে পরিভাষিত। ফলে বাংলায় লেখা ওই ইংরেজি বা ল্যাটিন শব্দগুলো একটা আন্তর্জাতিক রূপও পাবে। আর এগুলো আমাদের মুখে ব্যবহৃত হয়ে ‘বাংলা’ হয়েই যাবে, যেমন হয়েছে সেল ফোন (‘মুঠোফোন’ কোনো টেকসই পরিভাষা হতে পারে না), টেলিভিশন বা কম্পিউটার। এসব ক্ষেত্রে যত বিদেশি শব্দ আসবে, ততই মঙ্গল। কারণ এসব বিষয়গুলো আন্তর্জাতিক যোগসূত্রে গাঁথা। কাজেই আমার অভিমত এই যে, বিজ্ঞান আর চিকিৎসা ও প্রকৌশল শাস্ত্রের বইতে বাংলা অক্ষরেই শক্ত ল্যাটিনজাত শব্দ ব্যবহার করতে হবে। উদ্দেশ্য, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পরিভাষাকে বিশ্বমুখী ও বিজ্ঞানসম্মত করা।
এখন থেকে শতাধিক বছর আগে বিখ্যাত বাঙালি রসায়নবিদ প্রফুল্ল চন্দ্র রায় মারকিউরাস নাইট্রাইট আবিষ্কার করে সমগ্র বিশ্বে অমর হয়ে আছেন। বাঙালি জাতিকে অন্তর থেকে বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলাই ছিল তার আজীবনের সাধনা। বাংলা ভাষার প্রতি তার ভালোবাসা ছিল প্রগাঢ়। তার কর্মজীবনে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যপনায় তিনিই একমাত্র বাংলা ব্যবহার করতেন। বিজ্ঞানের প্রসারে মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চা প্রকল্পে তার অবদানও ছিল প্রচুর। তার অনেক বিখ্যাত ছাত্রের মধ্যে ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাথ সাহা প্রমুখ। এরা ছিলেন বিজ্ঞানের পথিকৃৎ।
পদার্থবিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু বাংলায় বিজ্ঞানচর্চার প্রবল সমর্থকই ছিলেন না, তার জীবনে তিনি বাংলায় বিজ্ঞানচর্চার ধারাটিকেও বৃদ্ধি করে গেছেন। এ প্রসঙ্গে তার একটি উক্তি অমর হয়ে আছে-‘যারা বলেন, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা হয় না; তারা হয় বাংলা জানেন না, নয় বিজ্ঞান বোঝেন না।’ বাংলায় বিজ্ঞানচর্চার প্রসারের উদ্দেশ্যে ‘বিজ্ঞান পরিচয়’ নামে একটি পত্রিকাও তিনি প্রকাশ করেছিলেন। এ ছাড়া বাঙালিরা বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে নিউটন-আইনস্টাইনের চেয়ে কম যায় না, তা প্রমাণ করেন জগদীশ চন্দ্র বসু।
উচ্চশিক্ষায় ব্যবহার উপযোগী মাতৃভাষার বইয়ের সংকট এখনো রয়ে গেছে। তবে কলা ও মানবিক অনুষদ বা ব্যবসায় প্রশাসন বিষয়গুলোতে পাঠ্যবইয়ের সংকট আছে, তা বলা ঠিক হবে না। বাংলায় চিকিৎসা শাস্ত্র, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়গুলোতে এখনো যে উচ্চমানের বইয়ের প্রাপ্যতা নেই-তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এসব ক্ষেত্রে এখনো শিক্ষার্থীদের অনেকটাই ইংরেজি বইয়ের ওপর নির্ভর করতে হয়। তবে বিজ্ঞানভিত্তিক বইগুলো শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন সামনে রেখে সেভাবে বাংলায় অনূদিত হয়নি বলে সেখানেও এক রকম সীমাবদ্ধতা রয়েছে।
একুশের আরও একটি অর্জন হচ্ছে, বাঙালির চেতনা ও আবেগের সঙ্গে জড়িত আমাদের বইমেলা। করোনা অতিমারির কারণে এবারের গ্রন্থমেলা দুই সপ্তাহ দেরিতে শুরু হয়েছে। বইমেলা মানেই পাঠক, লেখক ও প্রকাশকের মিলনমেলা। বলা বাহুল্য, আমাদের পাঠ্যাভ্যাস বাড়ানোর পাশাপাশি বই কেনার অভ্যাসও বাড়িয়ে দেয় এ বইমেলা। যে কোনো ভাষার চেয়ে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন সর্বজনস্বীকৃত। বইমেলাকে কেন্দ্র করে দেশে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার প্রয়াস আরও বেগবান হোক, এটাই প্রত্যাশা।
ড. রাশিদুল হক : সাবেক উপ-উপাচার্য, বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী; সাবেক অধ্যাপক, এমোরি বিশ্ববিদ্যালয়, আটলান্টা, যুক্তরাষ্ট্র; অধ্যাপক, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
