শতফুল ফুটতে দাও
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ভালো-মন্দ
ড. মাহবুব উল্লাহ্
প্রকাশ: ১৮ মার্চ ২০২১, ১২:০০ এএম
প্রিন্ট সংস্করণ
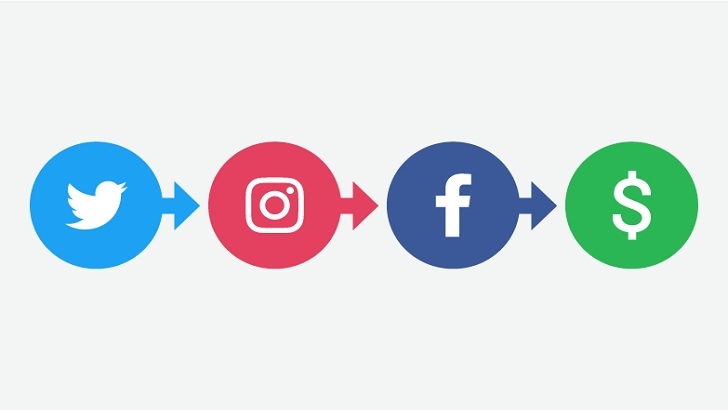
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সমাজে কী ভূমিকা পালন করে তা নিয়ে প্রচুর আলোচনা হচ্ছে এবং এই আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক অনেকদিন অব্যাহত থাকবে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যেমন ভালো কাজে ব্যবহৃত হতে পারে, তেমনি ক্ষতিকর কাজেও ব্যবহৃত হতে পারে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বা ডিজিটাল মাধ্যম যাতে অনৈতিক ও অনাকাঙ্ক্ষিত কাজে ব্যবহৃত হতে না পারে তার জন্য সরকার ডিজিটাল সিকিউরিটি আইন প্রণয়ন করেছে এবং বেশ কিছু ক্ষেত্রে এটির অপপ্রয়োগ মানুষের মধ্যে বিশেষ করে মিডিয়াকর্মীদের মধ্যে হতাশা ও ক্ষোভ সৃষ্টি করেছে।
অতি সাম্প্রতিককালে দুজন ব্যক্তির ওপর ডিজিটাল সিকিউরিটি আইন প্রয়োগে দেখা গেছে প্রচণ্ড নিষ্ঠুরতা। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো এমনভাবে কাজ করেছে, তাতে যে কোনো নাগরিকেরই তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দিহান হওয়ার কথা এবং হয়েছেও তাই। যে দুজন ব্যক্তি আইনের নামে দানবিক শক্তির ভয়াবহতার শিকার হয়েছেন তাদের জন্য সাধারণ মানুষের মনে প্রচণ্ড সহানুভূতি সৃষ্টি হয়েছে।
অপরদিকে সরকার ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কার্যকলাপ সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। কোনো সরকারের জন্যই এমন নেতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি না হওয়াই কাম্য। যে দুজন ব্যক্তি অতি সাম্প্রতিক সময়ে ডিজিটাল সিকিউরিটি আইনের ভিকটিম, তারা হলেন কারারুদ্ধ অবস্থায় মৃত্যু বরণকারী মুশতাক ও কার্টুন আঁকিয়ে কিশোর নামে এক ব্যক্তি। ডিজিটাল সিকিউরিটি আইন দারুণ প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়েছে। অনেকেই আইনটি বাতিল করার পক্ষে।
অবশ্য কেউ কেউ মনে করেন আইনটির আপত্তিকর ধারাগুলো অপসারণ করে এর সংশোধন করা উচিত। যারা আইনটি বাতিল করার পক্ষে তারা মনে করেন, দেশের প্রচলিত আইনেই গণমাধ্যমের অপব্যবহার রোধ করা সম্ভব। আমরা আশা করব, স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তিতে যেসব কালো আইন মানুষকে নিপীড়িত করে সেগুলো ছেঁটে ফেলা হবে। গণতন্ত্রের পথকে করে তোলা হবে আরও প্রশস্ত। হাইব্রিড গণতন্ত্র কারোরই কাম্য নয়।
গত ১৪ মার্চ আমার ফেসবুকে একটি ছবি ভেসে ওঠে। ছবিটি হলো চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগে আমার সহকর্মী প্রফেসর ড. হরেন্দ্র কান্তি দে এবং তার স্ত্রী পূরবী দে’র। তবে ফেসবুকের ছবিতে স্বামী ও স্ত্রী যুগলবন্দি হলেও ফেসবুকের অ্যাকাউন্টটি মিসেস পূরবী দে’র। ছবিতে তাদের খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। এই ছবি দেখে মনে হয় না, প্রফেসর দে ভয়ানক অসুস্থ।
আমি ২০০৫ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগে প্রফেসর হিসাবে নিয়োগ পাই এবং এই দায়িত্বে বিলম্ব না করে যোগদান করি। প্রফেসর দে’র স্ত্রী পূরবী দে ৯০-এর দশকের শুরুর দিকে চট্টগ্রাম ছেড়ে কলকাতায় চলে যান। প্রফেসর দে তার এই পারিবারিক সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আমাদের কাউকে কখনোই কিছু বলেননি। মজার ব্যাপার হলো, আমি এবং আমার স্ত্রী দিল্লি যাওয়ার জন্য বিমানের চট্টগ্রাম-কলকাতা ফ্লাইট ধরার জন্য এয়ারপোর্টের প্যাসেঞ্জার লাউঞ্জে বসেছিলাম।
কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখতে পেলাম মিসেস দে’ও আমাদের সঙ্গে একই ফ্লাইটে কলকাতা যাচ্ছেন। সোফায় আমাদের পাশেই তিনি বসেছিলেন। আমার স্ত্রী এবং মিসেস দে গল্প করছিলেন। কিন্তু তিনি আমাদেরকে ন্যূনতম ইঙ্গিত দেননি যে, এই যাত্রার মধ্য দিয়েই তার বাংলাদেশে অবস্থানের পরিসমাপ্তি। আমরাও ভাবতে পারিনি কলকাতায় তিনি কী জন্য যাচ্ছেন।
১৯৪৭ সালে যখন ভারতবর্ষে ২টি রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়, তখন পাকিস্তান থেকে হিন্দু নাগরিকরা ব্যাপকভাবে দেশত্যাগ করেন। একইভাবে ভারত থেকে অনেক মুসলমান নাগরিক পাকিস্তানে চলে আসেন। ব্যাপকহারে হিন্দু ও মুসলমানদের নিজ নিজ জন্মভূমি পরিত্যাগ করে নিজ সম্প্রদায়ের মানুষরা যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে তাদের নতুনভাবে জীবনযাপনের চেষ্টা দক্ষিণ এশিয়া উপমহাদেশের সমাজ জীবনে ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা ঘটায়।
১৯৭১-এ বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ হয়েছিল। এই যুদ্ধে বাংলাদেশকে সর্বতোভাবে সাহায্য করার চেষ্টা করে ভারত। ভারতের এই সাহায্য ও সহযোগিতা নিছক পরার্থপরতা বা সহমর্মিতার দৃষ্টান্ত ছিল না। ভারত এই যুদ্ধের মধ্য দিয়ে চিরবৈরী পাকিস্তানকে দুর্বল করতে চেয়েছিল। বাংলাদেশের মানুষ চেয়েছিল স্বাধীনতা ও মুক্তি। চেয়েছিল পাকিস্তানের জল্লাদ বাহিনীর গণহত্যার অবসান। বাংলাদেশের মানুষ স্বপ্ন দেখেছিল আত্মমর্যাদা বজায় রেখে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে।
পাকিস্তানি বাহিনী ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ ভারতের সশস্ত্র বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। বাংলাদেশ সৃষ্টির পর অনেক সমাজতত্ত্ববিদ বলেছিলেন, ৭১-এর যুদ্ধের মধ্য দিয়ে দ্বি-জাতিতত্ত্বের অবসান ঘটল। কিন্তু বাংলাদেশের অভ্যুদয় সত্ত্বেও দেখা গেল অনেক সংখ্যালঘু পরিবার ভারতে চলে যাচ্ছে এবং সেখানে থিতু হওয়ার চেষ্টা করছে। এ কারণেই হয়তো অন্নদাশংকর রায়ের মতো বোদ্ধা ব্যক্তি দ্বি-জাতিতত্ত্বের অবসান সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন।
প্রফেসর হরেন্দ্র কান্তি দে’র সঙ্গে আমার চমৎকার একটি সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। আমি তার পাণ্ডিত্যকে শ্রদ্ধা করতাম। তিনি নানা ধরনের গ্রন্থাদি পাঠ করতেন। রাজনৈতিক চিন্তার দিক থেকে বামপন্থী মনোভাবাপন্ন হলেও তিনি কখনো কোনো সভা সেমিনারে রাজনৈতিক বিষয়াদির ওপর আলোচনায় যোগ দিতেন না। বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক শিক্ষক রাজনীতিতে তিনি কখনো সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেননি। তবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে গিয়ে তার নিশ্চয়ই পছন্দ-অপছন্দ ছিল।
প্রফেসর হরেন্দ্র কান্তি দে’র স্ত্রী ও সন্তানরা কলকাতায় চলে গেলেও প্রফেসর দে চট্টগ্রামে থেকে গেলেন এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে অধ্যাপনা অব্যাহত রাখেন। তিনি বড় একা হয়ে পড়েছিলেন। একটি ছোট্ট বাসা ভাড়া নিয়ে তিনি থাকতেন। এখানে তার কোনো সঙ্গী-সাথী ছিল না। প্রফেসর দে শহরের কোনো জায়গায় যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করলে হেঁটেই চলে যেতেন। এর জন্য আমি তাকে প্রায়ই বলতাম, দাদা আপনি যেভাবে হাঁটাহাঁটি করেন, তার ফলে আপনি হৃদযন্ত্র ও মস্তিষ্কের কোনো রোগে আক্রান্ত হবেন না।
আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে আসার বছর দুয়েক পরে প্রফেসর দে মস্তিষ্কের স্ট্রোকে আক্রান্ত হন। তিনি চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রায় জ্ঞানশূন্য অবস্থায় চিকিৎসা নেন। প্রফেসর দে’র স্বাস্থ্যগত এই দুর্যোগ সম্পর্কে আমাকে ফোন করে জানিয়েছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক গোলাম মুস্তাফা। প্রফেসর দে’র স্বাস্থ্যগত সংকটে তার স্ত্রীর কাছে থাকাটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। কিন্তু তিনি কিভাবে চট্টগ্রামে আসবেন, তাকে তো বাংলাদেশের ভিসা পেতে হবে।
ওই সময় ভারত ও বাংলাদেশ দুই দেশেই ভিসার জন্য দীর্ঘসূত্রতায় পড়তে হতো। প্রফেসর মুস্তাফা আমাকে অনুরোধ করলেন, কলকাতায় বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনারের অফিসে যদি কোনো পরিচিত ব্যক্তি থাকেন তাকে আমি যেন অনুরোধ করি মিসেস দে’র ভিসা তাৎক্ষণিকভাবে প্রদান করার জন্য। সেই সময় কিছুতেই মনে করতে পারছিলাম না, ডেপুটি হাইকমিশনারের অফিসে আমার পরিচিত কে আছেন।
কিছুক্ষণ পর আমার মনে পড়ল কাউন্সেলর বিভাগের যিনি প্রধান তিনি আমাকে শ্রদ্ধা করতেন এবং ভালোবাসতেন। তাকে ফোন করে আমি আমার অনুরোধের কথা জানাই। তিনি কথা দিলেন ভিসার জন্য পাসপোর্ট সাবমিট করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভিসা মঞ্জুর করে দেবেন। তার এই আশ্বাসের পর মিসেস দে’কে ফোন করে জানানো হলো তিনি যেন কালবিলম্ব না করে আমার রেফারেন্স দিয়ে ওই কর্মকর্তার সঙ্গে দেখা করেন। মিসেস দে ওই কর্মকর্তার সঙ্গে দেখা করার ২০-৩০ মিনিটের মধ্যেই বাংলাদেশে আসার ভিসা পেয়ে গেলেন।
পৃথিবীর মানুষ এক দেশ থেকে অন্য দেশে, এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে বিভিন্ন সময় ও যুগে অভিবাসন করেছে। তখন জাতিরাষ্ট্র ছিল না বলে পাসপোর্ট ও ভিসার প্রয়োজন হতো না। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, যে কারণেই হোক না কেন মিসেস দে’কে নিজ জন্মভূমিতে আসার জন্য ভিসার প্রয়োজন হচ্ছে। ইতিহাসের এই জটিল ও খেয়ালি গ্রন্থিগুলো বিচ্ছিন্ন করার জন্য প্রয়োজন গবেষণা।
প্রফেসর দে কিছুটা সুস্থ হলে তাকে কলকাতায় আরও ভালো চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। অনেক দিন তার সঙ্গে দেখা হয় না। আমরা একে অপরের সঙ্গে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার ওপর আলাপ-আলোচনা করতাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন একজন সহকর্মী পাওয়া খুবই সৌভাগ্যের ব্যাপার। ফেসবুকের মেসেঞ্জারের সুবাদে মিসেস দে এবং প্রফেসর দে আমার সঙ্গে কথা বললেন ১৫ মার্চ সকাল ১১টায়। তিনি আমার পরিবারের সদস্যরা কে কেমন আছে এবং কী করছে জানতে চাইলেন। তারা স্বামী ও স্ত্রী উভয়ই আমার পরিবারের সদস্যদের শারীরিক সুস্থতা এবং কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানতে চাইলেন। প্রফেসর দে এতবড় স্বাস্থ্যগত বিপর্যয়ের পরও বেঁচে আছেন এবং গুছিয়ে কথা বলতে পারছেন সেটা দেখে খুবই আনন্দিত হলাম।
প্রফেসর দে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর নিয়েছেন। তার মতো জ্ঞানী ও যোগ্য শিক্ষক তার সময়ে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে খুবই কম ছিল। প্রফেসর দে আমেরিকার বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি করেছেন। তিনি গাণিতিক অর্থনীতি এবং অর্থমিতি খুব ভালো করে শিখেছিলেন। গাণিতিক অর্থনীতির ওপর দুই খণ্ডে তিনি একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এটি বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত হয়।
এ ছাড়া আন্তর্জাতিক জার্নালেও তার লেখা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। বহু বছর পর এই মানুষটির সঙ্গে কথা বলতে পেরে আমার খুব ভালো লাগল। আমাদের দুজনের মধ্যে বয়সের ব্যবধান যতসামান্য। সৃষ্টিকর্তা আমাকে প্রফেসর দে’র মতো কঠিন স্বাস্থ্য সংকটে ফেলেননি। এজন্য আমি সৃষ্টিকর্তার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।
প্রফেসর দে’র জীবনের এ গল্পটি চিন্তক মানুষের জন্য গভীর চিন্তার খোরাক। দক্ষিণ এশিয়া উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক এখনো যে কতটা ভঙ্গুর তার একটি দৃষ্টান্ত আমরা পাই প্রফেসর দে’র জীবন থেকে। তিনি অধিকাংশ সময় কাটান শয্যাশায়ী অবস্থায়। তাকে ডাক্তারের কাছে যেতে হয় অ্যাম্বুলেন্সে। ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করে দেখেন অ্যাম্বুলেন্সের মধ্যে শায়িত অবস্থায়।
প্রফেসর দে এবং তার স্ত্রীর সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয় দীর্ঘ ১৫ বছর পর। ডিজিটাল প্রযুক্তি আমাদের কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। আমরা একে অপরের কণ্ঠস্বর শুনেছি। অর্থনীতি শাস্ত্র দিয়ে এর মূল্য নিরূপণ করা কঠিন। ডিজিটাল টেকনোলজির অপব্যবহার পরিত্যাগ করে সামাজিক গণমাধ্যম যেন মানুষকে একে অপরের কাছে নিয়ে আসতে পারে সেদিকেই আমাদের মনোযোগী হতে হবে। রাজনৈতিক হীন স্বার্থে এর ব্যবহার মোটেও কাম্য নয়।
ড. মাহবুব উল্লাহ : শিক্ষাবিদ ও অর্থনীতিবিদ

