
প্রিন্ট: ০১ মে ২০২৫, ০৩:০৪ পিএম
ড. মাহবুব উল্লাহ্
প্রকাশ: ১০ ডিসেম্বর ২০২০, ১২:০০ এএম
প্রিন্ট সংস্করণ
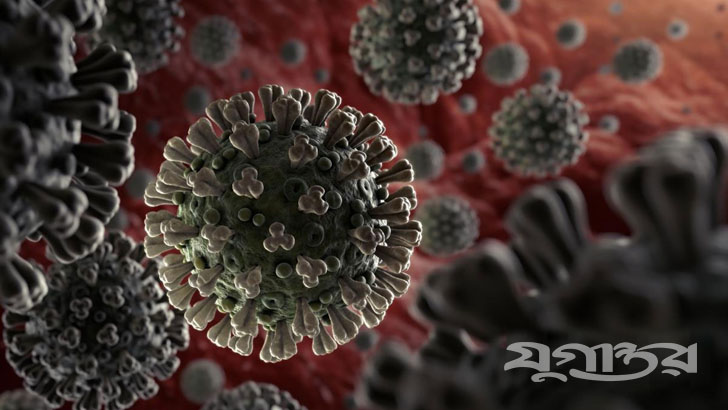
আরও পড়ুন
কোভিড-১৯ মানবজাতিকে ছাড়ছে না। ইতোমধ্যেই পৃথিবীর অনেক দেশই, বিশেষ করে পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রগুলো কোভিড-১৯-এর কারণে বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, কোভিড-১৯-এর দ্বিতীয় ঢেউয়ের সূচনা হয়েছে। শীত মৌসুমকে ভর করে কোভিড-১৯ ভয়াবহ রূপ নিতে পারে। কোভিড-১৯-এর কারণে পৃথিবীর উন্নত অনেক দেশই অর্থনৈতিকভাবে সংকুচিত হয়ে পড়েছে। বহু কর্মজীবী মানুষ বেকার হয়ে গেছে। কলকারখানাগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।
মানুষের হাতে যদি ক্রয়ক্ষমতা না থাকে, তাহলে চাহিদাও সংকুচিত হবে। চাহিদা সংকোচনের মানে হল ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস হয়ে যাওয়ায় মানুষের পক্ষে অনেক জিনিসই ক্রয় করা সম্ভব হবে না। সোজা কথায়-মানব জাতি এখন একটা দুষ্টচক্রের মধ্যে পড়ে গেছে।
কোভিড-১৯ যে ভয়াবহতা নিয়ে পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েছে, এর কারণে মানুষ এ ব্যাধি থেকে মুক্তির জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। এ রোগটির কোনো ওষুধ নেই। চিকিৎসকরা রোগটির বিভিন্ন লক্ষণের ওপর চোখ রাখেন এবং সে অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের ওষুধ ব্যবহার করেন। এ রোগে মারাত্মকভাবে যারা আক্রান্ত হন তাদের বাঁচানোর জন্য ভেন্টিলেটর এবং আইসিইউর সাহায্য গ্রহণ করতে হয়।
এ ব্যয়বহুল চিকিৎসা সত্ত্বেও অনেক রোগী মারা গেছেন। জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল আন্তোনিও গুতেরেস অতি সম্প্রতি মন্তব্য করেছেন, কোভিড-১৯ মহামারী আরও কয়েক দশক অব্যাহত থাকবে। যদি তা-ই হয়, তাহলে একবিংশ শতাব্দী মৃত্যুর শতাব্দীতে পরিণত হবে।
আন্তোনিও গুতেরেস চিকিৎসাবিদ্যা ও চিকিৎসা সংক্রান্ত গবেষণার সঙ্গে জড়িত নন। তা সত্ত্বেও তিনি কী করে এ রকম মহাবিপদের কথা বলতে পারলেন! জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল অনেক সূত্র থেকে যেসব তথ্য পান, এর বেশির ভাগই বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানরা পান না। সুতরাং জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেলের এ ভয়াবহ মন্তব্য বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকারকে গুরুত্বের সঙ্গে দেখতে হবে।
কোভিড-১৯-এর টিকা আবিষ্কারের জন্য শতাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে বলে গণমাধ্যম থেকে জানা যায়। এগুলোর মধ্যে পাঁচটি টিকা সফল হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। কিন্তু এ টিকাগুলো একজন টিকা গ্রহণকারী মানুষকে কতদিন পর্যন্ত এ ভাইরাসের আক্রমণ থেকে রক্ষা করবে, তা কেউ বলতে পারছে না। এ ব্যাপারটি জানা যাবে টিকাদানের পর। এর মধ্যে একটি টিকা সংরক্ষণ করতে হয় মাইনাস ৮০-৯০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে।
এ কারণে এ টিকাটি উন্নয়নশীল দেশগুলোর পক্ষে ব্যবহার করা সম্ভব হবে না। কারণ এসব দেশের এজন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নেই। বাংলাদেশ প্রাথমিক পর্যায়ে টিকাদানের জন্য ৭ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। কিন্তু এর পাশাপাশি টিকা পরিবহন এবং সংরক্ষণের জন্য কোনো ধরনের অবকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে কি না, তার কোনো উদ্যোগের খবর পাওয়া যাচ্ছে না।
বাংলাদেশ বিভিন্ন দেশ ও সংস্থা কর্তৃক আবিষ্কৃত টিকার যথাযোগ্যতা পরীক্ষার জন্য কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বলে শোনা যায় না। বাংলাদেশে বিগত দিনগুলোয় যেভাবে শেয়ার মার্কেট, ব্যাংক এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প থেকে লুটপাট করা হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে টিকা নিয়েও লোভী ব্যক্তিরা মুনাফা করতে পারে। অবশ্য অর্থনীতি শাস্ত্রের সঠিক সংজ্ঞানুসারে এটাকে মুনাফা না বলে Economic Rent বলাই সঠিক।
টিকা আবিষ্কারের জন্য আরেকটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। এটা হল মেধাস্বত্ব সংরক্ষিত করার প্রশ্ন। একমাত্র চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং আমার দেখায় অন্তত দু’বার বলেছেন, চীন দেশে যে টিকা তৈরি করা হয়েছে সে টিকা আন্তর্জাতিক গণদ্রব্য হিসেবে পৃথিবীর সর্বসাধারণের জন্য মুক্ত করে দেয়া হবে। এর ফলে ধনী-দরিদ্র এ টিকা গ্রহণ করলে তেমন কোনো অর্থের প্রয়োজন হবে না।
অতি সস্তায় এ টিকা সর্বসাধারণ গ্রহণ করতে পারবে। দুটি টিকার ক্ষেত্রে জানা গেছে একটি ডোজের জন্য যথাক্রমে পাঁচ ও বিশ ডলার ব্যয় করতে হবে। এ পরিমাণ অর্থ দিয়ে পৃথিবীর দরিদ্র এবং নিম্নবিত্ত লোকের পক্ষে এসব টিকা গ্রহণ করা সম্ভব হবে না। সোজা কথায়, এ টিকাগুলো পৃথিবীর বিপুলসংখ্যক মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরেই থেকে যাবে। এ টিকার জন্য রাষ্ট্রীয় ভর্তুকি প্রদান করা অনেক রাষ্ট্রের পক্ষেই সম্ভব হবে না।
নতুন আবিষ্কৃত টিকার এত দাম কেন? কারণ টিকা উৎপাদনে স্থির ব্যয় (Fixed Cost) খুবই বেশি। গবেষণা স্তরে অনেক অর্থ ব্যয় করতে হয়। ঝুঁকিও থাকে প্রচুর। এসব টিকা অন্তত ৩ দফা কয়েক সহস্র লোকের ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে হয় এগুলো কতটুকু নিরাপদ। তাছাড়া আরও বড় দাবি হচ্ছে মেধাস্বত্বের মূল্য। মেধাস্বত্ব হল আবিষ্কারকের মেধা, বুদ্ধি ও জ্ঞানের মূল্য।
এক্ষেত্রে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে দুটি মত আছে। প্রথমত আবিষ্কারক যদি তার কাজের মূল্য না পান তাহলে ভবিষ্যতে কেউ গবেষণা করতে চাইবে না। গবেষণাকে প্রণোদিত করার জন্যই মেধাস্বত্বের দাবি পূরণ করতে হয়। দ্বিতীয়ত, যারা এ মতের সঙ্গে একমত নন, তাদের যুক্তি হল মানব জাতির বিশাল সব আবিষ্কার, এমনকি অতি ক্ষুদ্র আবিষ্কার সভ্যতার সময়কালেই হয়েছে।
যে কোনো ব্যক্তি যদি জ্ঞান ও আবিষ্কারের ক্ষেত্রে অতি সামান্য অবদান রাখেন তাহলে এ অবদান গত কয়েক হাজার বছরে পুঞ্জীভূত জ্ঞানেরই অতি সামান্য অগ্রগতি। মানব জাতির শত শত প্রজন্মে যে জ্ঞানরাশি সৃষ্টি হয়েছে তার ওপর ভিত্তি করেই ঘটে সামান্য আবিষ্কার। কাজেই আবিষ্কারক তার আবিষ্কারকে এককভাবে নিজের মেধা ও বুদ্ধির ফল বলে দাবি করতে পারেন না।
জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে একটি অতি বিরাট সত্য হল, যারা জ্ঞানসাধক, তারা কোনো রকম পুরস্কারের আশায় জ্ঞান সাধনা করেন না। তারা জ্ঞান সাধনার মধ্যে আনন্দ খুঁজে পান। সুতরাং মেধাস্বত্ব বাবদ সত্যিকারের জ্ঞানসাধককে প্রণোদিত করার জন্য কোনো অর্থ প্রদান না করলেও তিনি জ্ঞান সাধনা করবেন। তবে তার সাধনাকে সহায়তা করার জন্য উন্নত গ্রন্থাগার এবং ল্যাবরেটরি থাকতে হবে। রাষ্ট্র এক্ষেত্রে বিনিয়োগ করবে। কর্পোরেট হাউসগুলোও উদ্ভাবনার জন্য অর্থব্যয় করে। তবে তাদের লক্ষ্য হল Economic Rent আদায় করা।
যে কোনো ওষুধ বা টিকার আবিষ্কার হলে সেসব টিকা বা ওষুধ এ ফর্মুলা ব্যবহার করে কোটি কোটি ডোজ উৎপাদন করতে অন্যদের তেমন কোনো ব্যয় হয় না। এ ধরনের কাজে গবেষণার জন্য বিনিয়োগ ব্যয়টিই প্রধান খরচ। এখন উদ্ভাবনা ও মেধাস্বত্ব সম্পর্কে কিছু কথা বলা প্রয়োজন। ক্ল্যাসিকেল প্রবৃদ্ধি তত্ত্ব আমাদের বলছে, পুঁজি সঞ্চিত হয়েই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হয়। এর পাশাপাশি শ্রমশক্তিরও প্রয়োজন হয়।
উন্নতমানের শ্রমশক্তি কেবল জনসংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে সৃষ্টি হয় না। শ্রমশক্তির জন্য স্বাস্থ্যসেবা এবং শিক্ষা প্রয়োজন। একটি নামকরা প্রবন্ধে ১৯৫৬ সালে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর রবার্ট সোলো দেখিয়েছেন, পুঁজির সঞ্চয়ন এবং শ্রমশক্তি নির্ণীত প্রবৃদ্ধির পুরোটা ব্যাখ্যা করে না। এর জন্য আমাদের বিবেচনায় নিতে হবে প্রযুক্তিগত অগ্রগতি। তাহলেই কেবল সঠিকভাবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ব্যাখ্যা করা যাবে।
১৯৫৬ সালের তুলনায় আজ ২০২০ সালে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনা প্রবৃদ্ধি প্রক্রিয়ার হৃৎপিণ্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে। একবিংশ শতাব্দীর অর্থনীতিকে জ্ঞানের অর্থনীতি বলা হয়। প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিশাল পরিবর্তন ঘটেছে। একবিংশ শতাব্দী হবে জ্ঞান অর্থনীতির যুগ।
অতীতের মতবাদ Catch-up economics-এর জন্য প্রযোজ্য। Catch-up economy কোনগুলো? এগুলো হল সে রকম দেশ যেগুলো নিম্ন আয় থেকে মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার চেষ্টা করছে। পৃথিবীতে যেসব দেশ এখন উন্নয়নের প্রয়াসে জড়িত তারা এর আগে যেসব দেশ উন্নতির শিখরে পৌঁছেছে তাদের ব্যবহৃত প্রযুক্তি ব্যবহার করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জাপান ৩টি উল্লেখযোগ্য দশকের মধ্য দিয়ে গেছে। ফ্রান্সও একই ধরনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গেছে। চীনে এ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ১৯৮০ থেকে।
কিন্তু এমন একটা সময় আসে যখন আগে উন্নত হওয়া দেশের প্রক্রিয়া ও কৌশল ব্যবহার করে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। কারণ সঞ্চিত পুঁজি ও শ্রম ব্যবহার করে উৎপাদন ক্রমান্বয়ে কমে আসে। তখন আর অতীতে উন্নত দেশের অনুকরণ করে প্রবৃদ্ধিকে এগিয়ে নেয়া যায় না। এ দেশগুলোকে নতুন পথের সন্ধান করতে হয় এবং প্রযুক্তিগত সীমান্ত অতিক্রম করার চেষ্টা করতে হয়। এ চেষ্টায় প্রয়োজন ভিন্ন এক সংস্কৃতি এবং প্রতিষ্ঠান।
বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে অবশ্যই উন্নতমানের প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হবে। গবেষণার জন্য সর্বোন্নত প্রক্রিয়া অনুসরণের চেষ্টা করতে হবে। শিক্ষার্থীদের উদ্যোগী হওয়ার জন্য উৎসাহিত করতে হবে। ব্যাংকগুলোকে এমন ঋণনীতি অনুসরণ করতে হবে যার ফলে শুধু বৃহৎ কোম্পানি এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীরই সুবিধা হয় না, যেসব উদ্যোগ উদ্ভাবনের চেষ্টা করে সেগুলোকেও ঋণ সুবিধা দিতে হবে।
বাংলাদেশে এখন বেশি বেশি করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলোর জন্য ঋণ দেয়ার দাবি জানানো হচ্ছে। কিন্তু উদ্ভাবনশীল উদ্যোগের জন্য কী করা উচিত, সে সম্পর্কে কোনো আলোচনা হয় না বললেই চলে। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ শুমপিটার ‘Creative destruction’-এর পক্ষে কাজ করার জন্য বলেছেন। এর ফলে নতুন উদ্ভাবনা ঘটবে এবং পুরনোগুলো প্রচলনের বাইরে নিক্ষিপ্ত হব।
স্বাধীন প্রতিযোগিতা কর্তৃপক্ষের কাজ হল বাজারে প্রবেশাধিকারের জন্য যেসব মেকি বাধা বিদ্যমান সেগুলোকে অপসারণ করা। এখানে হারানোর অনেক কিছু আছে। কারণ উদ্ভাবনের ওপর মূল্য সৃষ্টি নির্ভর করে। যেসব জাতি ভ্যালু চেইনের ঊর্ধ্বে অবস্থান করে তাদের পক্ষেই সম্পদশালী হওয়া সম্ভব।
পূর্বোক্ত আলোচনা থেকেই বিতর্কিত মেধাস্বত্বের কথা উঠেছে। এ থেকে আমরা কী বুঝতে পারি? মেধাস্বত্বের উপকারিতা ও ক্ষতিকর দিকগুলো কী? এর ফলে সরকার কি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়? এ চ্যালেঞ্জের একটি দৃষ্টান্ত হল পেটেন্ট থিকেট্স। পেটেন্ট আইন সম্পর্কে প্রায়ই আমরা অনেক কথা শুনি।
এ আইন থাকার ফলে প্রযুক্তিগত উন্নতি থেমে যায়। এর ওপর ভিত্তি করে আমরা যে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ করতে পারি তা হল, এ সমস্যাটির স্পষ্ট সমাধান করা। ফলে উদ্ভাবনার প্রণোদনা ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়া এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়।
ইউরোপ কয়েক বছর ধরে আর্থিক সংকটে ভুগছে। এ দুরবস্থার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় ইউরোপে উদ্ভাবনার হার কমে যাওয়া দায়ী। অবশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও Recession-এ ভুগেছে। সেটার কারণ ভিন্ন।
তবে এমন একদিন আসতে পারে যেদিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও এশিয়ার কয়েকটি দেশের পেছনে পড়ে যাবে। কারণ এসব দেশ জ্ঞান-অর্থনীতিতে প্রচুর বিনিয়োগ করেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের Thousand scholars scheme-এর কথা বলা যায়।
এ প্রকল্প অনুযায়ী চীন সরকার বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিত ও জ্ঞানী অধ্যাপককে চীনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় নিয়োগ দান করছে। এদের গবেষণা ফান্ডসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়। এদের সঙ্গে ধ্যানধারণা এবং বিশ্লেষণ বিনিময় করে চীনের অধ্যাপক ও শিক্ষার্থীরা জ্ঞানের ক্ষেত্রে অভিনব উদ্ভাবনের কথা ভাবতে পারছে।
চীন তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাপক বিনিয়োগ করে বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলছে। অচিরেই এগুলোর মান হার্ভার্ড, ক্যামব্রিজ এবং অক্সফোর্ডের মতো হবে বলে অনেক চীন বিশেষজ্ঞ মনে করেন। চীন সরকার উদ্ভাবনার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে।
সবকিছু বিবেচনা করলে দেখা যায় মেধাস্বত্বের ক্ষেত্রে সহযোগিতামূলক মডেল মেধাস্বত্বের প্যাটেন্ট আইনসহ অন্যান্য আইনের তুলনায় অনেক বেশি কার্যকর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এটা উপলব্ধি করে অনেক চীনা শিক্ষার্থীকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিতাড়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।
প্রশ্ন হল, এর ফলে জ্ঞান-সমাজের পথে চীনের অগ্রগতি কতটুকু ঠেকানো যাবে। এশিয়ায় আরও কয়েকটি সম্ভাবনাময় দেশের মধ্যে রয়েছে জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও ভারত। অবশ্য সাম্প্রতিককালে ভারতের প্রবৃদ্ধি অনেক নিচে চলে গেছে। জ্ঞান-সমাজ সৃষ্টির প্রশ্নে বাংলাদেশ কোথায় অবস্থান করছে? এ ব্যাপারে চিন্তা করলে ভয়ানক মানসিক কষ্ট পেতে হয়।
ড. মাহবুব উল্লাহ : শিক্ষাবিদ ও অর্থনীতিবিদ
