
প্রিন্ট: ০৬ এপ্রিল ২০২৫, ০২:৫৮ পিএম
একান্ত সাক্ষাৎকারে ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য
জটিল প্রেক্ষাপটে আসছে এবারের বাজেট
উচ্চ মূল্যস্ফীতি, ঋণের ঝুঁকি এবং জিডিপির প্রবৃদ্ধির নিম্নগতি * ভূরাজনীতিতেও কঠিন পরিস্থিতি * অপচয় রোধ, অনিয়ম ও দুর্নীতি বন্ধ এবং সুশাসন নিশ্চিত জরুরি
মনির হোসেন
প্রকাশ: ০৪ জুন ২০২৪, ১২:০০ এএম
প্রিন্ট সংস্করণ

আরও পড়ুন
বাজেট বাস্তবায়নে অপচয় রোধ, অনিয়ম ও দুর্নীতি বন্ধ এবং সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে। খুবই জটিল, আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে দেশ। এ মুহূর্তে বাজেট প্রস্তুতি কঠিন চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়েছে। অর্থনীতিতে সমস্যাগুলোর ত্রিযোগ ঘটেছে। সেখানে তিনটি বিষয় হলো উচ্চ মূল্যস্ফীতি, ঋণের ঝুঁকি এবং মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধির নিম্নগতি। ভূরাজনীতি বিশ্বব্যাপী ও আঞ্চলিক পরিস্থিতির ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে। যুগান্তরের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) বিশেষ ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য দেশের অর্থনীতি, সুশাসনসহ সামগ্রিক বিষয়ে খোলামেলা কথা বলেন। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন যুগান্তরের সিনিয়র রিপোর্টার মনির হোসেন।
যুগান্তর : বর্তমানে দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করছেন?
ড. দেবপ্রিয় : যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি চাপে রয়েছে দেশের সামষ্টিক অর্থনীতি। বিভিন্ন ধরনের রোগে আক্রান্ত। এই রোগ বা সমস্যাগুলোর ত্রিযোগ ঘটেছে। ইংরেজিতে বললে ‘ট্রাংগুলেশন অব প্রবলেমস’। অর্থাৎ তিনটি সমস্যা একত্রিত হয়েছে। এই সমস্যার মধ্যে একটি গত বছরই ছিল। যা হলো উচ্চ মূল্যস্ফীতি। সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়ার পরও মূল্যস্ফীতি অনিয়ন্ত্রিত। এটি গ্রামে এবং শহরে সব জায়গায়ই উচ্চ। এটি খাদ্যপণ্য ও বিভিন্ন সেবার জন্য সত্য। দ্বিতীয়ত ক্রমান্বয়ে আমাদের ঋণ পরিশোধের ঝুঁকি বাড়ছে। এটি শুধু বিদেশি ঋণ নয়, এখানে অভ্যন্তরীণ ঋণও আছে। কারণ সরকার বিদেশ থেকে যে টাকা নেয়, তার দ্বিগুণ টাকা নেয় অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে। এই দায়দেনা পরিস্থিতি বড় ধরনের সমস্যার ইঙ্গিত নিয়ে আসছে। তৃতীয় বিষয় হলো জিডিপি প্রবৃদ্ধির যে ধারা ছিল, বর্তমান অর্থবছরে তা বেশ কমেছে। এছাড়াও কর আহরণ কম থাকায় সরকারের খরচ করার ক্ষমতা সংকুচিত হয়েছে। এই তিন সমস্যা আগামী বাজেটকে নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করবে।
মূল্যস্ফীতি এখন ১০ শতাংশের আশপাশে। এতে ক্ষয় হচ্ছে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা। এটি দেশের আর্থ-সামাজিকভাবে দুর্বল জনগণকে বেশি আঘাত করছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশে যখন মূল্যস্ফীতি কমছে, তখন সেই সুফল বাংলাদেশের মানুষ পাচ্ছে না। ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে ঝুঁকি রয়েছে। বর্তমানে জিডিপির প্রায় ২৫ শতাংশের সমান বিদেশি ঋণ রয়েছে। পাশাপাশি ব্যক্তি খাতের বিদেশি ঋণ জিডিপির আরও ৫ শতাংশ। অর্থাৎ দেশি-বিদেশি মিলিয়ে বর্তমানে ঋণ জিডিপির প্রায় ৩০ শতাংশের সমান। এতে মুদ্রা বিনিময় হারের ওপর চাপ সৃষ্টি হয়েছে। টাকার মান কমছে। উপরন্তু এখন জ্বালানি ক্রয় ও আমদানি বাবদ অন্তত পাঁচ বিলিয়ন ডলার দিতে পারছি না। আমদানি বিল পরিশোধ হচ্ছে না। বিদেশি কোম্পানি মুনাফাও নিতে পারছে না। অর্থাৎ আমাদের গর্বের জায়গা ছিল, বিদেশিদের কাছে কখনো খেলাপি হইনি; সেই জায়গায় কিন্তু চির ধরেছে।
এর বাইরে প্রবৃদ্ধির হারে শ্লথ গতি। জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার প্রথম ছয় মাসে ৪ শতাংশে চলে এসেছে। কিন্তু সরকারের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৭ শতাংশের উপরে। সেই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে, বাকি সময়ে ১০ শতাংশের উপরে প্রবৃদ্ধি থাকতে হবে। সবাই জানে এটি বাস্তবসম্মত নয়। এক্ষেত্রে বড় সমস্যা হচ্ছে, সরকারের ব্যয়যোগ্য সম্পদ সীমিত, ব্যক্তিখাতের বিনিয়োগ স্থবির এবং সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) কম। প্রশ্ন হলো প্রবৃদ্ধি কমে যাওয়ার এই ধারাটি কি সাময়িক? এটি আগামী দুই এক বছরের মধ্যে ঘুরে দাঁড়াতে পারবে কি? এটি নির্ভর করছে আগামী বাজেটে কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়, তার ওপর অনেকটা।
যুগান্তর : এই পরিস্থিতিতে এবারের বাজেটে কী ধরনের চ্যালেঞ্জ থাকছে?
ড. দেবপ্রিয় : খুবই জটিল আর্থসামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এ বছর জাতীয় বাজেট আসছে। আগেই বলেছি, সমস্যা হলো গত ১০ বছরে রাজস্ব আদায় জিডিপির অনুপাতে বাড়েনি। তাই ঋণ করা ছাড়া এ মুহূর্তে সরকারের খরচ বাড়ানোর কোনো অবস্থা নেই। এই জটিল আর্থিক পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন কারণে। এর মধ্যে পণ্যমূল্য এবং বাজার মন্দার কারণও আছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বৈরী আবহাওয়াগত কারণ। একই সঙ্গে আঞ্চলিক রাজনীতি এবং ভূকৌশলগত বিভিন্ন পরিস্থিতি আমাদের অর্থনীতিকে প্রভাবিত করছে। এছাড়াও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) সঙ্গে একটি শর্তযুক্ত ঋণের মধ্যে রয়েছে দেশ। এসবই বিবেচনায় নিতে হবে জাতীয় বাজেট প্রস্তুতের সময়।
এ বছরের বাজেটের সঙ্গে আরও কয়েকটি বিষয় বিবেচনায় নিতে হবে। যেমন আমাদের এলডিসি বা স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণের প্রস্তুতি। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়নে অগ্রগতি অর্জন। এছাড়াও এই মুহূর্তে বিশ্বব্যাপী ভূরাজনৈতিক কঠিন পরিস্থিতি বিরাজ করছে। রাজস্ব আদায় বাড়ানো এবং নিয়মিত কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। ফলে আগের তিনটিসহ এসব সমস্যা মোকাবিলাই আগামী বাজেটের বড় চ্যালেঞ্জ। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। তবে কাজগুলো খুব সহজ হবে বলে মনে হয় না।
যুগান্তর : সব মহল থেকে কথা আসছে, দেশের রাজস্ব আদায় অনেক কম। বর্তমানে সরকারের রাজস্ব আয় এবং রাজস্ব ব্যয় সমান। অর্থাৎ যে টাকা আয় করে, সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন ভাতায় প্রায় সব ব্যয় হয়ে যায়। ফলে পুরো উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয় ঋণের টাকায়। এ অবস্থায় রাজস্ব আয় বাড়াতে কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া উচিত?
ড. দেবপ্রিয় : নিঃসন্দেহে দেশের রাজস্ব আদায় প্রতিযোগী এবং প্রতিবেশী যে কোনো দেশের চেয়ে কম। এটি অর্থনীতির বড় সমস্যা। তবে কর আদায় বাড়ানো প্রসঙ্গে তিনটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত সম্ভাব্য করদাতাদের আস্থাহীনতা বা ভীতি কমিয়ে আনতে হবে। এ জন্য কর কর্মকর্তাদের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা হ্রাস করা জরুরি। ডিজিটালাইজেশন এক্ষেত্রে বড় ভুমিকা রাখতে পারে। কারণ এর মাধ্যমে করদাতা ও আদায়কারীদের সম্পর্ক-সংস্পর্শ কমিয়ে আনা এবং সেবা উন্নত করা সম্ভব।
দ্বিতীয় বিষয় হলো ন্যায্যতা। একই ধরনের আয়ের ওপর ভিন্ন ভিন্ন কর দিতে হয়। কারণ বাংলাদেশের অনেক আয় পবিত্র নয়। অপবিত্র আয় কীভাবে ন্যায্য করের আওতায় আনা যায়, সেজন্য তথাকথিত কালো টাকা সাদা করার বিকৃত প্রক্রিয়া চালু হয়েছে। এখানে ন্যায্যতা স্থাপন করা জরুরি। তৃতীয়ত, শুধু আয়ের ক্ষেত্রে ডিজিটালাইজেশন করলে হবে না, হিসাব রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রেও ডিজিটালাইজেশন করতে হবে। না হলে প্রত্যাশিত ফল পাওয়া যাবে না। গবেষণায় দেখা গেছে, পৃথিবীর যেসব দেশে সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে গুণমান সম্পন্ন হয় এবং স্বচ্ছতা থাকে, সেসব দেশে করদাতারা কর দিতে বেশি অনুপ্রাণিত হয়।
যুগান্তর : আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ক্রমেই কমছে। আগামীতে বিদেশি ঋণ পরিশোধের বাধ্যবাধকতা বাড়বে। এই রিজার্ভ কী ধরনের ঝুঁকি তৈরি করতে পারে অথবা করণীয় কী?
ড. দেবপ্রিয় : রিজার্ভ পরিস্থিতি যতটা খারাপ হয়েছে, তা অব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়হীনতার কারণে। রিজার্ভের অর্থ সংগ্রহ ও ব্যয় এই দুটোর মধ্যে ভারসাম্য নেই। ফলে রিজার্ভ ধরে রাখা যাচ্ছে না। সরকার বাণিজ্য ও মুদ্রানীতি দিয়ে রিজার্ভের সমস্যা মোকাবিলার চেষ্টা করছে। দু’বছর আগে বলেছিলাম সরকারের দায়দেনার ক্ষেত্রে বড় ধরনের ধাক্কা আসবে। সেই ধাক্কা এখন এসেছে। বড় বড় প্রকল্পের জন্য বিভিন্ন মেয়াদে অর্থ নেওয়া হয়েছিল, তা পরিশোধের সময় এসেছে। কিন্তু এসব প্রকল্প থেকে রাতারাতি আয় আসে না। এলেও তা বিদেশি মুদ্রায় নয়। তাই বিদেশি দায়দেনা শোধ করার জন্য বৈদেশিক মুদ্রার মজুতের ওপর চাপ আরও বাড়বে। সেই সঙ্গে বিভিন্ন পণ্যের অপরিশোধিত দেনা শোধ করতে হবে। আবার বাজার স্থিতিশীল রাখতে ডলার বিক্রি করতে হবে। ফলে মজুতের ওপর চাপ আরও বাড়বে।
যুগান্তর : ব্যাংকিং খাতের নাজুক অবস্থা এবং শেয়ারবাজারে সংকট। বর্তমানে ব্যাংক একীভূত করা হচ্ছে। এসব বিষয় দেশের অর্থনীতিতে দীর্ঘমেয়াদে কী ধরনের বাস্তবতা তৈরি করবে?
ড. দেবপ্রিয় : ব্যাংক খাতের অবস্থা শোচনীয় এবং এটি একটি বড় চলমান সমস্যা। অনেক দিন ধরেই এই খাতের অবস্থা খারাপ, এখন সবচেয়ে খারাপ। ব্যাংকের অনাদায়ী ঋণের মাত্রা প্রতিদিন বাড়ছে। দেশের ব্যাংকিং খাত নির্যাতিত এতিমের মতো হয়ে আছে। দেখভাল করার কেউ নেই। এটা দেখভাল করার দায়িত্ব ছিল রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের। তারাও সেই দায়িত্ব পালন করে না। ব্যাংকের মন্দ ঋণ, সঞ্চয়ের ঘাটতি, পুঁজিকরণের ঘাটতি রয়েছে। তথাকথিত ব্যাংক একীভূত করার ভেতর দিয়ে এই সমস্যার সমাধান হবে না। এর একটি বড় কারণ হলো নীতি সমন্বয়ের অভাব। অন্যদিকে আরেকটি বড় কারণ হলো এগুলোকে মোকাবিলা করার জন্য যে রাজনৈতিক শক্তি দরকার, সেটি দেখছি না। বিপরীতে যারা সুবিধাভোগী, তুলনামূলকভাবে তাদের সামাজিক-রাজনৈতিক শক্তি অনেক বেশি। একই অবস্থা শেয়ারবাজারে।
যুগান্তর : দেশের অর্থনীতিতে শক্তির দিক কী আছে?
ড. দেবপ্রিয় : বাংলাদেশের অর্থনীতির এই মুহূর্তেও শক্তির জায়গা হলো কৃষি খাত। খাদ্য উৎপাদনের মাধ্যমে এই কৃষিই আমাদেরকে রক্ষা করছে। তাই এই খাতের যত্ন নিতে হবে। মনে রাখতে হবে কৃষকের কথা। এবার বহু প্রতিকূলতার মধ্যেও ফসল ভালো হয়েছে। বর্তমান বাজারব্যবস্থা, কৃষকের বিরুদ্ধে কাজ করছে। পণ্য উৎপাদনে এবং নিজের চাহিদা মেটাতে কৃষক বাজার থেকে সুবিধা পায় না। তাই আগামী বাজেটে কৃষিতে শর্তহীন সমর্থন প্রত্যাশা করছি। শক্তির আরেকটি উৎস হচ্ছে প্রবাসী কর্মজীবীরা। বৈদেশিক মুদ্রা সংকটের কারণে দেশের অর্থনীতিতে রেমিট্যান্স আয়ের গুরুত্ব আরও বেড়েছে। তাই এদের হয়রানি কমাতে হবে, টাকার বিনিময় হার নমনীয় করে তাদের ব্যাংকের মাধ্যমে অর্থ পাঠানোকে সুগম করতে হবে।





-67f23e1c2ccfe.jpg)

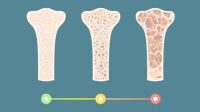

-67f239d3500f6.jpg)
