সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়
আগ্রহ কম গবেষণা ব্যয়ে
বরাদ্দ গত বছরের চেয়েও কমেছে সরকারিতে, বেসরকারি অনেক প্রতিষ্ঠানে একেবারেই নেই
মুসতাক আহমদ
প্রকাশ: ০৬ অক্টোবর ২০২১, ১২:০০ এএম
প্রিন্ট সংস্করণ
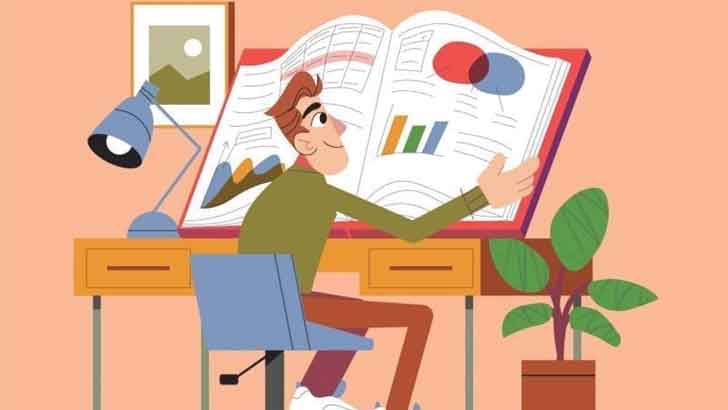
বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রধান কাজ হচ্ছে মৌলিক গবেষণা ও নতুন জ্ঞান সৃষ্টি। শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে গবেষক বা শিক্ষার্থীরা গবেষণা করবেন; যা বাস্তবজীবনে মানুষের কল্যাণে ব্যবহৃত হবে। কিন্তু বাংলাদেশের বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ই কেবল পাঠদান এবং পরীক্ষা নিয়ে গ্র্যাজুয়েট সৃষ্টির প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।
সংশ্লিষ্টদের মতে, এর মূল কারণ হচ্ছে গবেষণায় অপ্রতুল বরাদ্দ। দিন দিন এই খাতে ব্যয় কমছে। গত বছর এই খাতে সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বরাদ্দ ছিল মোট বাজেটের এক দশমিক ৬০ শতাংশ। সেখানে চলতি অর্থবছরে মাত্র এক শতাংশ বরাদ্দ রাখা হয়েছে।।
এছাড়া অন্য দেশগুলোর মতো বেসরকারি খাত থেকে এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পৃষ্ঠপোষকতা নেই। সব মিলিয়ে গবেষণা কাজে ব্যয়ের আগ্রহ খুবই কম। ফলে নিয়মিত ও মানসম্মত গবেষণা হচ্ছে না।
দেশের উচ্চশিক্ষার অ্যাপেক্সবডি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সর্বশেষ বার্ষিক প্রতিবেদনেও বেরিয়ে এসেছে এই চিত্র। সংস্থাটি বলছে, দেশে অর্ধেকের বেশি পাবলিক (সরকারি) বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১৯ সালে কোনো গবেষণা কার্যক্রম হয়নি। আর দুই-তৃতীয়াংশ শিক্ষকের ব্যক্তিগত গবেষণা বা পিএইচডি ডিগ্রি নেই। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ। ওইসব প্রতিষ্ঠানের গবেষণা করার মতো সিনিয়র শিক্ষকের ঘাটতি প্রকট। মোট শিক্ষকের মাত্র সাড়ে ১২ শতাংশ অধ্যাপক, যাদের অর্ধেকই খণ্ডকালীন বা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভাড়া করা। শিক্ষকের পদোন্নতিতে গবেষণা প্রধান বিবেচ্য বিষয় হলেও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে তা প্রায়ই ‘প্রমার্জন’ পাচ্ছে বলে অভিযোগ আসছে।
অবশ্য দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদরা বলছেন, এই অবস্থার জন্য কেবল বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষক দায়ী নন। দেশের সব উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানই মূলত ‘শিক্ষণ’ (টিচিং) বিশ্ববিদ্যালয়। ছাত্রছাত্রীদেরকে পড়িয়ে চাকরির বাজারের উপযোগী গ্র্যাজুয়েট সৃষ্টির লক্ষ্যে এসব প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হয়েছে। শুধু বাংলাদেশ নয়, ভারত, শ্রীলঙ্কাসহ দক্ষিণ এশিয়ার সব বিশ্ববিদ্যালয়েই এই একই পরিস্থিতি বিরাজ করছে।
উল্লেখ্য, সোমবার এক সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, গবেষণার জন্য আমাদের ফান্ড আছে। বিশেষ ফান্ড আছে। তবুও কেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের গবেষণার জন্য অনীহা তা আমি জানি না। অনেক শিক্ষক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানোর পর প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস নেওয়া শুরু করেন। টাকার মোহে না পরে গবেষণায় মনোযোগী হতে পারেন। গবেষণা হবে, হতে হবে-এমন মন্তব্য করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই মুহূর্তে বিজ্ঞান ও চিকিৎসা শাস্ত্রের বিষয়ে গুরুত্ব বেশি দিচ্ছি।
জানতে চাইলে ইউজিসির সাবেক চেয়ারম্যান ইমিরেটাস অধ্যাপক ড. একে আজাদ চৌধুরী যুগান্তরকে বলেন, তিন কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা অপেক্ষাকৃত কম গবেষণামুখী। প্রথমত, বাংলাদেশে গবেষণা সংস্কৃতি সেভাবে গড়ে ওঠেনি। দ্বিতীয়ত, সমাজে গবেষণা ও গবেষকের যথাযথ মূল্যায়ন নেই। আর তৃতীয়ত, এ খাতে খুবই অপ্রতুল বরাদ্দ, যা প্রয়োজনের তুলনায় কম। এর জন্য কেবল শিক্ষক নন, সমাজ, সরকার, রাষ্ট্রসহ আমরা সবাই দায়ী। অধ্যাপক চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ছিলেন।
ইউজিসির আরেক সাবেক চেয়ারম্যান এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল মান্নান বলেন, বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যে গবেষণা একেবারে হয় না তা নয়। কৃষি এবং বিজ্ঞানে এখনও বেশ গবেষণা হচ্ছে। বিশেষ করে কৃষিতে গবেষণা হয়েছে বলেই আমরা তিন-বেলা খাওয়ার মতো ধান উৎপাদনে যেতে পারছি। আমাদের খাবারের প্লেটে হারিয়ে যাওয়া দেশি প্রজাতির মাছ আসছে। তবে এটা ঠিক যে, সামাজিক বিজ্ঞানে কম-বেশি গবেষণা হলেও কলা এবং বিজনেস স্টাডিজ একদম পিছিয়ে আছে। এর প্রধানতম কারণ হচ্ছে, অর্থায়ন। বাজেটে এ খাতে বরাদ্দ যেমন অপ্রতুল, তেমনি পৃষ্ঠপোষকতা নেই। অধ্যাপকদের গবেষণার জন্য আমেরিকায় ইন্ডাস্ট্রি ও করপোরেট জগত থেকে মিলিয়ন ডলার দেওয়া হয়। আমাদের দেশে এই সংস্কৃতি আজও চালু হয়নি।
তবে বিশ্লেষকরা ভিন্ন অবস্থান থেকেও বিষয়টি মূল্যায়ন করেছেন। তাদের মতে, জবাবদিহিতা ও বিধানের অভাব এবং শিক্ষকদের অনীহার কারণেও গবেষণায় শিথিলতা বিরাজ করছে। কেননা, পিএইচডি ডিগ্রি ছাড়া যেখানে বিদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগই মেলে না, সেখানে বাংলাদেশে অনেকে পিএইচডি ডিগ্রি না করেও অধ্যাপক হতে পারছেন। পদোন্নতির ক্ষেত্রে গবেষণা প্রবন্ধ বা প্রকাশনার শর্ত আছে। কিন্তু কোথাও তা উপেক্ষিত হচ্ছে। আবার কোথাও একই প্রকাশনা বারবার দেখিয়ে পদোন্নতি নেওয়ার অভিযোগ আসছে। আবার যে ক’জন গবেষণা-প্রবন্ধ লিখছেন তাদের অনেকের বিরুদ্ধে চৌর্যবৃত্তির অভিযোগও আছে। বর্তমানে কেবল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই এমন অন্তত ৮টি অভিযোগের তদন্ত চলছে। ইউজিসিও পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ শিক্ষকের বিরুদ্ধে ওঠা এমন একটি অভিযোগের তদন্ত করছে।
সংশ্লিষ্টরা জানান, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের গবেষণায় হাতেখড়ি হয় তাদের নিজস্ব পিএইচডি ডিগ্রি করার মাধ্যমে। কিন্তু ৪৬ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়েরই দুই-তৃতীয়াংশ শিক্ষকের পিএইচডি ডিগ্রি নেই। ২০১৯ সালে দেশে ৪৬টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। ওই বছর ৪৬টির মধ্যে ১৯টির সব শিক্ষক মিলে একটি গবেষণা প্রকাশনা করতে পারেননি। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকরা ঠিকই সারা বছর পদোন্নতি-ইনক্রিমেন্ট সবই পেয়েছেন।
ইউজিসির প্রতিবেদন বলছে, উল্লিখিত বছরে দিনাজপুরের হাজী দানেশ ও সিলেট কৃষি ১টি করে, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও অ্যানিমেল সায়েন্স, যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ২টি করে এবং নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ৩টি প্রকাশনা বের করেছে। এই বছরে (২০১৯) সবচেয়ে বেশি গবেষণা প্রবন্ধ করেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা, ৯ হাজার ৪শ। রংপুরের রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় ১৭৩৯, টাঙ্গাইলের মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ৫৭১, রুয়েট ৫৬৬, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ৫১৮ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ৪৭২টি প্রকাশনা বের করেছেন।
বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মৌলিক জ্ঞান সৃষ্টির অন্যতম উপায় এমফিল ও পিএইচডি গবেষণা। ২০১৯ সালে সবকটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট এমফিল গবেষণা হয়েছে ২২০টি এবং পিএইচডি ২৩৩টি। এছাড়া চিকিৎসাবিজ্ঞানে এমএস/এমফিল/পিএইচডি,
এমএমএস/এমএমএড/এফসিপিএ হয়েছে ৮৮৬টি। এগুলোর মধ্যে এফসিপিএসে পাশের হার মাত্র ৫১ শতাংশ, এমএস/এমফিল/পিএইচডিতে পাশের হার ৬৪ শতাংশ। এমফিলে এই হার ৯০ শতাংশ। আর সবচেয়ে দৃষ্টিকটু হচ্ছে, ৪৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ২৪টিতেই এমফিল-পিএইচডি গবেষণা হয়নি। আবার তথ্য প্রদানে স্ববিরোধিতাও আছে। রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যক প্রকাশনা বের করার তথ্য দিয়েছে ইউজিসিকে। অথচ প্রতিষ্ঠানটিতে একটি এমফিল-পিএইচডি গবেষণাও হয়নি উল্লিখিত বছরে।
বার্ষিক প্রতিবেদনে আরও দেখা যায়, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সংস্থাটির পক্ষ থেকে গবেষণা খাতে ব্যয় হয় ৫ কোটি ৯৬ লাখ টাকা। ৩৯১ শিক্ষক এ তহবিল নিয়েছেন। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে ৩১৬ শিক্ষক প্রকল্প নেন।
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সাহাবুল হক যুগান্তরকে বলেন, যদিও তহবিল ঘাটতিকে গবেষণার অন্যতম প্রতিবন্ধক হিসেবে দেখা হয়, কিন্তু আমি মনে করি, এর চেয়েও বড় সংকট উদ্যম, উদ্যোগ আর ব্যবস্থাপনায়। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়েই এই খাতে কম-বেশি অর্থ বরাদ্দ থাকে। সরকার প্রতিবছর যে
অর্থ দেয় তার মধ্যে খুবই অল্প অংশ রাখা হয় গবেষণা খাতে। সিংহভাগ ব্যয় করা হয় বেতন-ভাতাসহ অন্য খাতে। বিদেশে গবেষণা না করলে পদোন্নতি না দেওয়া দূরের কথা, চাকরি চলে যাওয়ার ব্যবস্থা আছে; যেটা আমাদের দেশে নেই। তাই যতটুকু বরাদ্দ রাখা হয় সেটার সদ্ব্যবহার করে গবেষণা করা জরুরি। পাশাপাশি যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়, সেটা সিরিয়াস-গবেষকের উপকারে আসছে না। এদিকে ইউজিসির নজর দেওয়া প্রয়োজন।
গবেষণায় বরাদ্দ কমছে : এদিকে এই পরিস্থিতির মধ্যেও গবেষণায় সরকারি বরাদ্দ শতাংশের হিসাবে কমছে। চলতি অর্থবছর চলার জন্য দেশের ৪৯টি সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়কে ১০ হাজার ৩২ কোটি ৮১ লাখ টাকা দিয়েছে সরকার, যা ইউজিসি বণ্টন করেছে। ওই অর্থের মধ্যে ৫ হাজার ৮৭৫ কোটি ৮১ লাখ টাকা রাজস্ব খাতে এবং ৪ হাজার ১৫৭ কোটি টাকার উন্নয়ন খাতে দেয়া হয়েছে। রাজস্ব ব্যয়ের মধ্যে গবেষণা খাতে দেওয়া হয়েছে ১শ কোটি ৭৪ লাখ টাকা, যা মোট বাজেটের হিসাবে ১ শতাংশেরও কম। যদিও এই খাতে বরাদ্দ গত বছরের তুলনায় ৫১ শতাংশ বেড়েছে। কিন্তু মোট বাজেটের দিক থেকে কমেছে। গত বছর এই খাতে মোট বাজেটের ১ দশমিক ৬ শতাংশ অর্থ বরাদ্দ ছিল।
দেখা গেছে, কম বরাদ্দের এই ঢেউ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে লেগেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেটে গবেষণায় বরাদ্দ রেখেছে মাত্র ১১ কোটি টাকা, যা মোট ব্যয়ের ১ দশমিক ৩২ শতাংশ। গত অর্থবছরের তুলনায় এবার এ খাতে কমেছে বরাদ্দের পরিমাণ। গতবার বরাদ্দ ছিল বাজেটের মোট ৪ দশমিক ৭ শতাংশ অর্থ, যা টাকার হিসাবে ছিল ৪০ কোটি ৯১ লাখ টাকা। এর আগের বছরে (২০১৯-২০) গবেষণায় বরাদ্দ ছিল ৪০ কোটি ৮০ লাখ ৭০ হাজার টাকা, যা বাজেটের ৫ দশমিক ৪ শতাংশ ছিল।
তবে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের জন্য ইউজিসির গবেষণা তহবিলে বরাদ্দ বেড়েছে। গত বছর এ খাতে বরাদ্দ ছিল ১৫ কোটি। ৩ কোটি বাড়িয়ে এবার তা করা হয়েছে ১৮ কোটি টাকা বরাদ্দ ধরা হয়েছে। এই অর্থ এমফিল, পিএইচডি এবং বিশেষায়িত গবেষণার জন্য শিক্ষকদেরকে দেওয়া হয় বলে জানান ইউজিসি পরিচালক মো. ওমর ফারুখ।
বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় : বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল-পিএইচডি গবেষণার অনুমতি নেই। তবে ৮৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৮৫টিই দাবি করেছে যে তারা বিভিন্ন হারে গবেষণার জন্য ব্যয় করেছে। এই দাবিদারদের মধ্যে শিক্ষকদের ১২ হাজার টাকা দেওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ও আছে। তাই গবেষণায় আদৌ ব্যয় করা হয়েছে কিনা, সেই প্রশ্ন উঠেছে। এর চেয়েও উদ্বেগজনক তথ্য হচ্ছে, এসব প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডিধারী বা সিনিয়র শিক্ষকের সংকট প্রকট। মোট ১৬০৭০ শিক্ষকের মধ্যে অধ্যাপক মাত্র ২১১৩ জন, যা সাড়ে ১২ শতাংশ। তাদের মধ্যে আবার ১৩০৮ জনই খণ্ডকালীন। ইউজিসির কর্মকর্তারা বলছেন, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এ খাতে কমবেশি বরাদ্দ থাকলেও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সিংহভাগই বরাদ্দ রাখে না। কাগজে-কলমে রাখলেও তা আবার খরচ না করার নজির আছে।
৮৮ শতাংশই ব্যর্থ : ২০১৯ সালে ইউজিসি গবেষণার জন্য ১২৮৯টি প্রকল্প অনুমোদন দেয়। এর মধ্যে নানা কারণে বাতিল হয়েছে ৪৬৯টি। বাকিগুলোর মধ্যে মাত্র ১৫১টির কাজ শেষ হয়েছে।

