
প্রিন্ট: ০৩ এপ্রিল ২০২৫, ০৪:১৯ পিএম
বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে আমাদের আঞ্চলিক ভাষা
হোসাইন মোহাম্মদ জাকি
প্রকাশ: ০৭ মার্চ ২০২৫, ১২:০০ এএম
প্রিন্ট সংস্করণ
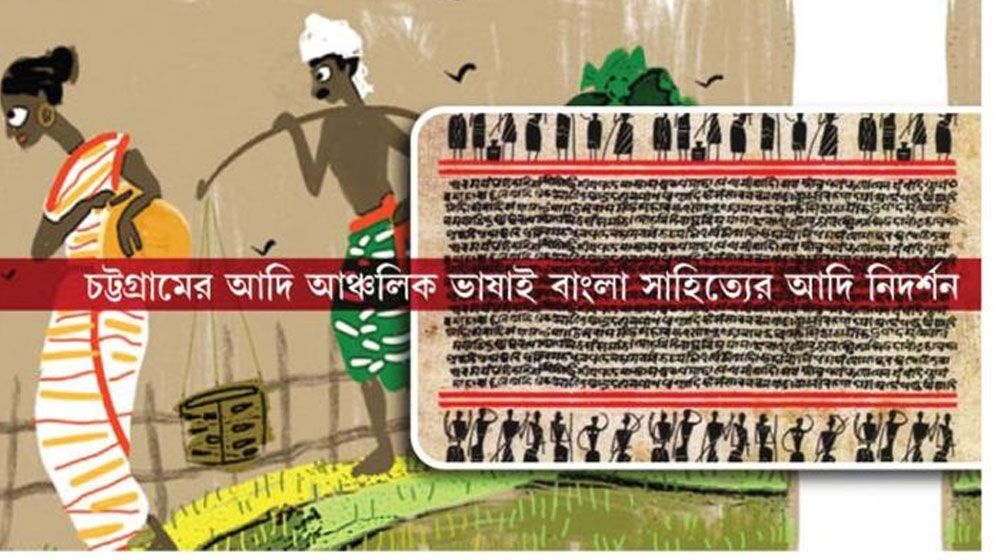
বাংলা ভাষা হাজার বছরের ঐতিহ্যে ঋদ্ধ। বিচিত্র-সংস্কৃতি আর বর্ণিল পেশার জনগোষ্ঠীর এ ভাষার রয়েছে অগণিত উপভাষা। ভাষাতাত্ত্বিকদের কাছে উপভাষাগুলোর বিশেষ গুরুত্ব আছে। বিশ্বব্যাপী প্রতিটি আঞ্চলিক ভাষারই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যে কোনো অঞ্চলের ভাষা তার আঞ্চলিক পরিচিতির অন্যতম নৃতাত্ত্বিক উপাদান। কোনো একটি উপভাষাকে ভিত্তি করে রাজনৈতিক, ধর্মীয় বা সাহিত্যিক প্রভাবে সাহিত্যিক ভাষা গড়ে ওঠে। সাহিত্য সৃষ্টিতে স্থানীয় ভাষাসম্পদ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। সাহিত্যে ব্যবহৃত আরবি-ফারসি তথা অন্যান্য বিদেশি শব্দ অপেক্ষা আঞ্চলিক ভাষায় ব্যবহৃত বিদেশি শব্দগুলো নানা কারণে ভাষাতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক গবেষণার ক্ষেত্রে অধিকতর মনোযোগ আকর্ষণ করে। ভাষার প্রকৃত এবং স্বাভাবিক জীবন তার উপভাষাগুলোতে। উপভাষার গুরুত্ব প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন-‘বাংলা ভাষায় একখানি ব্যাকরণ রচনা সাহিত্য পরিষদের একটি প্রধান কাজ। কিন্তু কাজটি সহজ নহে। এই ব্যাকরণের উপকরণ সংগ্রহ একটি দুরূহ ব্যাপার। বাংলাদেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশে যতগুলি উপভাষা প্রচলিত আছে তাহাদের তুলনাগত ব্যাকরণই যথার্থ বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণ।’
২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ (২৭তম সংস্করণ), ভাষার গুরুত্বপূর্ণ ওয়েবসাইট Ethnologue বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন ভাষার মধ্য থেকে সর্বাধিকসংখ্যক কথা বলা ২০০ আঞ্চলিক ভাষা নিয়ে ‘The Ethnologue 200’ প্রকাশ করেছে। এটি বিশ্লেষণে দেখা যায়, বিশ্বের মোট ভাষাভাষীর প্রায় ৮৮ শতাংশ আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে। বাংলাদেশের তিনটি বিশেষ অঞ্চলের ভাষা এ তালিকায় স্থান পেয়েছে। চট্টগ্রাম (৯৬তম), সিলেট (১১১তম) ও রংপুর (১২০তম)। তবে ২০২১ সালে এই অবস্থান ছিল যথাক্রমে চট্টগ্রাম (৯৪তম), সিলেট (১০৫তম) ও রংপুর (১১২তম)। অর্থাৎ তিন বছরে এসব অঞ্চলের ভাষায় কথা বলা মানুষের সংখ্যা ক্রমশ কমেছে। ধারণা করা যায় উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, নানা উপভাষাভাষী জনগণের সঙ্গে অধিকতর মিলন-মিশ্রণ-বিবাহ, ক্রমবর্ধমান শিক্ষার হার ইত্যাদির প্রভাবে এ উপভাষাগুলো নানা ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। সমাজ পরিবর্তনে উপভাষাও পরিবর্তিত হয়। কারণ সমাজের ওপর স্থানিক ও কালিক এ দুটো প্রভাব প্রচণ্ড। ভাষায়ও এ প্রভাব লক্ষণীয়। কালের পরিবর্তনে মানুষের মানসিকতা ও রুচিবোধের পরিবর্তনের ছাপ ভাষা কিংবা উপভাষায়ও যে বর্তায় সে সম্পর্কে ড. মুহম্মদ এনামুল হক তার ‘চট্টগ্রামী বাঙালার রহস্য-ভেদ’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এভাবে-“চট্টগ্রামের নিজস্ব বুলিতে যাহা মাত্র ১০/১৫ বৎসর পূর্বে ‘আতাইক্যা’ বা ‘আতাইক্কা’ (যাহা তাকাইবার পূর্বে ঘটে অর্থাৎ হঠাৎ বা আচম্বিতে ঘটে) বলিয়া প্রকাশ করা হইত, তাহা এখন স্ত্রীলোক ও নিতান্ত অশিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া আসিতেছে এবং তৎস্থলে শিক্ষিত ব্যক্তিরা ‘হঠাৎ’ বা তৎভাবজ্ঞাপক অন্য শব্দটিই বেশিরভাগ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।”
এথনোলগের তথ্য মোতাবেক, বিশ্বব্যাপী প্রায় এক কোটি ৩০ লাখ মানুষ চাঁটগাইয়া বুলির ধারক ও বাহক। চট্টগ্রাম, রাঙামাটি, বান্দরবান ও কক্সবাজার জেলার বেশিরভাগ মানুষ এ ভাষায় কথা বলে। ছিলটি ভাষায় কথা বলা মানুষের সংখ্যা প্রায় এক কোটি ১৫ লাখ। সিলেট বিভাগের হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ ও সিলেট জেলায় ছিলটির আধিক্য। প্রায় এক কোটি আট লাখ মানুষ কথা বলে রংপুরি ভাষায়। রাজশাহী বিভাগের জয়পুরহাট এবং রংপুর বিভাগের দিনাজপুর, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, নীলফামারী, পঞ্চগড়, রংপুর ও ঠাকুরগাঁও জেলায় রংপুরি ভাষার প্রচলন রয়েছে। এ ছাড়া জলপাইগুড়ি (পশ্চিমবঙ্গ), গোয়ালপাড়া (আসাম) ও কোচবিহারে (পশ্চিমবঙ্গ) রংপুরি ভাষা প্রচলিত। চাঁটগাইয়া, ছিলটি বা রংপুরি ভাষা উৎপত্তির ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, এগুলো মূলত ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পরিবারের ইন্দো-আর্য শাখার পূর্বাঞ্চলীয় ইন্দো-আর্যের উপশাখা বাংলা-অসমীয়র সদস্য। শ্রীগৌরচন্দ্র গোপ-এর লেখনীতে আমাদের আঞ্চলিক ভাষার বৈচিত্র্যময়তার নানা দিক খুঁজে পাওয়া যায়। ১৯২৭ সালে ‘ত্রিপুরা জিলার কথ্য-ভাষা’ শিরোনামে লেখা গ্রন্থের অবতরণিকায় গৌরচন্দ্র লিখেছেন, ‘প্রত্যেক ভাষাই দ্বিবিধ লেখ্য এবং কথ্য। লেখ্য ভাষা ব্যাকরণ ঘটিত বিধি বা ভাষাবিষয়ক নিয়ম দ্বারা শাসিতা হইয়া নির্দ্দিষ্ট গণ্ডিতে অবরুদ্ধা, স্বাভাবিকতাবর্জ্জিতা, লাবণ্যবিহীনা। কিন্তু কথ্য ভাষা স্বাধীনা, উন্মুক্তা, স্বাভাবিক ওজস্বিতা গুণসম্পন্না ও লাবণ্যবিমণ্ডিতা। মোটের উপর আগে কথন তথপর লিখন, ইহাই নৈসর্গিক ক্রম বিকাশ বা বিবর্ত্তন। কথিত বিষয়টিই চিরস্থায়ীভাবে সুরক্ষিত করিবার জন্য ব্যাকরণ যন্ত্রের সাহায্যে মার্জ্জিত করিয়া লিখিত বিষয়ে পরিণত করা হইয়াছে। অর্থাৎ পূর্ব্বের কথিত ভাষা ব্যাকরণ সাহায্যে বিশুদ্ধ হইয়া লিখিত ভাষায় পরিণত হইয়াছে। এই লিখিত ভাষা একটু কঠিন আবরণে আবৃত হইয়া সাধারণের দুর্ব্বোধ্য হইলেও সর্ব্বত্র প্রায় একরূপ ধারণ করিয়াছে। কিন্তু কথ্য ভাষা কাল, পাত্র, আবহাওয়া, পারিপার্শ্বিক প্রভাব ও শিক্ষার প্রসার ভেদে বিচিত্র, বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া পার্থক্যের মাত্রা পরিবর্দ্ধিত করিয়াছে। অন্যান্য কথ্য ভাষায় স্থান, কাল, পাত্র ভেদে যত পার্থক্য, বঙ্গভাষায় ঐরূপ পার্থক্যের মাত্রা আরও অধিক। এমনকি বাঙ্গলা কথ্য ও লেখ্য ভাষাকে অনেক স্থলে এক ভাষা বলিয়া স্বীকার করিতে প্রবৃত্তি হয় না। যেমন চাটগেঁয়ে, শ্রীহট্ট, কি নোয়াখালীর কথ্য বাঙ্গলা। কোন বিদেশীয় ভ্রমণকারী যদি উক্ত বিভিন্ন জেলার বিভিন্নরূপ কথ্য ভাষা শ্রবণ করেন, তবে তিনি কিছুতেই তাহাদিগকে একই বঙ্গভাষাভাষী বলিয়া স্বীকার করিবেন না।’
১৯০৩ থেকে ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত পাক-ভারত উপমহাদেশের ভাষা সম্পর্কিত বিবরণী প্রকাশিত হয়। এগুলো স্থান পায় ‘The Linguistic Survey of India’ নামক গ্রন্থে। Sir G A Grierson-এর সম্পাদনায় প্রকাশিত এই ভাষাবিবরণী এতদঞ্চলের উপভাষাগুলো সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান আহরণের অন্যতম অবলম্বন। ‘Linguistic Survey of India Vol.V, Indo-Aryan Family, Eastern Group Part-I Specimens of the Bengali and Assamese Languages’ গ্রন্থে পূর্ববঙ্গ ও আসাম অঞ্চলের বিভিন্ন উপভাষা সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য জানা যায়। গ্রিয়ার্সন বাংলা ভাষার উপভাষাগুলোকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যভেদে প্রধান দুই ভাগে বিভক্ত করেন। প্রাচ্য বিভাগের শাখার মাঝে রয়েছে পূর্বদেশি ও দক্ষিণ-পূর্ব। পূর্বদেশির একটি অংশ হলো সিলেট ও কাছাড় (আসাম)। অন্যদিকে দক্ষিণ-পূর্ব অংশের অন্তর্ভুক্ত হলো চট্টগ্রাম ও আকিয়াব জেলার উত্তরাংশ (মিয়ানমার)। মিয়ানমারের সঙ্গে চট্টগ্রামবাসীর সম্পর্ক অতি সুপ্রাচীন। প্রায় হাজার বছরকাল আরাকান রাজ্যভুক্ত ছিল। বার্মা ও আরাকানের সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগাযোগের ফলে চট্টগ্রামের উপভাষায় ওখানকার বহু শব্দ স্থান পেয়েছে। চর্যাপদের আদি জন্মভূমি চট্টগ্রাম এবং চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায়ই চর্যাপদ রচিত। সে দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা বলতে পারি, চট্টগ্রামের আদি আঞ্চলিক ভাষাই বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন।
ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা এবং তিব্বতী-বর্মী ভাষার সংগমস্থলে অবস্থিত এ উপভাষা অঞ্চলে অতি প্রাচীনকাল থেকে বর্ণসংকরতা ঘটেছে। এখানে পর্তুগিজ, বর্মি, আরবীয়, আর্মেনীয়, গোয়ানিজ, ইংরেজ, ইরানি, তুর্কি এবং আরও বহু অজানা জাতির মিশ্রণ ঘটেছে বলে অনুমান করা হয়। যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে এখানকার সামাজিক স্থিতি বারবার বিপর্যস্ত হয়েছে। বিভিন্ন ভাষা গোষ্ঠীর লোক এ অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করেছে। ফলে এ অঞ্চলের ভাষায় বহু ভাষার ধ্বনি, শব্দ, স্বরভঙ্গি ও অন্যান্য উপাদানের ছাপ পড়েছে। ১৮৬৯ সালে প্রকাশিত রেভারেন্ড জ্যামস লঙ-এর লেখা ‘ইউরোপ ও এস্য খণ্ডস্থ প্রবাদমালা’র দ্বিতীয় ভাগে জার্মানীয়, ইতালীয়, স্প্যানীয়, পর্তুগিজ, ওলন্দাজি ও দিনামারসহ আরো নানাবিধ প্রবাদের সঙ্গে আমাদের বিভিন্ন আঞ্চলিক প্রবাদের মিল লক্ষণীয়। যেমন-আশায় যে ভর করে, অনাহারে সেই মরে (জার্মানীয়), অন্ধকে পথ দেখান সহজ নয় (ইতালীয়), অনলে দগ্ধ বিড়ালের শীতল বারিতে ভয়, ঘর পোড়া গরু সিঁন্দুরে মেঘ দেখে ডরায় (স্প্যানীয়), তার মাথা আছে বটে, কিন্তু আলপিনেরও মাথা আছে (পর্তুগিজ), অল্পকালে পাকে যেই, ত্বরায় পচে সে। অল্পকালে জ্ঞানী হৈলে, শীঘ্র যায় টেসে (ওলন্দাজী), অধিক উচ্চে উঠিতে চেষ্টাই অধঃপাতে যাইবার পথ (দিনামার)।
অঞ্চলভেদে আবার চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষার মাঝে তারতম্য রয়েছে। (ক) উত্তর চট্টগ্রাম (খ) মধ্যম ও শহর চট্টগ্রাম (গ) দক্ষিণ চট্টগ্রাম এবং (ঘ) সন্দ্বীপ, মিরসরাই ও সীতাকুণ্ড অঞ্চলের ভাষায় সুস্পষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন : ভোরে উঠতে হবে, এটাকে চট্টগ্রামের দুই অঞ্চলে দুইভাবে বলে। এক স্থানে বলে, ফজরত্ উডন পড়িব। আরেক স্থানে বলে, বিয়াইন্নে উডন পড়িব। চট্টগ্রামের ভাষায় এমন কিছু এক্সপ্রেশন আছে যা অনুবাদ করা প্রায় অসম্ভব। যেমন : অবাইজ্জাখোদা! অবাজিরে! উম্মারেমা! এ রকম আরও শত শত এক্সপ্রেশন। চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্টের আঞ্চলিক ভাষা অপরাপর জেলার অধিবাসীদের কাছে দুর্বোধ্য। ফলে তারা আলোচ্য উপভাষাভাষী জনগণের প্রতি রঙ্গব্যঙ্গের তীর হামেশাই নিক্ষেপ করে। এ নিন্দা সেকালেও ছিল। চৈতন্যভাগবত তার উজ্জ্বল প্রমাণ। সেখানে লেখা-সভার সহিত প্রভু হাস্য কথা রঙ্গে। /কহিলেন যেন মত আছিলেন বঙ্গে।। /বঙ্গ দেশি বাক্য অনুকরণ করিয়া। /বাঙ্গালেরে কদর্থেন হাসিয়া হাসিয়া।। /বিশেষ চালেন প্রভু দেখি শ্রীহট্টিয়া। /কদর্থেন সেই মত বচন বলিয়া।। সংস্কৃত শ্লোকেও তার অনুরণন পাওয়া যায় : আশীর্বাদং ন গৃহ্লীয়াৎ বঙদেশনিবাসিনঃ। /শতায়ুরিতি বক্তব্যে হুতায়ুর্বদতি যতঃ। [অর্থাৎ বঙ্গদেশবাসীর আশীর্বাদ গ্রহণ করিবে না, কারণ বঙ্গবাসী শতায়ু বলিতে গিয়া হুতায়ু বলিয়া ফেলে।]
চাঁটগাঁইয়া, ছিলটি ও রংপুরি-এই তিনটি বিশেষ আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার এবং বিকাশ লক্ষণীয়। ১৬৪৮ খ্রিষ্টাব্দে রচিত আলাওলের ‘পদ্মাবতী’তে খুঁজে পাওয়া যায় চাঁটগাঁইয়া শব্দ: ‘শুক সম্বোধিয়া নৃপ করিল পুছার’ [পুছ (জিজ্ঞাসা করা)]। চট্টগ্রামের প্রবাদ-প্রবচনগুলোও বেশ ব্যতিক্রমধর্মী। ১৯১৯ সালে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত ‘চট্টগ্রামে প্রচলিত বঙ্গভাষা’ শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে সেকালের চমকপ্রদ চাঁটগাঁইয়া প্রবাদের দেখা মিলে। যেমন-অল্প মনুষ্য’ইয়া জঁইদারি পায়। কানর গুরিত্ কলম গুজি ভাঐয়া নাচায়।। (সামান্য লোকে জমিদারি পেলে কানে কলম গুঁজে বালক নাচায়) আদা বেচে গাদা। মিডা বেচে হারামজাদা।। (আদা শুকালে ওজনে কমে, সুতরাং যে আদার ব্যাপার করে সে বুদ্ধিহীন (গাধা)। গুড় বিক্রি না হলে তার সাথে অন্য দ্রব্য মিশিয়ে ওজন বৃদ্ধি করা হয়, সুতরাং গুড়-ব্যবসায়ী অতি দুষ্ট প্রকৃতির লোক-হারামজাদা)। সিলেটের হেঁয়ালী যেমন-ছয়চরণ কৃষ্ণবরণ পেট কাটিলে আটে (পিঁপড়া), উপরে তক্তা তলে তক্তা, মাঝখানে কলকলি দেবতা (জিহ্বা) আমাদের লোকসাহিত্যের অনন্য উপকরণ। বিশ্বদরবারে নন্দিত হয়েছে রংপুরের ভাওয়াইয়া ও পল্লীগীতি। রংপুরের সেইসব পালাগান (চাঁদমণি-নামে রে কইন্যা/খোরাশান শহরে,/ওরে বাপের নামটি আর বাহাদুর/ বড়ো ত্যাজে ধরে-ও) তো হারাতেই বসেছে।
আঞ্চলিক ভাষার বৈচিত্র্যময়তা আমাদের অহংকার, আমাদের ঐশ্বর্য। না বুঝতে পারার জন্য, হৃদয়ঙ্গম করতে না পারার জন্য, আঞ্চলিক শব্দগুলোকে আমাদের কখনো সখনো বিদ্রুপাত্মক বা হাস্যকর মনে হয়। তবে ভাষার প্রতি ভালোবাসা জন্মালে সেটা আর ব্যাঙ্গাত্মক মনে হয় না। মুচকি হাসিটা আর আসে না। বরং একটা স্নিগ্ধতায় মন ভরে যায়। আঞ্চলিক ভাষাভাষী সেই মানুষগুলোকে তখন অনেক বেশি আপন মনে হয়। আঞ্চলিক ভাষার লেখ্য রূপ অতটা দৃষ্টিগোচর হয় না, যতটা এ উপভাষাগুলো দাবি রাখে। ঐতিহ্য সংরক্ষণের জন্য হলেও এ উপভাষাগুলো সংরক্ষণ জরুরি। আঞ্চলিক ভাষারূপ সংরক্ষণের ব্যাপক নিয়মরীতি গড়ে তোলা সম্ভব হলে সাহিত্যিক সমাজের ব্যবহারের ফলে তখন এগুলোর সর্বাঞ্চলবোধ্য একটি লেখ্য রূপ গড়ে উঠবে বলে আশা করা যায়।
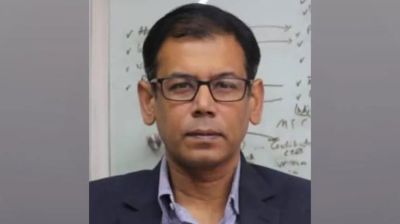

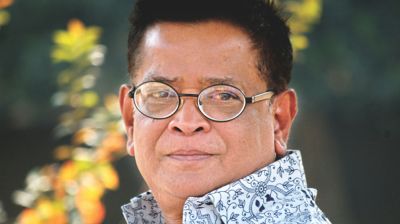










-67ee58a317f05.jpg)


