ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিদেশনীতি : বাংলাদেশ, চীন ও ভারত
ড. ইমতিয়াজ আহমেদ
প্রকাশ: ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, ০৩:৩৬ পিএম
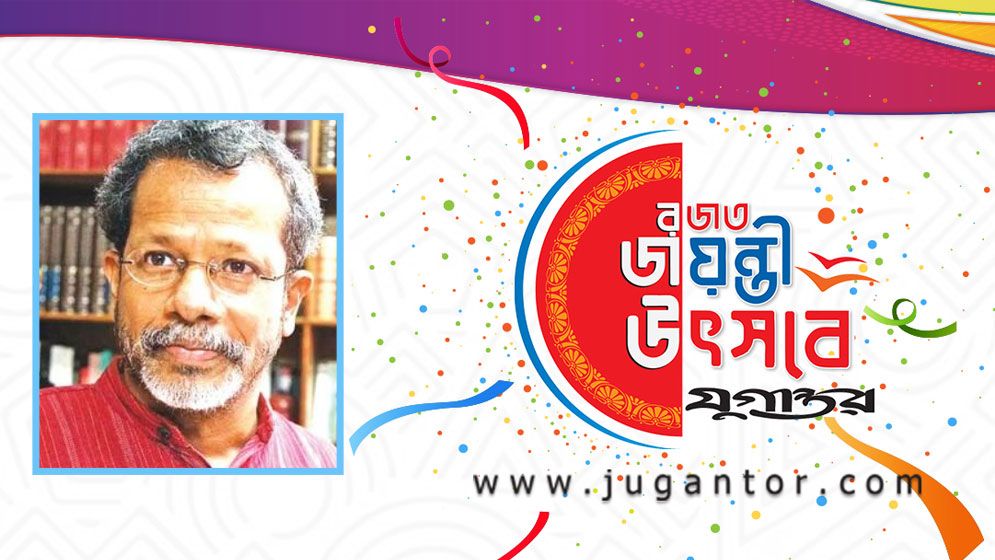
ছবি: যুগান্তর
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসাবে ডোনাল্ড ট্রাম্প তার দ্বিতীয় মেয়াদ শুরু করেছেন। গত নির্বাচনে তিনি বিশাল জয় পেয়েছেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। যুক্তরাষ্ট্রর ইতিহাসে বিগত ১২৮ বছরে এত বড় বিজয় আর কেউ অর্জন করতে পারেননি। ইলেক্টোরাল ভোট, পপুলার ভোট-সব ক্ষেত্রেই ট্রাম্প ও তার দল রিপাবলিকান পার্টি বিজয় অর্জন করেছে। দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রথম দুই বছর ট্রাম্প বিভিন্ন নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অত্যন্ত আক্রমণাত্মক থাকবেন, এটি মোটামুটি নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। তিনি তার নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি-‘মেইক অ্যামেরিকা গ্রেট অ্যাগেইন’ বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকবেন। এ নীতি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে ট্রাম্প চীনের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপের চিন্তাভাবনা করতে পারেন।
চার বছর আগে ট্রাম্পের আগের মেয়াদকালে চীনের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা শুরু হয়েছিল। সেই সময় চীন এমন অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার জন্য প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু ডেমোক্রেটদের শাসনামলেও কিছুদিন এ অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা ছিল, তাই চীন এ ব্যাপারে মোটামুটি প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল। দুই বছর আগেই মোটামুটি বোঝা গিয়েছিল, পরবর্তী মার্কিন নির্বাচনে রিপাবলিকানরা আবারও ক্ষমতায় আসতে পারে। তাই চীন সম্ভাব্য নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে প্রস্তুতি নিয়েছিল। যেহেতু চীন মার্কিন নিষেধাজ্ঞার জন্য আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল, তাই মনে হয় না তারা এ নিষেধাজ্ঞার কারণে খুব একটা অসুবিধায় পড়বে। চীন অন্য যে কোনো সময়ের চেয়ে বর্তমানে বেশি শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে। বিশ্ব বাণিজ্যে চীনের অবস্থান এখনই খুবই শক্তিশালী। তাই যুক্তরাষ্ট্র চীনের বিরুদ্ধে আগের মতো অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবে কিনা, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। টিকটকের ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে তড়িঘড়ি না করার জন্য ট্রাম্প নির্দেশনা দিয়েছেন। অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা দিয়ে চীনকে কোণঠাসা করা যাবে-সেই অবস্থায় চীন এখন আর নেই। চীনের অভ্যন্তরীণ বাজারের বিষয়টিও বিবেচনায় রাখতে হবে। ১২৩ কোটি মানুষের দেশ চীনের অভ্যন্তরীণ বাজার যেমন দিন দিন বড় হচ্ছে, তেমনি চীনা জনগোষ্ঠীর ক্রয়ক্ষমতাও বাড়ছে। বলতে গেলে চীনা জনগণের সবাই শিক্ষিত। তারা আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞানে সমৃদ্ধ। চীনা কোম্পানিগুলো অভ্যন্তরীণ বাজারের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পণ্য চাহিদা পূরণ করছে। চীনা পণ্যের একটি বিশেষত্ব হচ্ছে, তুলনামূলক কম মূল্যে তারা যে কোনো পণ্যের জোগান দিতে সক্ষম।
যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে সৃষ্ট বিরোধের অন্যতম কারণ হচ্ছে বাণিজ্য অসমতা। যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে চীনা পণ্যের প্রচণ্ড দাপট পরিলক্ষিত হয়। অনেকদিন ধরেই যুক্তরাষ্ট্র চীনের বিরুদ্ধে অনৈতিক বাণিজ্যচর্চার অভিযোগ করে আসছে। যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগ-চীন ইচ্ছা করেই স্থানীয় মুদ্রা ইউয়ানের বিনিময় হার অবমূল্যায়ন করে রেখেছে। স্থানীয় মুদ্রা অবমূল্যায়ন করে রাখার ফলে চীনা উৎপাদক ও পণ্য রপ্তানিকারকরা প্রণোদিত হচ্ছে। তারা বেশি পরিমাণ পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানি করছে। এতে মার্কিন উৎপাদকরা প্রতিযোগিতায় ক্রমেই পিছিয়ে পড়ছে। যদিও চীন যুক্তরাষ্ট্রের এ অভিযোগ অস্বীকার করে আসছে।
চীন বর্তমানে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। একটি দেশের মোট জনসংখ্যার ৫০ শতাংশের বেশির বয়স যদি ১৫ থেকে ৬৫ বছরের মধ্যে হয়, অর্থাৎ কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা বেশি হয়, সেই অবস্থাকে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড বলে। ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড অবস্থায় একটি দেশের উন্নয়ন সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি থাকে। কয়েক বছর আগে চীন জাপানের ৪৪ বছরের আধিপত্যকে খর্ব করে বিশ্ব অর্থনীতিতে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনেকটাই এগিয়ে গেছে চীন। তাদের রয়েছে উচ্চশিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত জনগোষ্ঠী। চীনা জনগণের ক্রয়ক্ষমতা আগের তুলনায় অনেকটাই বেড়েছে। ফলে চীনের অভ্যন্তরে বড় ও শক্তিশালী বাজার গড়ে উঠেছে। জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে বাইরের দেশগুলোর ওপর চীনকে খুব একটা নির্ভর করতে হয় না। তবে লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে, চীনের নিজস্ব বাজার বিকশিত হওয়ার পাশাপাশি আন্তর্জাতিকভাবেও তার পণ্য রপ্তানির পরিমাণ দিন দিন বাড়ছে। পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে চীনের একটি বড় সাফল্য হচ্ছে, তারা তুলনামূলক সস্তা দামে গুণগত মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদন ও জোগান দিতে সক্ষম।
যে কোনো দেশের ভোক্তাদের একটি সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে, তারা তুলনামূলক সস্তায় উন্নত মানের পণ্য কিনতে চায়। এ মুহূর্তে চীনের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা দিয়ে খুব একটা লাভবান হওয়া যাবে বলে মনে হয় না। এটি যুক্তরাষ্ট্র নিশ্চয়ই অনুধাবন করতে পারবে। তাই যুক্তরাষ্ট্র চীনের বিরুদ্ধে আগ্রাসী ভূমিকায় অবতীর্ণ না-ও হতে পারে। আগে চীনের পণ্য রপ্তানি অনেকটাই যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু বিগত চার বছরে চীন তার রপ্তানি গন্তব্য ভিন্নমুখী করতে সক্ষম হয়েছে। এখন চীনের রপ্তানি শুধু যুক্তরাষ্ট্রনির্ভর নয়। বিশ্বে এমন দেশ খুব কমই পাওয়া যাবে, যেখানে চীনের পণ্য রপ্তানি হচ্ছে না। ইউরোপীয় ইউনিয়ন, আফ্রিকা, এশিয়ার বিভিন্ন দেশ, রাশিয়া ইত্যাদি গন্তব্যেও চীনা পণ্য স্থান করে নিয়েছে। কাজেই চার বছর আগের চীন আর এখনকার চীন এক নয়। যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে চীনা পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে যে নির্ভরশীলতা তৈরি হয়েছিল, তা আর এখন নেই।
ট্রাম্পের পররাষ্ট্রনীতি কী হবে, তা নিয়ে নানামুখী আলোচনা হচ্ছে। নির্বাচনের আগে বলেছিলেন, তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে ইউক্রেন যুদ্ধ থামানোর এবং রাশিয়ার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কোন্নয়নের চেষ্টা করবেন। তিনি তার এ অঙ্গীকার কতটা রক্ষা করতে পারবেন, তা নিয়ে এখনই সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলা মুশকিল। কারণ, বিষয়টি বেশ জটিল। রাশিয়া অনেকটা তড়িঘড়ি করে সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট আসাদকে কেন বর্জন করল, এটি কোনো বিশেষ পরিকল্পনার অংশ কিনা, তা নিয়ে ভাবতে হবে। যুক্তরাষ্ট্র ইসরাইলের ওপর বড় আকারের চাপ দিতে পারবে কিনা, তা সময়ই বলতে পারবে।
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কখন কী করেন, তা আগে থেকেই নিশ্চিতভাবে অনুমান করা যায় না। ট্রাম্পের চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তিনি যুদ্ধের প্রতি খুব একটা আগ্রহী নন। তিনি প্রথমবার যখন ক্ষমতায় ছিলেন, তখনো নতুন করে কোনো যুদ্ধ শুরু করেননি। কাজেই মনে হচ্ছে, এবারও তিনি যুদ্ধের প্রতি তেমন একটা আগ্রহী হবেন না। বরং তার উদ্দেশ্য থাকবে যুক্তরাষ্ট্রকে অর্থনৈতিকভাবে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অবকাঠামো বেশ পুরোনো হয়ে গেছে। অবকাঠামোগত উন্নয়নের দিক থেকে বিশ্বের অনেক দেশই এগিয়ে গেছে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র এক্ষেত্রে অনেকটাই পিছিয়ে আছে। ট্রাম্প সেই পুরোনো অবকাঠামোগুলো উন্নয়নের জন্যই বেশি মনোযোগ দেবেন বলে আশা করা হচ্ছে। কারণ, অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা না গেলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন টেকসই এবং দ্রুততর করা সম্ভব হবে না। যুক্তরাষ্ট্রে স্বাস্থ্য খাতের অবস্থাও খুবই খারাপ। এগুলো উন্নয়নের জন্য ট্রাম্পকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। তিনি আমেরিকার ভেতরে বড় আকারের বিনিয়োগ করতে চাচ্ছেন। যুক্তরাষ্ট্র যদি তার অভ্যন্তরে নানা উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পাদন করতে চায়, তাহলে তাকে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতে হবে। যুদ্ধ এবং অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন একসঙ্গে চলতে পারে না। তাই ট্রাম্প তার এ মেয়াদে অভ্যন্তরীণ উন্নয়নের প্রতিই বেশি জোর দেবেন বলে মনে হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে অস্ত্র রপ্তানির একটি বড় ধরনের অবদান রয়েছে। ট্রাম্প সেখানে বড় ধরনের পরিবর্তন আনতে চাচ্ছেন।
আমাদের আগ্রহের বিষয় হলো, ভারত ও বাংলাদেশের প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা কী হতে পারে। বিশেষ করে বাংলাদেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা কেমন হতে পারে। ট্রাম্প বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কেমন মনোভাব পোষণ করছেন, তা তার একটি টুইট থেকে কিছুটা অনুমান করা যায়। তিনি বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে লিখেছেন, বাংলাদেশ যেন বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে দেখে। অবশ্য বাংলাদেশে সংখ্যালঘু প্রশ্নে ট্রাম্পের উদ্বেগ নতুন নয়। আগেরবার যখন তিনি প্রেসিডেন্ট ছিলেন, তখন বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ছিল, সেই সময় প্রিয়া সাহা নামে এক বাংলাদেশি নারী ট্রাম্পের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ইস্যুটি উত্থাপন করেছিলেন।
ট্রাম্প বিভিন্ন সময় জানিয়েছেন, তিনি ভারতের সঙ্গে বড় ধরনের সম্পর্কোন্নয়ন চান। কৌশলগত কারণেই যুক্তরাষ্ট্র ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সুসম্পর্ক বজায় রাখতে চাইবে। কারণ এ অঞ্চলে চীন ও পাকিস্তানের প্রভাব মোকাবিলায় ভারতের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সুসম্পর্ক রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি। তাই যুক্তরাষ্ট্র যেভাবেই হোক, ভারতের সঙ্গে উন্নত দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বজায় রাখতে চাইবে। বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারতের নেতিবাচক মনোভাব লক্ষণীয়। ভারত বাংলাদেশের বিতাড়িত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আশ্রয় দিয়েছে। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবেই এর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। ভারত যদি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও উন্নত ও গভীর করতে পারে, তাহলে বাংলাদেশের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রহ কমে যেতে পারে। আগের সরকারের আমলে বাংলাদেশ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের যে আগ্রহ ছিল, তাতে ভাটা পড়তে পারে। আগের মার্কিন সরকার বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রতি যেভাবে সমর্থন দিয়েছিল, আগামীতে তা না-ও থাকতে পারে। এমনকি যুক্তরাষ্ট্র হয়তো বাংলাদেশ প্রসঙ্গে ভারতের ওপর আরও বেশিমাত্রায় নির্ভরশীল হয়ে পড়তে পারে। সত্যি সত্যি যদি তেমন কিছু হয়, তাহলে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ কেমন হবে, তা এ মুহূর্তে নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না।
লেখক : শিক্ষাবিদ ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষক

