ভারতের দাদাগিরি দক্ষিণ এশিয়ার মূল সমস্যা
আকমল হোসেন
প্রকাশ: ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, ১২:০০ এএম
প্রিন্ট সংস্করণ
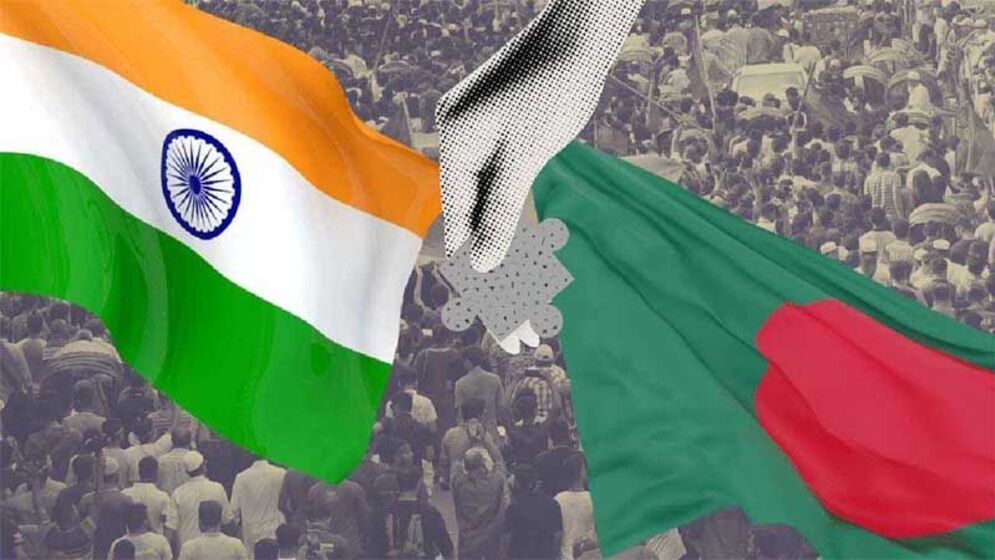
ভারত ১৯৪৭ সাল থেকে পররাষ্ট্রনীতিতে তার সীমান্ত সন্নিহিত অঞ্চলকে গুরুত্ব দিয়ে পদক্ষেপ নিয়েছে। এর পেছনে প্রধান কারণ ছিল তার নিরাপত্তা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা। প্রতিবেশী পাকিস্তানের সঙ্গে শুরুতেই দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্ক তৈরি হওয়ার প্রেক্ষাপটে নীতিনির্ধারকদের কাছে অন্য প্রতিবেশীরা গুরুত্ব পেয়েছে। ভুটানের সঙ্গে ১৯৪৯ সালে চিরস্থায়ী শান্তি ও মৈত্রী চুক্তি এবং ১৯৫০ সালে নেপালের সঙ্গে শান্তি ও মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে ভারতের নিরাপত্তা স্বার্থ সুরক্ষা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। উল্লেখ করা দরকার, হিমালয় অঞ্চলের প্রতিবেশী গণচীনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক তখনো বৈরিতার দিকে মোড় না নেওয়া সত্ত্বেও ভুটান ও নেপালে যাতে চীন কোনো কৌশলগত সুবিধা না নিতে পেরে, তার দিকে ভারতীয় নীতিনির্ধারকদের দৃষ্টি ছিল। কৌশলগত এ পদক্ষেপ সত্ত্বেও ১৯৬২ সালে চীনের সঙ্গে সীমান্তযুদ্ধ ভারতের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তা আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ ভারতকে বিরাট কৌশলগত সুবিধা এনে দিয়েছিল। চিরবৈরী পাকিস্তান ভেঙে গেলে দক্ষিণ এশিয়ায় ক্ষমতার ভারসাম্যে যে পরিবর্তন আসে, তা ভারতকে আঞ্চলিক শক্তি হওয়ার পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। ভারত তার নিরাপত্তা সুরক্ষিত করার জন্য ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সঙ্গে ২৫ বছর মেয়াদি শান্তি, মৈত্রী ও সহযোগিতা চুক্তি (মৈত্রী চুক্তি নামে পরিচিত) স্বাক্ষর করে। দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে তার কর্তৃত্ব নিশ্চিত করার ইচ্ছা থেকে ইন্দিরা গান্ধী ১৯৮৩ সালে এক ডকট্রিন ঘোষণা করেছিলেন, যাতে অঞ্চলবহির্ভূত কোনো শক্তির হস্তক্ষেপকে যেমন বিরোধিতা করা হয়েছিল, তেমনি কোনো সংকটে ভারতের ওপরই নির্ভর করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছিল। শান্তি ও নিরাপত্তা নিয়ে এসব চুক্তির পরও ভারতের সঙ্গে প্রতিবেশীদের সম্পর্ক নানা ইস্যুতে প্রায় সময় প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। ভারতের আকার-আয়তন, সামরিক শক্তি ও বাণিজ্যিক স্বার্থ ক্ষুদ্র প্রতিবেশীদের কাছে দেশটিকে কর্তৃত্ববাদী শক্তি হিসাবে তুলে ধরেছে। ভারতের বর্তমান হিন্দুত্ববাদী সরকার শুরু থেকেই ‘নেইবার ফার্স্ট’ (প্রতিবেশী প্রথম) নামকরণ করে যে গালভরা নীতি ঘোষণা করেছিল, তা কতদূর ফলপ্রসূ হয়েছে, প্রশ্ন করা যেতে পারে।
পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের শুরুর দিনগুলো
স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে অভ্যুদয়ের প্রাক্কালে কংগ্রেস নেতা জওহরলাল নেহেরু বলেছিলেন, নিয়তি ভারতকে বিশ্বের অন্যতম নেতার স্থানে প্রতিষ্ঠা করেছে। ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের পাশে ভারত চতুর্থ শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠা পাবে। বৈশ্বিক মর্যাদা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে ভারত তার কাছের প্রতিবেশীদের ব্যাপারে বিশেষ নীতি প্রণয়ন করতে সচেষ্ট ছিল। ষাটের দশকে শুরু হওয়া জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের অন্যতম উদ্যোক্তা ভারতকে জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির ঘোষণা দিয়ে এক শান্তিবাদী ভাবমূর্তি গড়ার চেষ্টা করতে দেখে গেছে। একইসঙ্গে দুই পরাশক্তির কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে ক্রমান্বয়ে তার সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করেছে। প্রথমে সৎ প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক গড়ার চেষ্টা করেও সীমান্ত নিয়ে ভারতের সঙ্গে চীনের মতপার্থক্য ১৯৬২ সালে যুদ্ধে গড়িয়েছিল। অন্যদিকে প্রতিবেশী পাকিস্তানের সঙ্গে কাশ্মীর ইস্যুতে দ্বন্দ্ব ভারতীয় নেতাদের আঞ্চলিক ক্ষমতার ভারসাম্যে পরিবর্তন আনার চিন্তায় ব্যস্ত রেখেছে। ১৯৭৪ সালে শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে পরমাণু পরীক্ষা আদতে ১৯৯৮ সালে তাকে পরমাণু অস্ত্রের মালিক হতে সাহায্য করেছিল।
এদিকে ১৯৭৫ সালে আধা স্বাধীন রাজ্য সিকিমকে কূটকৌশলে ভারতের অঙ্গীভূত করে তার নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা হয়। বাংলাদেশের সঙ্গে স্বাক্ষরিত ১৯৭২ সালের মৈত্রী চুক্তির পেছনে শিলিগুড়িসংলগ্ন চিকেন নেকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার অভিলাষ কাজ করেছিল। ভবিষ্যতে চীনের সঙ্গে সীমান্ত সংঘাতে ১৯৬২ সালের অবস্থার (চীনারা যখন ‘চিকেন নেক’ অবরোধ করে রেখেছিল) পুনরাবৃত্তি রোধে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল দিয়ে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর চলাচল নিশ্চিত করতে মৈত্রী চুক্তি ব্যবহার করার অবকাশ তৈরি হয়েছিল। ভারতের নেতৃস্থানীয় সামরিক কৌশলবিদ কে সুব্রাহমানিয়াম ১৯৭২ সালে এক লেখায় এ ধরনের সম্ভাবনার পূর্বাভাস দিয়েছিলেন।
দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের অভিলাষ
ভারতের নেতারা আঞ্চলিক নেতৃত্বের বাসনা পূরণ করতে যেভাবেই হোক সামরিক হস্তক্ষেপ, কূটনৈতিক উপায়, রাজনৈতিক চাপ, পছন্দের রাজনৈতিক শক্তিকে রাষ্ট্রক্ষমতায় বসানোর নীতি দ্বারা চালিত হয়েছে। কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় সব প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক একইভাবে পরিচালিত হয়নি। বিভিন্ন সময় সম্পর্কের পারদ উঁচু-নিচু হয়েছে। যদিও সার্ক সংগঠনের সূত্রপাত করা হয়েছিল আঞ্চলিক সহযোগিতা এগিয়ে নিতে; কিন্তু বর্তমানে তা নিষ্ক্রিয় হয়ে আছে ভারত-পাকিস্তানের কাশ্মীর দ্বন্দ্বের কারণে। একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করা দরকার। এ অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলোর ক্ষমতাসীন সরকারগুলোও ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক হ্রাস-বৃদ্ধির জন্য দায়ী। বাংলাদেশ, নেপাল, শ্রীলংকা ও মালদ্বীপে ভারতপন্থি সরকার ক্ষমতা হারালে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে শীতলতা তৈরি হতে দেখা যায়। পনের বছরের বেশি সময় ক্ষমতাসীন ভারতের একান্ত মিত্র শেখ হাসিনার সরকার গণ-অভ্যুত্থানে অপসারিত হওয়ার পর বর্তমান বাংলাদেশের প্রতি ভারত সরকারের নীতি কোনোভাবেই বন্ধুসুলভ নয়। ভারতের সরকার, একশ্রেণির গণমাধ্যম ও জনগণের একটি অংশ বাংলাদেশের সরকার ও জনগণের প্রতি খোলাখুলিভাবে বিদ্বেষ প্রদর্শন করছে। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও নেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা বরাবর প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্ক নির্মাণে ভারতীয় নীতিতে প্রভাব ফেলেছে। জওহরলাল নেহেরুর আমলে পঞ্চশিল তথা পাঁচটি নীতি দিয়ে ভারতের পররাষ্ট্রনীতি পরিচালিত হবে বলা হতো। এর অন্যতম ছিল তৃতীয় বিশ্বের সঙ্গে সংহতি তৈরি করার নীতি। পরবর্তীকালে দেব গৌড় সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আই কে গুজরাল ‘গুজরাল ডকট্রিন’ নামে প্রচারিত পাঁচটি লক্ষ্যসংবলিত পররাষ্ট্রনীতি ঘোষণা করেছিলেন। এতে প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্কের ওপর গুরুত্বারোপ করে বলা হয়েছিল, ভারত তার প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্ক নির্মাণে কোনো পারস্পরিক প্রতিদানের নীতি দ্বারা পরিচালিত হবে না। তবে বাস্তবতার নিরিখে ভারতের পররাষ্ট্রনীতি প্রণেতাদের দেখা গেছে দক্ষিণ এশিয়ায় দিল্লির কর্তৃত্বশীল অবস্থান নিশ্চিত করতে। দ্বিপাক্ষিকতাকেই ভাবা হয় সমস্যা সমাধানের পদ্ধতি। এ অঞ্চলের বাইরের কোনো রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রতিবেশীদের সম্পর্ক তৈরির যে কোনো চেষ্টা ভারত সন্দেহের চোখে দেখে অভ্যস্ত। তাই আঞ্চলিকতাবাদের সম্ভাবনা নিয়ে সার্ক যাত্রা শুরু করলেও তিন দশক পর ভারতের অনাগ্রহে সংগঠনটি বর্তমানে প্রায় নিষ্ক্রিয় হয়ে আছে।
মোদি সরকারের ‘নেইবার ফার্স্ট’ নীতি
দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি ভারতকে তার স্বার্থের ব্যাপারে নতুন করে সচেতন করেছে। বিজেপি ২০১৪ সালে প্রথমবার ক্ষমতায় এসে ‘নেইবার ফার্স্ট’ (প্রতিবেশীরা প্রথম) নীতিকে তাদের পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনার কৌশল বলে ঘোষণা দিয়েছিল। নির্বাচনি প্রচারণার সময় নরেন্দ্র মোদি প্রতিবেশীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ও সমন্বিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের নীতি গ্রহণ তার পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম বিবেচ্য বিষয় হবে বলে প্রচার করেছিলেন। শপথ অনুষ্ঠানে আঞ্চলিক রাষ্ট্রনেতাদের আমন্ত্রণ জানিয়ে চমক সৃষ্টি করা হয়েছিল। মনে হচ্ছিল, পূর্বসূরি কংগ্রেস সরকারের অনুসৃত অ্যাপ্রোচকে বদলে বিজেপি যে অ্যাপ্রোচ নিচ্ছে, তা মৌলিকভাবে ভিন্ন হবে; কিন্তু দেখা গেছে বাস্তবে তা হয়নি। কাশ্মীর ইস্যু নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে পুরোনো বিবাদ থেকে উদ্ভূত সংকটের কারণে সার্ক শীর্ষ সম্মেলনকে স্থগিত করতে ভারত উদ্যোগ নিয়েছিল। তার মিত্র বাংলাদেশসহ অন্য রাষ্ট্রগুলো তাকে অনুসরণ করায় ২০১৬ সালে সার্ক শীর্ষ সম্মেলন স্থগিত হয়ে যায়।
বিজেপির হিন্দু জাতীয়তাবাদের ঢেউয়ে বর্তমানে ভারতীয় সমাজ আচ্ছন্ন হওয়ার উপক্রম হওয়ায় এর নেতিবাচক অভিঘাত দ্বারা আঞ্চলিক নীতি আক্রান্ত হওয়ার উপক্রম হয়েছে। বাংলাদেশের মতো ‘ঘনিষ্ঠ’ বন্ধু ২০১৯ সালে কাশ্মীরের মর্যাদা পরিবর্তনকে ভারতের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলেছে; কিন্তু ভারতের নাগরিকপঞ্জি ও নাগরিকত্ব আইন নিয়ে উদ্বেগের প্রেক্ষাপটে দু’দেশের যৌথ নদী কমিশনের বৈঠক স্থগিত করার ঘটনা ঘটেছে। সর্বোচ্চ পর্যায়ে রাষ্ট্রীয় সফরে তিস্তাচুক্তি নিয়ে ভারতের বারবার দেওয়া প্রতিশ্রুতি অন্তঃসারশূন্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।
যদিও ভারতের ওপর নেপালের ব্যাপক অর্থনৈতিক নির্ভরতা রয়েছে, তা সত্ত্বেও দুই দেশের সম্পর্কে মাঝেমধ্যে সংঘাত তৈরি হয়। ১৯৫০ সালে স্বাক্ষরিত চুক্তির ৫ ধারা অনুযায়ী নেপালের যে কোনো সমরাস্ত্র আনতে ভারতীয় ভূখণ্ড ব্যবহার করার শর্ত রয়েছে। আশির দশকে নেপাল চীন থেকে সমরাস্ত্র আনার চেষ্টা করলে ভারত তার ভূখণ্ড থেকে নেপালে পণ্য পরিবহণের দুটি ছাড়া সব পথ বন্ধ করে দেয়। নেপালে কমিউনিস্টরা ক্ষমতায় থাকাকালীন নেপাল-ভারত সম্পর্কের অসমতার বিষয়টি সামনে চলে আসে। সীমান্তবর্তী মহাকালী নদী নিয়ে দু’দেশের এক পুরোনো বিরোধ ছিল, যা নিরসনে দুই দেশ ১৯৯৬ সালে এক চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।
নেপালের অভ্যন্তরীণ বিষয়েও ভারতের হস্তক্ষেপের উদাহরণ আছে। নতুন সংবিধান প্রণয়ন করার সময় ২০১৫ সালে নেপালি মহাদেশি জনগোষ্ঠীর দাবির সমর্থনে পাঁচ মাস ধরে ভারত তারাই অঞ্চলে অবরোধ করে রেখেছিল। অবরোধের কারণে নেপালে ভারত থেকে রপ্তানি হওয়া ভোগ্যপণ্যের সংকট দেখা দেয়; কিন্তু কয়েক বছর আগে লিম্পিয়াধুরা, লিপুলেখ ও কালাপানি নামের অভিন্ন সীমান্তের তিনটি অঞ্চল নিয়ে যে বিরোধ তৈরি হয়েছিল, তার ব্যাপ্তি আগের সব বিরোধকে ছাড়িয়ে গেছে। ভারত এ অঞ্চলে সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার জন্য সড়ক তৈরি করলে নেপাল সরকার তীব্র্র আপত্তি জানায়। এসব ভূখণ্ড নিজেদের দাবি করে নেপাল এক নতুন মানচিত্র প্রকাশ করে এবং আইনসভায় তা পাশ করিয়ে নেয়, যাতে এ তিনটি স্থান নিজস্ব ভূখণ্ড বলে দেখানো হয়েছে।
তামিল বিচ্ছিন্নতাবাদকে কেন্দ্র করে শ্রীলংকার গৃহযুদ্ধে ভারতের হস্তক্ষেপ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে জটিল করে তুলেছিল। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেশটির সঙ্গে চীনের ঘনিষ্ঠতা ভারতের অপছন্দ। শ্রীলংকার বন্দরে চীনা জাহাজের আগমনে ভারত আপত্তি জানিয়েছে। এদিকে মালদ্বীপ ও ভারতের মধ্যে সম্পর্কে দেশটির বর্তমান প্রেসিডেন্ট মুইজ্জুর সময় উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। চীনপন্থি বলে পরিচিত মুইজ্জু ‘ইন্ডিয়া আউট’ বলে নির্বাচনি প্রচার চালান এবং নির্বাচিত হয়ে তার দেশ থেকে ভারতের সৈন্যদের সরিয়ে নেওয়ার আহ্বান জানান।
প্রতিবেশীদের মধ্যে বাংলাদেশ পনের বছরের বেশি সময় ধরে ভারতের বিশ্বস্ত মিত্র বলে পরিচিত ছিল। এ সময় বাংলাদেশ ভারতের নিরাপত্তা, ট্রানজিট, বন্দর সুবিধা, রেল সংযোগ স্থাপনের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ পূরণে পদক্ষেপ নিয়েছে, যদিও তিস্তা নদীর পানির ভাগাভাগি, সীমান্ত হত্যা বন্ধ, রপ্তানিতে অশুল্ক বাধা অপসারণ করার কোনো সুবিধা পায়নি। কিন্তু গণ-অভ্যুত্থানে একনায়ক ফ্যাসিবাদী শাসক শেখ হাসিনা অপসারিত হয়ে ভারতে আশ্রয় নিলে বাংলাদেশের প্রতি ভারতীয় বিদ্বেষ খোলাখুলি হয়ে পড়ে। সর্বদলীয় সভায় বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিবর্তন নিয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। বাংলাদেশের বিষয়ে ভারতীয় গণমাধ্যম ও জনগণের বড় অংশ মিথ্যাচার ও শত্রুতামূলক আচরণ করছে। হিন্দু জনগোষ্ঠীর ওপর নির্যাতনের অতিরঞ্জিত বয়ান, মৌলবাদ এবং পাকিস্তানি বাণিজ্যিক জাহাজের আগমন নিয়ে মিথ্যাচার করা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়েনের আবদারও করা হয়েছে। বাংলাদেশের জন্য ভিসা সুবিধাদান একদম সীমিত করে দেওয়া, কূটনৈতিক নীতি লঙ্ঘন করে শাসক বিজেপির নেতাকর্মীদের বাংলাদেশের দূতাবাসের অঙ্গনে প্রবেশ এবং বাংলাদেশের জাতীয় পতাকায় আগুন দেওয়ার মতো ঘটনা ঘটেছে। বাংলাদেশবিরোধিতা এখন ভারতের রাজনীতিতে বড় এক উপাদানে পরিণত হয়েছে।
‘প্রতিবেশী প্রথম’ নীতির ব্যর্থতা
বিজেপি সরকারের ‘নেইবার ফার্স্ট’ নীতি তাহলে কী ফল দিয়েছে? আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ভারত তার ভূমিকা বাড়াতে যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোর সঙ্গে সামরিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক এগিয়ে নিচ্ছে; কিন্তু তার প্রতিবেশীদের সঙ্গে বর্তমানে যে সম্পর্ক, তা কোনো আদর্শ সম্পর্ক বলা যাবে না। ভারতের মতো এক উদীয়মান বৈশ্বিক শক্তি তার অঞ্চলকে ঠিক রাখতে না পারলে তার পক্ষে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রভাবশালী হওয়া সম্ভব হবে না। তাছাড়া বলা বাহুল্য, তার নিরাপত্তার জন্য আঞ্চলিক সম্পর্ককে ঠিক করতে হবে। নীতিনির্ধারকদের অধিপতিসুলভ ব্যবহার ত্যাগ করতে হবে।
সাম্প্রতিককালে চীনের সঙ্গে সীমান্ত বিরোধের কারণে ভারতকে যথেষ্ট সামরিক ও রাজনৈতিক হেনস্তার শিকার হতে হয়েছে। বিরোধের সময় তাকে তার প্রতিবেশীদের কোনো প্রকাশ্য সমর্থন দিতে দেখা যায়নি। অপরপক্ষে চীনকে দেখা গেছে বাংলাদেশকে বাণিজ্যক্ষেত্রে এক বড় সুবিধা দেওয়ার ঘোষণা দিতে। এরপরই ভারতের গণমাধ্যম বিষয়টিকে অত্যন্ত নেতিবাচকভাবে তুলে ধরে সংবাদ পরিবেশন করেছে। চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক ও সামরিক সম্পর্ক ভারতের জন্য কাঙ্ক্ষিত নয়। ভারতের অপছন্দের চীনের রোড অ্যান্ড বেল্ট পদক্ষেপকে বাংলাদেশ আগেই গ্রহণ করেছে, যা ভারত প্রত্যাখ্যান করে থাকে।
ড. আকমল হোসেন : অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়



