কর্তৃত্ববাদের ঝোঁকটাই ফেলেছে বিপদে
হাসান মামুন
প্রকাশ: ২৮ অক্টোবর ২০২৩, ১২:০০ এএম
প্রিন্ট সংস্করণ
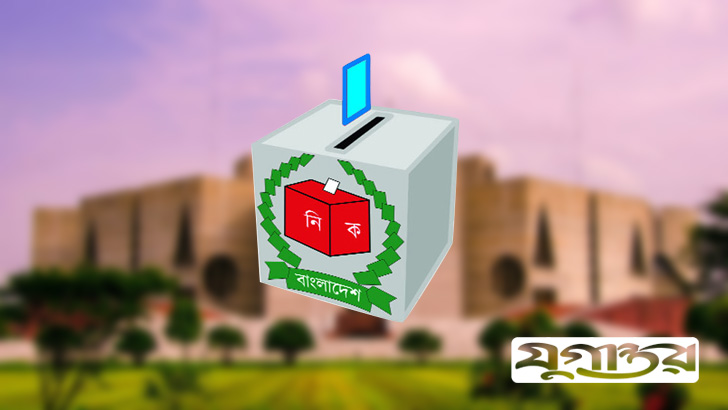
নব্বইয়ের পর দেশ একটা গণতান্ত্রিক উত্তরণের দিকে গেলেও সেটা নির্বাচিত সরকারপ্রাপ্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। আর নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদ গঠিত হলেও তা কার্যকর হয়নি। সেটা শুধু বিরোধী দলের অসহযোগিতায় নয়; সরকারের গা-জোয়ারি আচরণের কারণেও। যত ভোট আর আসন পেয়েই সরকার গঠিত হোক, তারা অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে বিরোধী দলের প্রতি। জনগণের অধিকারেরও তোয়াক্কা করেনি। সুশাসনে নজর হ্রাস পেয়েছে ক্রমে। প্রতিটি নির্বাচনে বিরোধী দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হলেও তারা কেউ এমনকি সাম্প্রতিক অতীত থেকে শিক্ষা নেয়নি। দুর্নীতি-সন্ত্রাস বেড়ে যেতেই দেখেছি। কালাকানুন রদের বদলে নতুন করে তা প্রণয়নের প্রয়াসও দেখা গেল। প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার বদলে তা বিনষ্ট করার প্রবণতা বেড়ে উঠেছে ক্রমে। প্রশাসনসহ সবখানে দলীয় প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা তীব্র থেকে তীব্রতর।
এ অবস্থায় মাঝে ওয়ান-ইলেভেনের সুবাদে সেনাসমর্থিত একটি সরকার রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কারের উদ্যোগ নিলেও তারা ব্যর্থ হয় নানা কারণে। তার চেয়ে বড় কথা, এখান থেকেও কোনো শিক্ষা নেয়নি সেই দলগুলো, যারা হাতবদল করে ক্ষমতাচর্চা করছে। বিশেষত ওয়ান-ইলেভেন ব্যর্থ হওয়ার পর যারা ক্ষমতায় এসেছে, তারা আগের সংস্কার কর্মসূচিগুলো বাতিল করেছে-যেমন হিমঘরে পাঠিয়েছে নিজেদের বিরুদ্ধে হওয়া মামলাগুলো। তারা অতঃপর বিরোধী দলের ক্ষমতায় ফিরে আসার সুযোগ নিঃশেষ করে দিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিলের দিকে চলে গেছে। ব্যবস্থাটি গণতান্ত্রিক শাসনের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয় বটে। সেক্ষেত্রে তাদের দায়িত্ব ছিল গণতান্ত্রিক দেশগুলোয় স্বীকৃত নির্বাচনব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করে দেখানো। গণতান্ত্রিক দেশগুলোয় দলীয় সরকারই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হিসাবে থাকে জাতীয় নির্বাচনের সময়। তাতে নির্বাচনের কাম্য পরিবেশে এমন কিছু ঘটে না, যাতে বিরোধী দল নির্বাচনে আসতে ভয় পায় কিংবা নির্বাচনের পর সেটা নিরপেক্ষ হয়নি বলে অভিযোগ করে। পাকিস্তান বাদে এ অঞ্চলেরও কোনো দেশে কিন্তু নির্বাচনকালীন দলনিরপেক্ষ সরকারব্যবস্থা নেই এবং তেমন দাবি উত্থাপিতও হচ্ছে না। আমরা পাকিস্তান রাষ্ট্রকাঠামোয় থাকার সময়েও ১৯৫৪ ও ১৯৭০ সালে তৎকালীন দলীয় সরকারের অধীনেই নির্বাচন হয়েছিল এবং তাতে কেউ বিরোধী দলের বিজয় ঠেকায়নি। দুর্ভাগ্যবশত সেই ধারা আমরা বজায় রাখতে পারিনি স্বাধীনতা উত্তরকালে। কী গণতান্ত্রিক, কী সামরিক, কী ছদ্ম গণতান্ত্রিক-সব শাসনামলেই দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন কম-বেশি বিতর্কিত হয়েছে। এটা বড় লজ্জার কথা। বিগত দুটি নির্বাচনে তা গভীরতর হয়ে সম্ভবত চূড়ান্ত রূপ নিয়েছে।
বিরোধী দল থেকে যৌক্তিকভাবেই বলা হচ্ছে, ধারাবাহিকভাবে এবং পারলে আজীবন ক্ষমতায় থাকার জন্য তাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ এ ব্যবস্থা করেছে। যারা এমন অভিযোগ করছে, তাদের বিরুদ্ধেও কিন্তু অভিযোগ রয়েছে নির্বাচন ব্যবস্থাকে একাধিকবার বিনষ্ট করার; সেটাকে নিজেদের পক্ষে আনতে নানা অপচেষ্টা চালানোর। যখন তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা সংবিধানের অংশ ছিল না, তখন যেমন, আবার ব্যবস্থাটি সংবিধানের অংশ হওয়ার পরও তারা নানাভাবে সেটাকে ব্যবহারের অপপ্রয়াস চালায়। এতে সফল হতে পারলে তাদের হাতে নির্বাচন ব্যবস্থাটি কী রূপ নিত কিংবা তারাও একপর্যায়ে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা বাতিল করে দিত কিনা, সে প্রশ্ন রয়েছে। উভয়পক্ষই তো দেখেছে, নির্বাচনকালে দলনিরপেক্ষ সরকার থাকলে সদ্যবিদায়ি ক্ষমতাসীনরা কোনোভাবেই ক্ষমতায় ফিরতে পারে না। পরপর চারবার এমনটি ঘটতে দেখে যারা শেষবার ক্ষমতায় এসেছে, তারা সুযোগ পেয়েই এমনকি নিজ দল ও সংসদীয় কমিটির সুপারিশ উপেক্ষা করে অবস্থান নিয়েছে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা বাতিলের পক্ষে।
প্রসঙ্গটি একটু লম্বা করে তুলতে হলো এজন্য যে, সরকারকে জবাবদিহির মুখোমুখি করা অর্থাৎ প্রয়োজনে তাকে আর ক্ষমতায় ফিরতে না দেওয়ার যেটুকু সুযোগ জনতার হাতে ছিল-সেটাও কেড়ে নেওয়ার ব্যবস্থা হয় তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা বাতিলের মাধ্যমে। এর স্বাভাবিক ফলস্বরূপ বিরোধী দলগুলো আবার নির্বাচন বর্জন ও প্রতিহতকরণের ডাক দিয়ে মুখোমুখি হয় সরকারের। তাতে ব্যর্থ হয়ে পরেরবার সরকারের প্রতিশ্রুতি পেয়ে নির্বাচনে অংশ নিয়ে তাদের হতে হয় ‘প্রতারিত’। এর আগে বিরোধী দল ও মতের মানুষদের মতপ্রকাশের অধিকার নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে বানিয়ে নেওয়া হয় আইন। দলীয় সরকারের অধীনে স্থানীয় নির্বাচনও সুষ্ঠুভাবে হতে পারেনি বলে এতেও জনঅংশগ্রহণ কমে আসে সাধারণভাবে। এ অবস্থায় সরকার স্বভাবতই হয়ে ওঠে ‘কর্তৃত্ববাদী’।
কর্তৃত্ববাদী সরকারও কোনো কোনো ক্ষেত্রে এক ধরনের সুশাসন দিয়ে গ্রহণযোগ্যতার সংকট দূর করতে না পারলেও তা ঢাকতে চায়। বর্তমান শাসনামলে সেটিও লক্ষ করা যায়নি। অবকাঠামো নির্মাণ, বিদ্যুৎ-জ্বালানি ও ব্যাংকসহ বিভিন্ন খাতে অভাবনীয় ব্যয়, ক্যাপাসিটি চার্জের নামে মহলবিশেষের হাতে বিপুল অর্থ তুলে দেওয়া, নিয়ন্ত্রিত সুদের হারে ঋণ জুগিয়ে তা আত্মসাৎ ও পাচারের সুযোগ করে দেওয়ার মতো গুরুতর অভিযোগ উঠেছে এর মধ্যে। এমনকি পার্শ্ববর্তী দেশগুলোয় মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সাফল্য অর্জিত হলেও বাংলাদেশে এটি ক্রমবর্ধমান এবং তাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জীবনে উঠে গেছে নাভিশ্বাস। রিজার্ভ বিপজ্জনকভাবে ক্ষয়ে যাওয়ায় আগামীতে জরুরি পণ্যসামগ্রী আমদানি করে অর্থনীতি সচল রাখার ক্ষেত্রেও দেখা দিয়েছে প্রশ্ন। আওয়ামী লীগের বদলে বিএনপি ২০০৮ সালের নির্বাচনে জয়ী হয়ে একইভাবে টানা তিন মেয়াদে সরকার পরিচালনা করলেও পরিস্থিতি হয়তো এর চেয়ে ভিন্ন হতো না। কারণ, উভয় দলে রাজনৈতিক-আদর্শগত তফাত কম এবং দুপক্ষই একইভাবে সরকার পরিচালনায় অভ্যস্ত। তারা বরং প্রতিপক্ষের মন্দ কাজ অনুসরণ করে সেটার পক্ষে যুক্তি জোগাতেও কুণ্ঠিত নয়।
এ অবস্থায় সামনে যে নির্বাচন রয়েছে, তাকে গ্রহণযোগ্য করার তাগিদ পশ্চিমা গণতান্ত্রিক মহলও অব্যাহতভাবে দিয়ে যাচ্ছে। এমন ভূমিকা গ্রহণ করতে আগে তাদের কখনো দেখা যায়নি। ইতঃপূর্বে নির্বাচন ঘিরে একাধিক সময়ে সংকট ঘনীভূত হয়ে উঠলেও প্রধানত বিরোধী পক্ষ তাদের সম্পৃক্ত করেছে। পশ্চিমারা এবার যুক্ত হয়েছে নিজে থেকে। মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে বাংলাদেশ পুলিশের এলিট ফোর্সের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে তারা সম্পৃক্ত হয় বেশ আগে। সেটা ক্রমে হয়েছে গভীর। সুশাসন ও সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবি ঘিরে ঘটলেও এ সম্পৃক্ততার নেপথ্যে রয়েছে পশ্চিমা বিশ্বের নেতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থ। বাংলাদেশের অর্থনীতি ও রাজনীতিতে উদীয়মান পরাশক্তি চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব তাদের উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে। তারা এখন এমন একটি সরকার এখানে দেখতে চায়, যারা চীনের বদলে পশ্চিমা গণতান্ত্রিক মহলের সঙ্গে বেশি সম্পৃক্ত হয়ে কাজ করবে। এ অবস্থায় বাংলাদেশের আগামী নির্বাচন সুষ্ঠু করতে সহায়তার লক্ষ্যে তারা ইতোমধ্যেই নিয়েছে কিছু পদক্ষেপ। আরও পদক্ষেপ নির্বাচনের আগে না হলেও নির্বাচনের পর আসবে বলেই অনেকের ধারণা।
এদিকে পরিস্থিতি এমন যে, বিরোধী দল ও পশ্চিমাদের পছন্দমতো নির্বাচনে যেতে পারছে না সরকার। সবচেয়ে বড় কথা, পরিপূর্ণ দলীয় প্রভাবে থাকা প্রশাসন ও রাজনৈতিক আনুকূল্য লাভকারী ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ভিন্ন একটি সরকারের ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনা মেনে নিতে একেবারে অপ্রস্তুত। এটা ব্যক্তিবিশেষের সদিচ্ছার ওপর আর নির্ভরশীল নেই। ইতঃপূর্বে ১৯৯৬ সালে খালেদা জিয়া নেতৃত্বাধীন সরকার কিন্তু একতরফা নির্বাচন সম্পন্ন করে সরকার বানিয়ে ফেললেও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি পূরণে বিল পাশ করে একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের পথ করে দিয়েছিল। এতে পুনরায় ক্ষমতায় আসার ব্যাপারে তাদের আত্মপ্রত্যয় না থাকলেও খুব খারাপ ফল করার শঙ্কা ছিল না। নির্বাচনে ১১৬ আসন পেয়ে দেশের সর্ববৃহৎ বিরোধী দল হিসাবে আত্মপ্রকাশও করে বিএনপি। এটি উল্লেখ করতে হলো এজন্য যে, কোনো দলনিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন হলে তাতে বেশ খারাপ ফল করার শঙ্কায় বোধহয় রয়েছে ক্ষমতাসীনরা। বিরোধী দল থেকেও বলা হচ্ছে, নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা হলে ক্ষমতাসীনরা ‘দশটি আসনও’ পাবে না এবং এমন শঙ্কার মুখে তারাই নাকি নির্বাচন বর্জন করবে!
বাংলাদেশ সত্যি বলতে এমন একটা পরিস্থিতির মধ্যে এসে পড়েছে এবং ক্রমে এটা সৃষ্টি হয়েছে নির্বাচনকালীন দলনিরপেক্ষ সরকারব্যবস্থা বাতিলের কারণে। ব্যবস্থাটি বহাল থাকলেই ক্ষমতার হাতবদল হতে হতে দেশে গণতন্ত্র ও সুশাসন জোরদার হয়ে যেত, সেটা অবশ্য হলপ করে বলা যায় না। তবে টানা তিন মেয়াদে সরকার পরিচালনার মাধ্যমে একটি সরকার যেমন কর্তৃত্ববাদী হয়ে উঠেছে এবং যে কোনো মূল্যে আরও দীর্ঘদিন ক্ষমতায় টিকে থাকতে চাইছে, সে পরিস্থিতি অন্তত তৈরি হতো না। প্রশাসন, ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এবং দেশের বাইরে প্রধানত চীন ও রাশিয়ার সমর্থনে সরকার যেভাবে ক্ষমতা ধরে রাখতে সচেষ্ট, সেটাকে কার্যকরভাবে চ্যালেঞ্জ করার মতো ক্ষমতা দেখা যাচ্ছে বিরোধী দলেরও নেই। জনসমর্থন বাড়লেও বিদ্যমান অবস্থায় ভোটের বাক্সে এর প্রতিফলন ঘটিয়ে ক্ষমতায় ফিরে আসার সুযোগ তাদের সামনে অনুপস্থিত।
এ অবস্থায় কীভাবে নির্বাচন ঘিরে সৃষ্ট সংকটের নিষ্পত্তি হবে, সেটা এক গুরুতর প্রশ্ন। বিরোধী দলের দাবির সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পশ্চিমাদের অবস্থান মিলেমিশে যাওয়ায় অবশ্য মনে করা হচ্ছে, তাদের কোনো ব্যতিক্রমী ভূমিকায় এখান থেকে উত্তরণের একটা পথ হয়তো মিলবে। এটা আবার দেশকে নতুন কোনো সংকটে ফেলে কিনা, সে প্রশ্নও রয়েছে। এমন এক নজিরবিহীন প্রশ্নের মুখে জাতিকে দাঁড় করিয়ে দেওয়ার দায় যাদের-তারা এর কী জবাব দেবেন?
হাসান মামুন : সাংবাদিক, বিশ্লেষক



