আ মরি বাংলা ভাষা
ড. মাহবুব হাসান
প্রকাশ: ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, ১২:০০ এএম
প্রিন্ট সংস্করণ
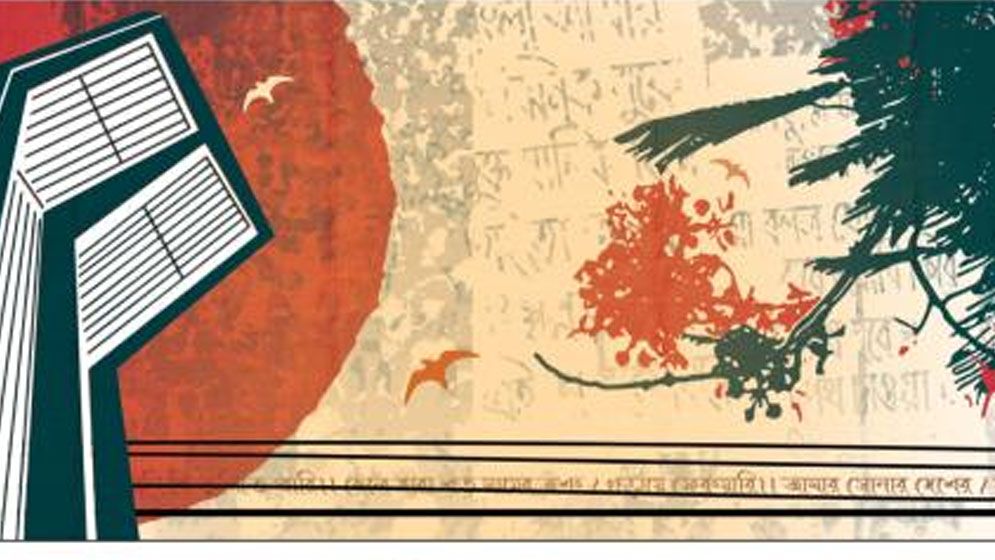
এ শিরোনামটি আমরা বহুকাল ধরে পড়ছি। বক্তৃতায় শুনে এতটাই মুগ্ধ হয়ে আছি যে, এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য় কী তা নিয়ে ভাববার অবকাশ পাইনি। কারণ পণ্ডিত মহাজনের মুখে বাংলা ভাষার ওই শব্দের অনুরণন এতটাই প্রগাঢ় হয়ে ছে যে, আমাদের মতো শব্দের আমজনতার পক্ষে তার তল-কাঠামোর (ডিপ স্ট্রাকচার) ব্যঞ্জনার্থ বোঝার প্রয়োজন হয়নি। প্রয়োজন হলেও আমরা সে পথে এগোনোর সাহস করিনি। আমরা বাংলা ভাষার সৌন্দর্য সম্পর্কে কী আর জানি? তাই, পণ্ডিত মহাজনদের হাতেই আমরা ওই দায়িত্ব অর্পণ করে স্বস্তিতে আছি। বা আমরা আজ বলতে পারি স্বস্তিতে ছিলাম। আমরা প্রায়ই বলি ও লিখি যে স্বস্তিতে ছিলাম, কিন্তু বাংলা ভাষার মতোই যে সেই বোধসত্তা প্রবহমান নদী, এটা ভুলে যাই। এখনো আমরা ভাষার সেই প্রবহমানতার ভেতরেই অবগাহন করছি। কখনো ডুব-সাঁতারে ভেসে যাচ্ছি, কখনো চিৎ-কাত সাঁতারে সেই স্রোতের মধ্যে নিজেদের রেখে এগিয়ে যাচ্ছি। কাঁথা সেলাইয়ের মতো সাঁতারে-সম্ভারে তাকে বুনে চলেছি। তাই এ চলমানতার নিরিখটিকে ওই প্রবহমানতার মধ্যে ছিলাম না বলে, আছি বলাই ভালো।
আমরা যখন খুব ছেলেবেলায় পুকুরে, পাগারে মা-বাবার সাহায্য নিয়ে সাঁতার শিখতাম, শিখে নদীতে সাঁতরেছি নদীর খরস্রোতকে তোয়াক্কা না করে, সাহসে ভর করে ওপারে আমাদের পৌঁছাতেই হবে,-এ সংকল্প নিয়ে, তখন কিন্তু একবারও মনে আসেনি যে, আমার মায়ের শেখানো ভাষা নদীতেও আমাদের সাঁতরাতে হবে, শিখতে হবে অনেক জটিল-জঙ্গমতা এবং উপরি-কাঠামো আর তল-কাঠামোর বহু কিছু। যখন জানতে ও বুঝতে পারলাম তখন অনেক বয়স হয়ে গেছে আর জঙ্গম পৃথিবীর রূপ-রসও গেছে পালটে। জীবন তো ওই বহমান নদীরই সহোদর, তাকে সামনের দিকে টেনে নিয়ে যেতে হলে বয়স হয়ে গেছে, এই বলে তাকে পাশ কাটিয়ে সামনে এগোনোর কোনো উপায় নেই। জীবন সংগ্রামের ভেতরে আছে স্বস্তি ও অশান্তির নানা মহলের অনুপুঙ্খ বিষয়-আশয়। তার পরও আমরা আমজনতা পণ্ডিত-মহাজনদের হাতে ওই দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে ‘আ মরি বাংলা ভাষা’ বলে আবেগে-উচ্ছ্বাসে নিজেদের অরূপ-রতন মেলে ধরি।
ক.
আমরা কি যুক্তিশীল জাতি? আমরা কি সব বিষয়ে র্যাশনাল বা যুক্তিবাদী? মনে হয় না। আমরা একটুতেই আবেগে উচ্ছ্বসিত হই, কিংবা নেতিয়ে পড়ি। সংস্কৃতি আমাদের শিখিয়েছে যে, একটি জাতি সত্তার সব কিছু যুক্তি দিয়ে বর্ণনা বা ব্যাখ্যা করা যায় না। যুক্তি-অযুক্তি, যুক্তি-অযুক্তির ঊর্ধ্বের এমন অনেক কিছু আছে, যা ব্যাখ্যা করা যায় না। যুক্তির চেয়ে সেখানে বিশ্বাস অনেক বেশি শক্তিশালী। যেমন ধর্ম। কোনো ধর্মই পুরোপুরি যুক্তি দিয়ে বোঝা ও উপলব্ধি করা যায় না। সেখানে বিশ্বাস সচল।
আমাদের আবেগ, জাতি-চেতনার নানামাত্রিক আবেগকে আমরা চলমান ইতিহাস, রাজনৈতিক ও সামাজিক যুক্তি দিয়ে কী ব্যাখ্যা করতে পারি? নাকি ব্যাখ্যা করা যায়? হয় তো যায়, কিংবা যায় না। এ দোমুখো দোদুল্যমানতা নিয়েই কিন্তু আমরা বেঁচে আছি, আমাদের নিত্যদিনের রাজনৈতিক ও সামাজিক কাজকর্ম চালাচ্ছি। এ চালানোটাই হচ্ছে সাংস্কৃতিক প্রবাহ। আর এরই অন্তর্গত হচ্ছে আমাদের ভাষা-সাহিত্যের সব কিছু।
আবেগের প্রভাব এতটাই যে, আমরা একটি বক্তৃতাকে শুনেই বলি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বক্তৃতা। একবারও এটা ভাবি না যে পৃথিবীতে বহুরাস্ট্র আছে, বহুভাষা আছে, বহু রাজনীতিক আছেন, বহু প্রজ্ঞাবান আছেন, বহু সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞানের ভান্ডার আছে এবং তাদেরও শ্রেষ্ঠ রাজনীতিকদের শ্রেষ্ঠ বক্তৃতা আছে। কিন্তু আমরা সেটা মানতে রাজি না। আমাদের আবেগের প্রাবাল্য এতটাই যে নিজেদের অস্তিত্বকেও যেন অস্বীকার করে ফেলতে চাই। যুক্তি সেখানে অচল দোআনি।
খ.
আ মরি বাংলা ভাষার জন্য যারা ১৯৪৮ সালে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ আন্দোলন করেছিলেন, যারা ১৯৫২ সালে ৮ ফাল্গুন রক্ত দিয়ে, জীবন উৎসর্গ করেছিলেন বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে জন-আকাঙ্ক্ষার বুলি হিসাবে প্রতিষ্ঠার জন্য, তারা আমাদের শিরোস্ত্রাণ হয়ে বিরাজমান। সালাম, রফিক, সফিক, বরকত, জব্বার নামগুলোকে জাতির সূর্যসন্তান হিসাবে বসিয়ে রেখেছি। কিন্তু আত্মবলিদানের ওই মহাপুরুষদের জীবনদানের কী লক্ষ্য ছিল তা আমরা ভুলে গেছি। এখন কেউ আর সালাম রফিক সফিক, বরকত, জব্বার নামগুলো নিজের শিশু সন্তানের নাম হিসাবে রাখেন না। অন্তত নগরের বাসিন্দারা ছেলেমেয়েদের নাম রাখেই না। মহানগরের মধ্যবিত্ত শ্রেণির শিশুর নাম হচ্ছে বা তারা রাখেন শাশা, মিশা, কেউ বা রাখেন এলিস, আদিতা অ্যালাইনা, আজলান, সাফুয়ানা ইত্যাদি। যেসব নাম লিখলাম, সেগুলো বাংলা শব্দের নয়। এটা আমরা সহজেই বুঝতে পারি। তবে এই এরাই, এদের পিতা-মাতা, খালা, ফুপু এবং ভাইয়েরা ফেব্রুয়ারি মাস এলেই তাদের সাংস্কৃতিক চেহারা পালটে নিতে থাকে। ‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি? এ গানের তালে তালে তাদের চেহারায় একটু কাঁদো কাঁদো ভাব ফুটে ওঠে। যেন তারা কতটা ব্যথাদীর্ণ হয়েছে ৫২-এর কারণে। সেটা বোঝাতে চায়। প্যান্ট-শার্ট পালটে পায়জামা-পাঞ্জাবি, প্যান্টের ওপর ফতোয়া, গলায় নামাবলীর মতো উত্তরীয় ঝুলিয়ে সেজে বৈশাখের খরোরোদ্রের তাপে ঘামতে থাকা প্রকৃতির মধ্যে বাঙালিয়ানা মহড়া চলে। আর সারা বছর আমাদের পরনে ওঠে প্যান্ট-শার্ট আর প্রয়োজনে স্যুট-টাই ইত্যাদি। আমরা ঔপনিবেশিক পশ্চিমা সভ্যতার পোশাক-আশাক আর আচার-আচরণ অনুসরণ করে নিজেদের প্রাগ্রসর নাগরিক করে তুলি। চাল-চলনে, বুলি-বৈভবে ইংরেজি শব্দের বাহার সাজিয়ে নিই। আবার প্রয়োজনে পরিবর্তন করে পায়জামা-পাঞ্জাবি, ফতোয়া ইত্যাদি ব্যবহারে ফিরে আসি। এটাই ফেব্রুয়ারির আগে ও পরের ধারা। এ ধারাকে ধারণ করেই কি আমাদের ‘আ মরি বাংলা ভাষা’ চলে? না, চলে না। ফেব্রুয়ারি শেষ হওয়ার আগেই আমাদের সাংবাৎসরিক ভাষা ও পোশাক পালটে যায়। কেন যায়? সেটা ভাবতে হবে।
১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ছিল বসন্তের দিন। হলুদ আর লালের সমারোহের ওই দিনটি ছিল বাংলা সনের ফাল্গুনের ৮ তারিখ। কিন্তু আমরা সেটা ভুলে গেছি। কীভাবে আমরা সেটা ভুলে গেলাম? ‘ওরা আমার মুখের ভাষা কাইর্যা নিতে চায়’ আবদুল লতিফের রচনা ও সুরে একুশের প্রথম গান গীত হলেও, সেই গান বেশি দিন টেকেনি। বরং আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর লেখা গান আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি/ আমি কি ভুলিতে পারি? সুরারোপ করেন সুরকার আলতাফ মাহমুদ (১৯৭১-এর শহিদ) এবং তা নব্য জাতিসত্তায় যেন পেখম মেলে ধরে। নাগরিক ও সাংস্কৃতিক চেতনার রূপকাররা এ গানের মর্মবাণী ছড়িয়ে দেন। ফলে গৃহিত হয় জনমনে। আবদুল লতিফের গানে ছিল লোকসুর ও চাষাভুষাদের আবেগের ঢেউ-দোলা। জনমানুষের নিত্যদিনের বিষয়-আশয় আর চিন্তার প্রতিফলন ছিল সেই গানে। আর গাফ্ফার চৌধুরীর লেখা গানে ও আলতাফ মাহমুদের সুরে যে করুণ আবহ সৃষ্টি হয়, তা নাগরিক মনন ও মণীষায় নতুন ঢেউ তোলে। আবদুল লতিফের গান ও সুর ওই নব্য শিক্ষিত নগরশ্রেণির রুচিতে বাধে। কারণ তাদের সাংস্কৃতিক রুচিতে ওই গান নগর-চেহারা পায়নি। তা গ্রাম বাংলার মানুষের বিষয়টি রূপায়িত হয়। সাংস্কৃতিক-জীবনের নিয়ন্ত্রক শ্রেণি তাই ওই গান ও সুর নেয়নি। কীভাবে শ্রেণিবিভক্ত সমাজে জাতীয় আকাঙ্ক্ষার শিরে বসে যায় ক্ষুদ্র শিক্ষিত ইউরোপিয়ান চেতনার ধারকদের দেওয়া গানে? স্পষ্ট হয়ে ওঠে বাংলাদেশের জনশ্রেণির শ্রেণির রূপ, এভাবেই।
এই পথ ধরে পরবর্তী দশকগুলোতে চলতে থাকে নাগরিক শিক্ষিত শ্রেণির কালচারাল হেগেমনি বা আধিপত্যবাদিতার ধারা। তারা দেশের গ্রামস্তরের প্রতিটি স্কুলে স্থাপন করে শহিদ মিনার। এ শহিদ মিনার আমাদের চেতনার নির্মাতা হিসাবে কাজ করে। একে আমরা খারাপ বলছি না। কিন্তু রফিক, শফিক, বরকত, জব্বার যে ভাষার জন্য জীবন দান করেছিল, আজকে আমরা যে ভাষায় কথা বলি, যাকে বলে কলোক্যাল স্টান্ডার্ড ভাষা, তা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ভাষা নয়। এ ভাষা আরো ক্ষুদ্রতর হয়েছে। নাম দেওয়া হয়েছে প্রমিত বাংলা। এ স্ট্যান্ডার্ড কলোক্যাল বা প্রমিত ভাষায় স্কুল কলেজের পুস্তক লিখিত হলেও, ওই ভাষায় কিন্তু গ্রামের ছেলেমেয়েরা আজও দৈনন্দিন জীবনে কথা বলে না। তাহলে কেন ৫২-এর শহিদরা জীবন দান করেছিল? তাদের জীবন দান তো বিসর্জনের শামিল হলো আজ। কিন্তু কেন? এর দায় কার? এর জবাব কে দেবে?
গ.
দায় কী আমি এড়াতে পারি? না, পারি না। এ-দায় কি দেশের প্রজ্ঞার অধিকারী সংস্কৃতিবান সব স্তরের শিক্ষক, সমাজনেতা, রাজনৈতিক নেতা, সরকারি দলের মন্ত্রী-মিনিস্টার, এমপি এবং তাদেরই তাবেদার শ্রেণি কী দায় এড়াতে পারেন? যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাদের কি কোনো দায় নেই? যারা নুন, চিনি, হলুদ মরিচের ব্যবসা করেন, তাদের দায় আমরা কেমন চোখে দেখব? যারা আমদানি-রফতানি বাণিজ্য করে তারা কি এড়াতে পারেন? একটি কোম্পানির নাম যদি হয় আইকন ফ্যাশন অ্যাপারেল, বা বাটারফ্লাই গার্মেন্ট, একটি গ্রুপের নাম যদি হয় এমজিআই, মুরগির খাদ্যের উৎপাদক কোম্পানির নাম রাখেন রাসেল পোলট্রি ফিড কোম্পানি, পোলট্রি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের নাম যদি হয় কাজী ফার্ম, সয়াবিন তেলের আমদানি কারকের নাম রূপচাঁদা বা তীর হওয়াটা অন্যায় নয়, বসুন্ধরা গ্রুপের আসল ব্যবসা যাই হোক না কেন, পুঁজির ধর্ম অনুযায়ী তারা ইউরোপীয় বা আমেরিকান সংস্কৃতির প্রভাবে পোক্ত।
এদের বাইরে, যারা ছোট দোকানদার, বা চেইনশপ আগোরা, ডেইলি শপিং, রেস্তোরাঁর নাম পিজ্জা হাট, ও হান্ডি, সান্দ্রা, কফিশপের নাম গ্লোরিয়া জিন্স, বিল্ডিংয়ের নাম টুইন টাওয়ার, সেন্টার পয়েন্ট, চেইন পোশাক বিক্রির দোকানের নাম আর্টিসান, বহুতল বাজারের নাম সিটি সেন্টার, সিটি হার্ট, পিংক সিটি, পুলিশ প্লাজা, ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ড, ফিউচার পার্ক, পোষা পশু-পাখির খাদ্যের দোকান পেট শপ, পাস্তুরিত দুধের প্যাকেটের নাম ফার্মফ্রেশ, মিল্ক ভিটা, আড়ং, এসিআই মিল্ক। খাবারের দোকানের নাম ভূতের বাড়ি, পার্লার, পেস্তা শপ, নাপিতের দোকানের নামও ভিনদেশি। এ রকম অগণন নাম এ ঢাকা শহরের বিচিত্র ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের, যা আমাদের এটাই বলছে যে আমরা কি বাংলা ভাষার জন্য জীবন দান করেছিলাম? এ নামের মহিমা ছড়ানোর জন্যই কি আমরা মুক্তিযুদ্ধ করে দেশ হানাদারমুক্ত করেছিলাম? মহান একুশ কি তার গৌরব আর গাথা নিয়ে আমাদের শিশু-কিশোরদের জীবনচেতনায় জেগে আছে। নাকি তাদের নামের বহুভাষিক প্রভাব নিয়েই হয়ে উঠছে এক একজন আন্তর্জাতিক শিশু-কিশোর-যুবক। তাদের পিতা-মাতাদের মতোই শেকড়-বাকড়হীন হয়ে গড়ে উঠছে বামনগাছ হয়ে। আপনারা নিশ্চয় বামনগাছ বা বনসাই বৃক্ষ হওয়ার জন্য দেশ স্বাধীন করেননি। বনসাই দেখার জন্য আদাজল খেয়ে সংগ্রাম করেননি। আমাদের শিশুরা বেড়ে উঠছে ওই বনসাই বৃক্ষ হয়ে। শেকড়-বাকড়হীন মানে, আত্মপরিচয়হীন হয়ে। কারণ তাদের নামের সঙ্গে ও তাদের সাংস্কৃতিক চিন্তাধারার সঙ্গে জীবনযাপনের মিল-মহব্বত নেই। তারা বাংলাদেশের সোসিও-কালচারাল এনভারনমেন্টে বেড়ে উঠছে, কিন্তু তার চিন্তা-ভাবনার আবহটি বিদেশি বা ভিনদেশি স্বপ্নে মোড়ানো। সংস্কৃতিগতভাবে তারা নো-ম্যান্সল্যান্ডের মানুষ।
ঘ.
কেন বাংলা ভাষা ও তার রূপোশ্বর্য এমন এক সাংস্কৃতিক ফাটলের মধ্যে পড়েছে? তার দায় দায়িত্ব কার বা কাদের? সোজা কথায় তার গোটা দায় সরকারের এবং শিক্ষিত সমাজের, যারা বাংলার জন্য মায়াকান্না ছাড়া আর কোনো কিছুই করেনি।
কী কী করেনি, তার একটা তালিকা করা যাক।
ক. ভাষার আন্তর্জাতিক পরিচয়ের জন্য ৫২কে কেন্দ্রে রেখে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট করা হয়েছে। কিন্তু সেই ইনস্টিটিউট কিছু পুস্তিকা তৈরি ও বিতরণ ছাড়া আন্তর্জাতিক সমাজের কাছে কিছুই উপস্থাপন করতে পারেনি।
খ. বাংলা রাষ্ট্রভাষা হওয়া সত্ত্বেও সরকারি দফতরে বাংলা সর্বস্তরে চালু করতে ব্যর্থ হয়েছে।
গ. আদালতের ভাষা হিসাবে বাংলাকে প্রতিষ্ঠিত করা যায়নি বা হয়নি। উচ্চ আদালতে ইংরেজিতেই সওয়াল-জবাব চলে। বিচারপতিরা ইংরেজিতেই রায় লিখতে ভালোবাসেন।
ঙ. আইনজীবীরা যদিও বাংলাই ভাবতে ভালোবাসেন, কিন্তু তারা যেহেতু বার-এট-ল পড়েন বিলেতে, বা দেশের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে, ফলে তাদের শিক্ষাকেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক বোধে ইংরেজি ভাষা ও এটিকেট সেঠটে যায় চিন্তা জীবনের সঙ্গে। তো, সেই দেশের আইন ও যাবতীয় আইনের প্রজ্ঞাবানরা পোশাকে ও আচরণে, দিব্যজ্ঞানে ব্রিটিশ চেতনারই অনুকারী। পরিচয়পত্রে লেখেন ব্যারিস্টার।
চ. সরকার আইন করেছেন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অন্তত একটি বিভাগ খুলতে হবে। সে আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখিয়ে ১১৫টি বেসরকারি বিশ্বদ্যিালয়ের মধ্যে মাত্র ৫-৭টিতে বাংলা বিভাগ চালু করা হয়েছে। বাদবাকিরা কেন খোলেননি, কেন আইন অমান্য করে ওই প্রতিষ্ঠানগুলো চালাতে পারছেন? আমি জানি, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানে যারা কাজ করেন তারাও এর জন্য কম দায়ী নয়। বিগত স্বৈরাচারী আমলে বিশ্ববিদ্যালয় নামক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক গ্রুপ, নানা বাহানায় এটা ঠেকিয়ে রেখেছে।
ছ. বাংলা ভাষা শিক্ষার জন্য তৃণমূল স্তরের স্কুল ও হাই স্কুলগুলোতে কেন ভালো মানের শিক্ষক নিয়োগ করা হয়নি বা হয় না? তাদের জন্য বেতন কেন নিচু মানের? কেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চাকরি-বাজার সম্প্রসারিত হয়নি? কেন রাষ্ট্রভাষা বাংলাকে গুরুত্ব না দিয়ে সরকারি দফতরের আমলারা ইংরেজিতে মজে আছেন?
এর একটি বড় কারণ সাংস্কৃতিক আভিজাত্য বা কালচারাল হেগেমনি। ব্রিটিশরা আমাদের চেতনায় এটা বুনে গেছে যে কালচারালি আমরা খুবই পুয়র আর তারা কালচারালি ব্রাইট। পৃথিবীর জ্ঞান-জগতের পুরোটাই তাদের, বাদবাকিরা জ্ঞানহীন বা নিম্নমানের। আমেরিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার সোনাদানা লুটে নিয়ে গিয়ে গোটা ইউরোপ ধনবান হয়ে শিল্পবিপ্লব ঘটায়। আর সেই অর্থ ও বিত্তের প্রাচুর্যে তারা আমাদের ওপর রাজত্ব করেছে। ভারতীয় উপমহাদেশের সম্পদের গল্প শোনার পর তারা ভারত দখল করে নেয়। তাদের শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহের উৎস করে তোলে ভারত উপমহাদেশকে। সে উপনিবেশের শাসনকে দীর্ঘস্থায়ী করতেই সাংস্কৃতিক আগ্রাসন চালায় ব্রিটিশরা। আমরা আজ সেই আগ্রাসনের শিকার। এই যে প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নাম ইংরেজিতে রাখা হচ্ছে, কিন্ডারগার্টেন রাখা ও তার অনুমোদন দেওয়ার পেছনেও আছে ওই কালচারাল হেগেমনি। আর তার পেছনে কাজ করছে আগ্রাসন চেতনা। আমরা সেটা বুঝতে পারছি না। আন্তর্জাতিক ভাষার নামে ইংরেজিসহ ইউরোপিয়ান ভাষাগুলোকে কেন এতটা মর্যাদার আসনে বসানো হয়েছে, তা এখন আমরা বুঝতে পারছি। আজ কেবল পোশাক-আশাকেই নয়, সর্বত্র এ আগ্রাসন চলছে। খুব সহজেই বুঝতে পারবেন যে, চুল কাটার দোকানের নাম হট সেলুন। বই প্রকাশক নাম রাখছেন অ্যাডর্ন। শুনেছি বাংলাভাষার পত্রিকার নামও নাকি ইংরেজি নামে আছে। এ বিদেশি সাংস্কৃতিক আগ্রাসনই আমাদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে নিঃশেষ করে দেবে একদিন।

