কৃষি খাতের রূপান্তর ও আধুনিকায়ন
ড. জাহাঙ্গীর আলম
প্রকাশ: ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, ১২:০০ এএম
প্রিন্ট সংস্করণ
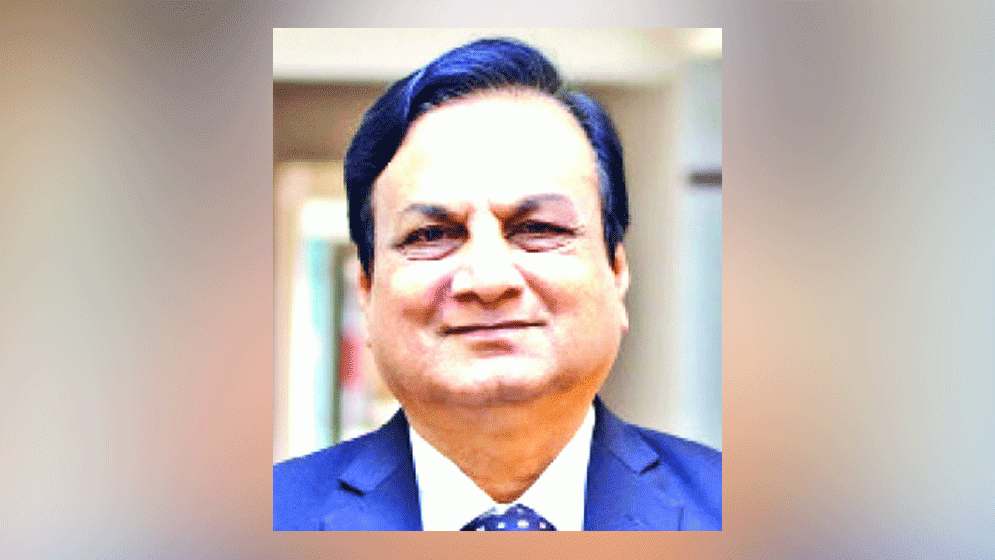
কৃষিকাজকে ইংরেজি ভাষায় বলা হয় ‘ফার্মিং’। মাঠের শস্য, ফলের গাছ, মাছ, পশুপাখি ইত্যাদির উৎপাদন বিশ্বব্যাপী কৃষিকাজের অন্তর্ভুক্ত। এ কাজ থেকে আমরা পেয়ে থাকি খাদ্য, বস্ত্র তৈরির আঁশ, জ্বালানি এবং শিল্পের কাঁচামাল। আজ থেকে প্রায় ১০ হাজার বছর আগে সূত্রপাত ঘটেছিল নিয়মানুগ কৃষিকাজের। এর আগে মানুষ ছিল শিকারি ও সংগ্রহকারী। অতঃপর সে শুরু করে বৃক্ষরোপণ, প্রাণী পালন ও শস্যের চাষ। মিশর ও ভারতে উর্বর মাটিতে বীজ বুনে ফসলের আবাদ করে মানুষ সূত্রপাত করেছিল কৃষিসভ্যতার। আফ্রিকা, নিউইয়র্ক, আমেরিকা ও চীনেও স্বতন্ত্রভাবে উন্মেষ ঘটেছিল কৃষিকাজের। প্রাচীন শস্যগুলোর মধ্যে ছিল গম, বার্লি, শিম, মসুর, মটর ইত্যাদি। খ্রিষ্টের জন্মের প্রায় ৭০০০ বছর আগে গমের চাষ শুরু হয় ভারতে। এর প্রায় ১০০০ বছর পরে দূরপ্রাচ্যে শুরু হয় ধানচাষ। আরও প্রায় ১০০০ বছর পর ভুট্টার চাষ শুরু হয় আমেরিকায়। প্রথমদিকে চাষ করা শস্যগুলোর জাত ছিল বুনো। এগুলোকে পোষ মানিয়ে গার্হস্থ্য করতে সময় লেগেছে প্রায় ৩০০০ বছর। অতঃপর ক্রমান্বয়ে মানুষ মনোনিবেশ করেছে আধুনিক চাষাবাদে। ভূমিকর্ষণে কাঠের সাধারণ লাঙল প্রবর্তিত হয় প্রায় খ্রিষ্টপূর্ব ৩৫০০ সালে, এর উন্নয়ন হয় মধ্যযুগে। ১৩০০ খ্রিষ্টাব্দে প্রবর্তিত হয় অধিক মাটি কর্ষণকারী উন্নত মোলবোর্ড লাঙল। এ সময় আগাছা পরিষ্কার, বুনো গাছ কাটা, সেচ প্রদান ও পানি নিষ্কাশন কার্যক্রমের প্রসার ঘটে। তখন গবাদিপশুর খাবার জোগানোর জন্য চাষাবাদ শুরু হয় বিভিন্ন ডালজাতীয় শস্যের। এ সময় প্রচলিত সাধারণ মানের কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে যে পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপাদিত হতো, তাতে মানুষের প্রয়োজন মিটত। ১৩১৫-১৭ খ্রিষ্টাব্দের বৈরী আবহাওয়ার সময় ছাড়া তেমন কোনো খাদ্যাভাব কখনো কোথাও পরিলক্ষিত হয়নি।
অতঃপর শুরু হয় চাষাবাদের আধুনিককাল। ১৪৯২ সালের পর থেকে শস্য ও গবাদি পশুর জাত বিনিময় শুরু হয় এক দেশ থেকে অন্য দেশে। আলুর উৎপাদন ও খাদ্য হিসাবে এর ব্যবহার পরিচিতি লাভ করে উত্তর ইউরোপে। রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার জনপ্রিয় হয়ে ওঠে সারা বিশ্বে। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের শিল্পবিপ্লব কৃষিক্ষেত্রে যন্ত্রের প্রচলন ঘটায়। চাষাবাদে শুরু হয় ট্রাক্টর ও টিলারের ব্যবহার। ফসল কাটার জন্য তৈরি হয় কম্বাইন্ড হার্ভেস্টার। বিংশ শতাব্দীর সবুজবিপ্লব গম, ভুট্টা ও ধান চাষে উচ্চফলনশীল জাতের ব্যাপক প্রবর্তন ঘটায়। উন্নত বীজ, রাসায়নিক সার ও পানি সেচ সম্প্রসারণের মাধ্যমে কৃষির উৎপাদনের সূচিত হয় এক অভাবনীয় পরিবর্তন। ১৭০০ থেকে ১৯৮০ সালের মধ্যে সম্প্রসারিত চাষাবাদের মাধ্যমে আবাদি জমির পরিমাণ ৪৬৬ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া নিবিড় চাষাবাদের ফলে ১৯০০ থেকে ১৯৯০ সাল নাগাদ গমের উৎপাদন হেক্টরপ্রতি বৃদ্ধি পায় আড়াইগুণ। তেমনি নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পায় ধান, ভুট্টা ও অন্যান্য খাদ্যশস্যের উৎপাদন। দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির মুখে সারা বিশ্ব আশ্চর্যান্বিত হয়ে অবলোকন করে খাদ্যের উদ্বৃত্ত। ইতোমধ্যে একটি নতুন বিপ্লব সূচিত হয় কৃষিক্ষেত্রে। এটি জীব প্রযুক্তির বিপ্লব। এর মধ্যে আছে উদ্ভিদ বিভাজন ও টিস্যু কালচার, মলিকুলার মার্কার ব্যবহারের মাধ্যমে উদ্ভিদ প্রজনন এবং ডিএনএ প্রযুক্তি বা কৌলিতাত্ত্বিক পরিবর্তনের মাধ্যমে উদ্ভিদ ও প্রাণী সৃষ্টি (জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং)। এ প্রযুক্তির ধারণ ও সম্প্রসারণ এখন সারা বিশ্বে অগ্রসরমান।
কৃষির সবচেয়ে বড় অবদান মানুষ ও প্রাণীর জন্য খাদ্য সরবরাহ করা। এর সরবরাহ হ্রাস পেলে বাজারে মূল্যবৃদ্ধি পায়। আবার সরবরাহ বৃদ্ধি পেলে মূল্যস্ফীতি কমে যায়। মানুষের চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে খাদ্যশস্যের জোগান বৃদ্ধি পেলে দ্রব্যমূল্য ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে থাকে। তাতে ক্ষুধা ও অপুষ্টি নিবারণ সম্ভব হয়। সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যেতে পারে দেশ ও জাতি। তাছাড়া কৃষি উন্নয়ন ত্বরান্বিত হলে অকৃষি খাতের প্রবৃদ্ধিও ত্বরান্বিত হয়। কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদনকারী কৃষক তাদের আয়ের একটা বড় অংশ খরচ করতে পারে শিল্পপণ্য ক্রয়ের জন্য। তাতে শিল্পপণ্যের অভ্যন্তরীণ বাজার সৃষ্টি হয়। অধিকন্তু কৃষি খাত শিল্প খাতের জন্য কাঁচামাল সরবরাহ করে। উদ্বৃত্ত শ্রমিক অবমুক্ত করে শিল্পে নিয়োজিত করার জন্য। উন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে কৃষি আয়ের উদ্বৃত্ত বিনিয়োগ করেই গড়ে ওঠে শিল্প। তদুপরি কৃষিপণ্য রপ্তানি করে আয় হয় অনেক বৈদেশিক মুদ্রা, যা শিল্প স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম আমদানিতে নিয়োজিত হতে পারে। এগুলো কৃষির উৎপন্ন দ্রব্য, বাজার, উৎপাদক ও বৈদেশিক মুদ্রা সম্পর্কীয় অবদান। কৃষিতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে উল্লেখিত অবদানগুলোর পরিধি সম্প্রসারণ করা সম্ভব। তাতে সুদৃঢ় হতে পারে জাতীয় অর্থনীতি।
উন্নয়নের প্রাথমিক স্তরে জিডিপিতে কৃষির অবদানই থাকে বেশি। এরপর ক্রমে বেড়ে যায় শিল্প ও সেবা খাতের অবদান, আর কৃষির অবদান হ্রাস পায়। বর্তমানে বিশ্বের মোট জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান প্রায় ৬ শতাংশ। তবে উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত এমন অনেক দেশ আছে, যেখানে জিডিপির প্রায় এক-ষষ্ঠাংশ এখনো কৃষি খাত থেকে আসে। তবে উন্নত দেশগুলোতে এ অবদান এখন নেমে গেছে ২ শতাংশের নিচে। বিশ্বের মোট শ্রমশক্তির অধিকাংশই একসময় কৃষিকাজে নিয়োজিত ছিল। এখন তা নেমে এসেছে প্রায় এক-তৃতীয়াংশে। বাকিরা চলে গেছে কৃষি খাত ছেড়ে। নিয়োজিত হয়েছে শিল্পে ও সেবা খাতে। পৃথিবীতে এখন এমন দেশও আছে, যেখানে কৃষিতে নিয়োজিত শ্রমিকের শরিকানা দুই শতাংশও নয়। উদারহণস্বরূপ আমেরিকা ও আর্জেন্টিনার কথা উল্লেখ করা যায়। সেখানে কৃষি খাতে নিয়োজিত শ্রমিকের হার যথাক্রমে মাত্র ১.৬ ও ১.২ শতাংশ। কিন্তু তাই বলে ওইসব দেশেও কৃষির অবদানকে খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। কারণ, একসময় কৃষির উদ্বৃত্ত দিয়েই সেখানে গড়ে উঠেছিল শিল্প ও সেবা খাত। এখনো সেখানে কৃষিজাত খাদ্যসামগ্রী ছাড়া মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার কোনো পথ নেই। খাদ্য হিসাবে কৃষিপণ্যের কোনো বিকল্পও হয় না।
কৃষি উন্নয়নের সূচনালগ্নে বিশ্বের উৎপাদনব্যবস্থা ছিল মিশ্র। বিভিন্ন শস্য, মৎস্য ও পশুপাখির উৎপাদন হতো মিশ্র খামার ব্যবস্থাপনায়। কৃষির উৎপাদন হতো খোরপোষ বা জীবনধারণ পর্যায়ে। এখন তা হয়ে গেছে বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত, কৃষকের উৎপাদন পরিকল্পনাকে প্রভাবিত করছে বাজার। তবু অনেক দেশ আছে পৃথিবীতে, যারা এখনো মিশ্র খামারব্যবস্থায় চাষাবাদ পরিচালনা করছে। বাংলাদেশ এর অন্যতম। এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলোর কৃষির উৎপাদন বর্তমানে অনেকটা বাজারমুখী হলেও মিশ্র উৎপাদনব্যবস্থা সর্বত্রই পরিলক্ষিত হচ্ছে। কৃষিতে প্রবৃদ্ধির হার রয়েছে উচ্চপর্যায়ে। বিশ্বের মোট কৃষি উৎপাদনেও এটি তাৎপর্যপূর্ণভাবে অবদান রেখে চলেছে। এক সময় ধারণা করা হতো পৃথিবীর জনসংখ্যা বাড়ছে জ্যামিতিক গতিতে আর খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়ছে গাণিতিক গতিতে। অতএব, পৃথিবীতে খাদ্যাভাব হবে, দুর্যোগ দেখা দেবে। এ ধারণার উদ্ভব ঘটিয়েছিলেন টমাস ম্যালথাস। কিন্তু তার প্রতিপক্ষের চিন্তাবিদরা বলেছেন, কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির প্রভাব উৎপাদনকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেবে। জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধি হটিয়ে দেবে খাদ্যোৎপানের প্রবৃদ্ধির হার। এখন তা সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। ১৯৭০ সালে বিশ্বে খাদ্যোৎপাদন ছিল ৮৯৩ মিলিয়ন টন। ২০২৪ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ২৮৩৬ মিলিয়ন টনে। এ সময় খাদ্যশস্যের উৎপাদন প্রতিবছর বৃদ্ধি পেয়েছে ২.১ শতাংশ হারে। অপরদিকে মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৩৪৭৮ থেকে ৮২০০ মিলিয়নে, বার্ষিক ১.৪ শতাংশ হারে। তাতে বিজয় সূচিত হয়েছে কৃষিবিজ্ঞানের। এ বিশ্ব হয়েছে খাদ্যে উদ্বৃত্ত। সেদিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান আরও ভালো। ১৯৭১-৭২ সালে এদেশে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ছিল প্রায় ১ কোটি টন। ২০২৪ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪ কোটি ৬৬ লাখ টনে। এই ৫৩ বছরে খাদ্যশস্যের বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধির হার হলো ২.৯ শতাংশ। অপরদিকে জনসংখ্যা বেড়েছে ৬.৮৪ থেকে ১৭.৩৬ কোটিতে। এর প্রবৃদ্ধির হার ছিল বার্ষিক ১.৮ শতাংশ। বিগত সত্তরের দশকের গোড়ার দিকে দেশে উচ্চফলনশীল খাদ্যশস্যের আবাদ ছিল মাত্র ১০ শতাংশ আবাদি জমিতে সীমাবদ্ধ। বর্তমানে তা ৯১ শতাংশ জমিতে সম্প্রসারিত হয়েছে। পানি সেচের আওতায় এসেছে প্রায় ৬৫ শতাংশ আবাদি জমি। এর প্রায় ৯৯ শতাংশই যন্ত্রনির্ভর। সনাতন শ্রমনির্ভর সেচের আওতায় রয়েছে মাত্র ১ শতাংশ জমি। হাল চাষে ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলারের ব্যবহার সম্প্রসারিত হয়েছে প্রায় ৯৫ শতাংশ জমিতে। কৃষক ব্যাপক পরিমাণে রাসায়নিক সার ও বালাইনাশকের ব্যবহার বাড়িয়েছে।
১৯৫১ সালে এদেশে শুধু ২৬৯৮ টন অ্যামোনিয়াম সালফেট দিয়ে রাসায়কি সারের ব্যবহার শুরু হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিভিন্ন জাতের সার মিলিয়ে ৬০ লাখ টন রাসায়নিক সার ব্যবহার হয়েছে। বালাইনাশকের ব্যবহার এখন বছরে ৩৮ লাখ টন। ১৯৫৬ সালে এর ব্যবহার শুরু হয়। ষাটের দশকের গোড়ার দিকে এর ব্যবহারের পরিমাণ ছিল বছরে প্রায় ২৫০ টন। বর্তমানে দুই, তিন ও চার ফসলি জমির পরিমাণ বেড়েছে। শস্য উৎপাদনের নিবিড়তা ১৯৭১-৭২ সালে ছিল ১৪৮ শতাংশ, এখন তা বৃদ্ধি পেয়েছে ১৯৮ শতাংশে। তবে কৃষি খাতে উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পেলেও জিডিপিতে এর অবদান হ্রাস পেয়েছে ষাট দশকের ৬০ শতাংশ থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১১ শতাংশে। শিল্প ও সেবা খাতে প্রবৃদ্ধির হার বেশি বিধায় জিডিপিতে কৃষির শরিকানা কমেছে। তবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে কৃষি খাতে উৎপাদন বৃদ্ধির গুরুত্ব বেড়েছে। শস্যবহির্ভূত কৃষি খাতে গত ৫৩ বছরে অনেক উন্নয়ন হয়েছে। স্বাধীনতা-উত্তরকালে দেশে মাছ, মাংস, ডিম ও দুধের বড় ঘাটতি ছিল। এখন তা অনেকটাই কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে মাছের উৎপাদন বছরে ৪৯ লাখ টন। মাংস ও দুধের উৎপাদন যথাক্রমে ৮৮ ও ১৪০ লাখ টন। ডিমের উৎপাদন ২৩৩৮ কোটি। গত ১৫ বছরে মাছ, মাংস, দুধ ও ডিমের উৎপাদনে বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ৩.৫, ১২.৮, ১১.৯ ও ৯.৪ শতাংশ। দেশের প্রত্যেক মানুষের জন্য বর্তমানে দৈনিক গড়ে ৭৯ গ্রাম মাছ, ১৪০ গ্রাম মাংস, ২২৫ গ্রাম দুধ এবং ১৮.৯ গ্রাম ডিম মজুত আছে; কিন্তু প্রকৃত ভোগ অনেক কম। বাজারে এসব প্রোটিনজাতীয় খাদ্যের দাম বেশ চড়া। কারণ ইউনিটপ্রতি উৎপাদন খরচ বেশি। আলু, শাকসবজি ও ফলমূলের উৎপাদন গত এক যুগে অনেক বেড়েছে। উৎপাদন মৌসুমে এগুলোর দাম সহনীয় থাকে। নিষ্ফল মৌসুমে বেশি হয়। স্বাধীনতার পর সত্তরের দশকের গোড়ার দিকে কৃষি অর্থনীতির প্রধান নিয়ামক ছিল শস্য খাত। কালক্রমে তার পরিবর্তন হয়েছে। ১৯৭১-৭২ সালে কৃষি জিডিপির প্রায় ৮০ শতাংশ শরিকানা ছিল শস্য খাতের। ২০২২-২৩ অর্থবছরে তা ৪৯ শতাংশে নেমে আসে। বর্তমানে কৃষি জিডিপিতে মৎস্য, পশুসম্পদ ও বনসম্পদের শরিকানা যথাক্রমে ২২, ১৫ ও ১৪ শতাংশ। অর্থাৎ বৃহত্তর কৃষি খাতে বহুধাকরণের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। শস্য খাতে বাড়ছে ফসলের বৈচিত্র্যকরণ।
বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে প্রতীয়মান হয়, কৃষিক্ষেত্রে বীজভিত্তিক আধুনিক প্রযুক্তি প্রসারের ফলে জীববৈচিত্র্য হুমকির মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। অতিরিক্ত রাসায়নিক সারের ব্যবহার জমির গুণগত মান হ্রাস করছে। সেচের পানির ব্যবহার বৃদ্ধির কারণে দেখা দিচ্ছে পানির সমস্যা। অতিরিক্ত কীটনাশকের ব্যবহার পরিবেশকে বিনষ্ট করছে। কোনো কোনো জীব প্রযুক্তিজাত খাদ্য মানুষের স্বাস্থ্যগত সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া কৃষির উৎপাদন ও পশুপালন বাতাসে মিথেইন গ্যাসের মাত্রা বাড়িয়ে দিচ্ছে, যা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক। এ অবস্থায় মানুষ এখন পরিবেশবান্ধব স্থায়ী কৃষি উন্নয়নের কথা ভাবছে। জৈব কৃষি ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন ও গ্রহণের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে। এরই মধ্যে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে কৃষির উৎপাদন বিঘ্নিত হচ্ছে। ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বন্যা ও খরা কমিয়ে দিচ্ছে বিশ্বের খাদ্য মজুত।
তদুপরি তেলের মূল্যবৃদ্ধির ফলে অনেক উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে খাদ্যশস্য থেকে উৎপাদন করা হচ্ছে ইথানল বা তেলের বিকল্প জ্বালানি। এরও চাপ পড়ছে খাদ্য মজুতের ওপর। বিশ্বব্যাপী খাদ্যমূল্য বাড়ছে। বাড়ছে ক্ষুধা ও পুষ্টিহীনতা। এতে উদ্বিগ্ন প্রত্যেক সচেতন মানুষ। বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এবং বিশ্বব্যাংকসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও সংগঠন এখন সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির ওপর। কৃষিতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির ওপর।
কৃষি বাঙালির প্রধান পেশা। প্রাচীনকাল থেকেই এদেশের মানুষের জীবন ও জীবিকার প্রধান উৎস ছিল কৃষি। এখানে বৃষ্টিপাত হয় পর্যাপ্ত। দেশজুড়ে নদ-নদীর অসংখ্য শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত। তাতে প্রতি বর্ষায় মাটির উপরের স্তরে জমা হয় পলির পুরো আস্তরণ। মাটি হয়ে ওঠে উর্বর। তদুপরি দেশের অধিকাংশ এলাকা সমভূমি হওয়ায় এখানে শস্যের উৎপাদন সহজ, ফলন হয় ভালো। সে কারণে এদেশে মানুষের মূল পেশা হয়েছে কৃষি। বেড়েছে কৃষিতে নিয়োজিত মানুষের ঘনত্ব। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এখানকার প্রায় ৭৭ শতাংশ মানুষ নিয়োজিত ছিল কৃষিকাজে। এখন তা নেমে এসেছে ৪৫ শতাংশে। বর্তমানে কৃষিবহির্ভূত গ্রামীণ কর্মকাণ্ডের পরিধি বেড়েছে, ত্বরান্বিত হয়েছে শহরভিত্তিক শিল্পকারখানায় শ্রমিক নিয়োগের হার। শহরমুখী বিভিন্ন কাজেও নিয়োজিত হয়েছে অনেক কৃষকসন্তান। অনেকে আবার দেশ ছেড়ে পাড়ি জমিয়েছে বিদেশে, অধিক উপার্জনশীল কাজের আশায়। ফলে কৃষিকাজে মানুষের চাপ কমেছে। বেড়েছে কৃষিশ্রমিকের মজুরি। অপরদিকে সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক সংস্কারের ফলে কৃষিতে ভর্তুকি কমেছে বিশ্বব্যাপী। উৎপাদনের আমদানিকৃত উপরকণমূল্য হয়েছে আকাশচুম্বী। তদুপরি এখানে তেল, বিদ্যুৎ ও গ্যাসের ঘন ঘন মূল্যবৃদ্ধির কারণে কৃষকের অবস্থা নাকাল। কৃষক তার উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য পাচ্ছে না। এদেশের প্রধান খাদ্যশস্য এক মন ধান বিক্রি করে সে তার উৎপাদন খরচটুকু তুলে আনতে পারছে না। অপরদিকে কৃষি খামারগুলো কাঠামোগত পরিবর্তনের মাধ্যমে ক্রমেই ছোট হচ্ছে।
১৯৯৬ সালে কৃষি খামারের গড় আকার ছিল ১.৭১ একর, ২০১৯ সালে তা ১.২৯ একরে হ্রাস পায়। প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র খামারের (০.০৫-২.৪৯) সংখ্যা ৭৯.১৭ থেকে ৯১.৮৯ শতাংশে বৃদ্ধি পায়। ফলে তাদের বিনিয়োগ সক্ষমতা হ্রাস পায়। অধিকন্তু বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম, নতুন বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, কলকারখানা ইত্যাদি প্রতিনিয়ত গ্রাস করে ফেলছে অনেক কৃষিজমি। ১৯৮৩-৮৪ সালে আবাদি কৃষিজমির পরিমাণ ছিল ৯.২ মিলিয়ন হেক্টর, ২০০৮ সালে তা নেমে এসেছে ৭.৭ মিলিয়ন এবং ২০১৯ সালে ৭.৫ মিলিয়ন হেক্টরে। ওই ৩৫ বছরে প্রতিবছর গড়ে ০.৫৮ শতাংশ কৃষিজমি হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে জনপ্রতি কৃষিজমির প্রাপ্যতা মাত্র ০.১১ একর। এমন পরিস্থিতিতে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও আবহাওয়া পরিবর্তনের অভিঘাত সামলে টেকসই কৃষি উন্নয়ন ও স্থায়ী উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যক্রম নিশ্চিত করার জন্য কৃষিতে সরকারি বিনিয়োগ বিপুল পরিমাণে বাড়াতে হবে। তাতে নিবিড় চাষাবাদ ও অগ্রসরমান কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রারণের মাধ্যমে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা বজায় রাখা সম্ভব হবে। সমৃদ্ধ হবে আমাদের কৃষি অর্থনীতি।
লেখক : কৃষি অর্থনীতিবিদ, গবেষক ও শিক্ষক; সাবেক মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট

