মূল্যস্ফীতি কমবে তো?
মামুন রশীদ
প্রকাশ: ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, ১২:০০ এএম
প্রিন্ট সংস্করণ
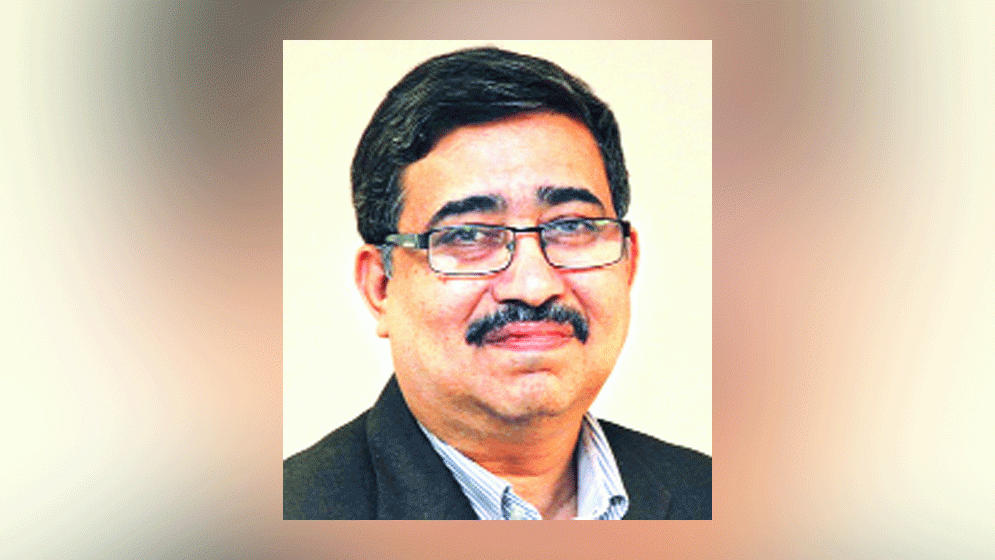
বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধির কারণ, এ অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য সরকার ও কেন্দ্রীয় বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়ে গভীর গবেষণা করার বোধহয় সময় এসেছে। স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয়েছে, দুর্বল অর্থমন্ত্রী আর একগুঁয়ে গভর্নর পালিয়ে গেছেন, ‘ভালো লোকের’ সরকার এসেছে, অপরাপর বা সমমানের অনেক দেশে পণ্যসামগ্রীর দাম কমেছে; কিন্তু বাংলাদেশে কমছে না।
অনেকেই বলেছেন এবং বলছেন-টাকার অবমূল্যায়ন, রিজার্ভ সংকটের কারণে আমদানিতে সীমাবদ্ধতা, জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি, বাজারের অব্যবস্থাপনা, করপোরেট মুনাফা বৃদ্ধির তাগিদসহ নানা কারণে দুবছর ধরে উচ্চ মূল্যস্ফীতিতে পিষ্ট সাধারণ মানুষ। সরকারের কোনো পদক্ষেপেই জিনিসপত্রের দাম নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। খাদ্যপণ্যের উচ্চ মূল্যস্ফীতিতে চরমভাবে ভুগছেন ভোক্তারা। বিশেষ করে দরিদ্র, নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনযাপন দিনদিন আরও কঠিন হয়ে উঠছে। আগে বারবার সুদের হার বাড়ালে সব ঠিক হয়ে যাবে বললেও সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিরা এখন বলছেন, লাগামহীন উচ্চ মূল্যস্ফীতি সহনীয় পর্যায়ে আসতে সময় লাগবে আরও এক বছর। অন্যদিকে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যমূল্য কমতে থাকায় মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। এক্ষেত্রে সরকারকে নানামুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে।
দেশে দুবছরের বেশি সময় ধরে টানা উচ্চ মূল্যস্ফীতি রয়েছে। আমরা জানি, ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ক্ষমতা হারানো আওয়ামী লীগ সরকারের জনপ্রিয়তা কমে যাওয়ার অন্যতম কারণ ছিল বাজারে পণ্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি রোধ করতে না পারা। ২০২২ সালে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে বিশ্বব্যাপী মূল্যস্ফীতি বেড়ে যায়। ভারত, শ্রীলংকাসহ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ এক থেকে দেড় বছরের মধ্যে মূল্যস্ফীতি কমাতে পেরেছে। কিন্তু বাংলাদেশ এর ব্যতিক্রম।
বিগত সরকারের পতনের পর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নিয়েই মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করাকে অগ্রাধিকার বলে ঘোষণা করে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত দৃশ্যমান কোনো উন্নতি দেখা যায়নি। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, গত সরকারের আমলে অর্থনীতির অবস্থা অনেক খারাপ হওয়ার প্রভাব, বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে টাকা ছাপিয়ে ঋণ দেওয়া, সাম্প্রতিক বন্যাসহ বিভিন্ন কারণে মূল্যস্ফীতি বেড়েছে।
কেউ কেউ অবশ্য বলেছেন, বাংলাদেশের মূল সমস্যা মূল্যস্ফীতি নয়, দ্রব্যমূল্য কমিয়ে আনা। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা গেলেও দ্রব্যের যে পরিমাণ মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে, তা কমাতে না পারলে মানুষের দুর্ভোগ কমবে না। বিশ্ববাজারে পণ্যমূল্য অনেকটাই কমে এসেছে। এখন বাংলাদেশে বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখতে পারলে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ সম্ভব।
আগে সমালোচনা থাকলেও বাজারে ইতোমধ্যে বেশকিছু টাকা ছাড়া হয়েছে, সেগুলোকে দ্রুতই তুলে নিতে হবে। এটা স্থায়ী হলে মূল্যস্ফীতির ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। আর দীর্ঘদিন ধরেই আমাদের বাজারে প্রতিযোগিতা অনুপস্থিত। বিশেষ করে ভোগ্যপণ্যের বাজার কয়েকটি ব্যবসায়ী গ্রুপের নিয়ন্ত্রণে। তারা যদি জোট বাঁধে বা সরবরাহে ঝামেলা করে, তাহলে মূল্যস্ফীতিতে সমস্যা তৈরি হতে পারে। এজন্য সরকারকে বিষয়টির দিকে নজর রাখতে হবে। আগামী বোরো মৌসুমে খাদ্যপণ্যগুলো ঠিকভাবে ঘরে তোলা গেলে বাজার নিয়ন্ত্রণ সহজ হবে বলে মনে করেন তাদের কেউ কেউ।
এমনকি ‘বিপ্লবী’ সরকারের অনেক উপদেষ্টা বলেছেন, এই মুহূর্তে দেশের প্রধান সমস্যা অর্থনৈতিক। আর অর্থনৈতিক সমস্যাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় উচ্চ মূল্যস্ফীতি। কয়েক বছর ধরে চলতে থাকা ধারাবাহিক উচ্চ মূল্যস্ফীতির চাপের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে দেশের সাধারণ মানুষ। তাই ভোগান্তিতে থাকা সাধারণ মানুষের মতোই বর্তমান সরকারের অন্যতম চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে উচ্চ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ। এজন্য ইতোমধ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় কিছু পণ্যে শুল্কছাড়সহ বেশকিছু পদক্ষেপ নিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। আগের সরকারও নীতি সুদহার বাড়ানোসহ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছিল। তবে বাস্তবতা বলছে, শিগগির নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হবে না মূল্যস্ফীতি।
দেশে উচ্চ মূল্যস্ফীতির এমন উদ্বেগের কথা বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সর্বশেষ হালনাগাদ প্রতিবেদনেও উঠে এসেছে। সরকারি হিসাবে গত নভেম্বরে পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভিত্তিতে মূল্যস্ফীতি হয়েছে ১১ দশমিক ৩৮ শতাংশ। খাদ্যপণ্যে মূল্যস্ফীতি হয়েছে ১৩ দশমিক ৩৮ শতাংশ। আর শহরে খাদ্য মূল্যস্ফীতি আরও বেশি, যা ১৪ দশমিক ৬৩ শতাংশ। বিবিএসের হিসাবে, গত এক বছর ধরে গড় মূল্যস্ফীতি ১০ শতাংশের বেশি। এত উচ্চহারে মূল্যস্ফীতি এ মুহূর্তে খুব কম দেশেই আছে। দেশে মূল্যস্ফীতি ইদানীং কিছুটা কমলেও খুব সুখবর নেই।
অন্যদিকে খোদ শ্বেতপত্র তৈরির কারিগরদের কেউ কেউ বলছেন, বাস্তব অবস্থা সরকারি হিসাবের চেয়ে বেশি। এ গোত্রের অনেকে অবশ্য আগে থেকেই বলে আসছেন, বাস্তবে মূল্যস্ফীতির হার আরও বেশি হবে। তাদের মতে, বিবিএস যে পদ্ধতিতে মূল্যস্ফীতি নিরূপণ করে, তা সঠিক নয়। বিশেষ করে খাদ্য মূল্যস্ফীতির ক্ষেত্রে সরকারি পরিসংখ্যানের সঙ্গে বাস্তবতার ফারাক বেশি। এতে সামগ্রিক মূল্যস্ফীতির হারেও প্রভাব পড়েছে। গত এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বরে বিবিএসের প্রকাশিত মূল্যস্ফীতির হার ৯ থেকে ১১ শতাংশ হলেও তাদের অনেকের মতে, দেশের প্রকৃত মূল্যস্ফীতির হার এখন ১৫ থেকে ১৭ শতাংশের মধ্যে। তাদের হিসাবে চলতি বছরের এপ্রিলে মূল্যস্ফীতি ছিল ১৫ শতাংশ, মে মাসে ১৫ দশমিক ৩, জুনে ১৫, জুলাইয়ে ১৮ দশমিক ১, আগস্টে ১৬ দশমিক ২ এবং সেপ্টেম্বরে ১৫ দশমিক ৩ শতাংশ।
দরিদ্র মানুষের জীবনে উচ্চ মূল্যস্ফীতির চরম অভিঘাত পড়ছে। এটা এক ধরনের অদৃশ্য ঘাতক। সমাজের সচ্ছল ও ধনী মানুষের ওপর এর তেমন প্রভাব না পড়লেও নিম্নআয়ের মানুষের ওপর এর প্রভাব ব্যাপক। শ্বেতপত্রেই বলা হয়েছে, ২০২২ সালে উচ্চ মূল্যস্ফীতি ও করোনার প্রভাবে দেশের ২৭ লাখ ৫১ হাজার মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমে গিয়েছিলেন।
২০২২ সালে বিশ্বের ১৯৪টি দেশের মধ্যে ১৭৯টি দেশে মূল্যস্ফীতির হার বেড়ে যায়। কিন্তু বিশ্ববাজারে পণ্যের দাম কমায় এরপর থেকে মূল্যস্ফীতির হার কমতে শুরু করে। ধারাবাহিকভাবে কমে ২০২৪ সালের জুনে বৈশ্বিক গড় মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়ায় ৫ দশমিক ৯ শতাংশে। অথচ ধারাবাহিকভাবে বাড়তে থাকা বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতি ২০২৩ সালের আগস্ট থেকে ১০ শতাংশের কাছাকাছি রয়েছে। অর্থাৎ একই সময়ে বিশ্বের অন্য দেশে মূল্যস্ফীতি কমলেও বাংলাদেশে বেড়েছে।
আমরা জানি, দেশের চাল, ডাল, তেলসহ ভোগ্যপণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণ করে হাতেগোনা কয়েকটি শিল্প গ্রুপ। বিগত সরকারের আমলে এসব গ্রুপের কেউ কেউ ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন খাতে লুটপাটে নেতৃত্ব দিয়েছেন। এজন্য অন্তর্বর্তী সরকার তাদের অনেকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সরকারকে বেকায়দায় ফেলতে এসব গ্রুপ ঐক্যবদ্ধ হলে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সরকারের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ তৈরি করবে।
বাজার পর্যালোচনায় দেখা গেছে, দেশের ভোগ্যপণ্যের বাজার অল্প কয়েকটি ব্যবসায়ী গ্রুপের নিয়ন্ত্রণে। তাই মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে হলে বাজারে প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করতে হবে। সরবরাহ শৃঙ্খলে আরও নতুন অংশীজনদের সম্পৃক্ত করতে হবে। আমদানির জন্য নতুন সূত্র খুঁজে বের করতে হবে। সরকার নিজেই কারগিল, ডব্লিউ ডব্লিউ গ্রেইন্সসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ী গ্রুপের সঙ্গে আলোচনা ও সম্পর্ক স্থাপনে যেতে পারে।
তথ্য বলছে, আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে কয়েকজন শীর্ষ ব্যবসায়ী দেশের ব্যাংক খাতের ভিত্তি ধ্বংস করে দিয়েছে। বিশেষ করে রাষ্ট্রায়ত্ত ও শরিয়াহভিত্তিক ব্যাংকগুলো থেকে এমনভাবে লুটপাট করা হয়েছে যে, দেড় বছর ধরে ব্যাংকগুলোর তারল্য সংকট সামাল দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এমন পরিস্থিতিতে লুটপাটের শিকার ছয় ব্যাংকের তারল্য সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশ ব্যাংক ২২ হাজার কোটি টাকার বেশি ছাপিয়ে তাদের সহায়তা দিয়েছে। এটিও মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে অন্তর্বর্তী সরকারকে বড় চ্যালেঞ্জে ফেলতে পারে বলে মনে করেন অনেকে।
বাজারে ছাড়া টাকাগুলো দীর্ঘ সময়ের জন্য স্থায়ী হলে মূল্যস্ফীতির ওপর প্রভাব তৈরি করবে। এজন্য দুর্বল ব্যাংকগুলোর জন্য বাজারে ছাড়া অর্থ দ্রুত তুলে নেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আর সরকার পরিবর্তনের পর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। এটা এখন কিছুটা নিয়ন্ত্রণে নেওয়া গেছে। দ্রুত আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি করতে না পারলে সিন্ডিকেট, চাঁদাবাজি ও অন্য ইস্যুগুলো নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হবে না, যা মূল্যস্ফীতির ওপর সরাসরি প্রভাব তৈরি করবে। এছাড়া বাজার মনিটরিংয়ে ভোক্তা অধিকার ও প্রতিযোগিতা কমিশনের মতো প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরও কার্যকর করার পরামর্শও এসেছে।
পত্র-পত্রিকা বলছে, অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে বেশকিছু উদ্যোগ নিয়েছে। এর মধ্যে প্রধান উদ্যোগ মুদ্রানীতির মাধ্যমে চাহিদা নিয়ন্ত্রণ এবং কিছু নিত্যপণ্যে শুল্ক ছাড় দেওয়া হয়েছে। বিগত সরকারের শেষ সময়ের দিকে মূলত আইএমএফের কাছ থেকে ঋণ নেওয়ার শর্ত হিসাবে মুদ্রানীতির সংকোচন শুরু হয়। আইএমএফের সাবেক এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর হিসাবে দায়িত্ব নেওয়ার পর তিন দফা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতি সুদহার বাড়ানো হয়েছে। যেটা আগেই বলেছি, তাতেও মুক্তি মিলছে না।
এমনকি বেশকিছু নিত্যপণ্যে শুল্ক ছাড় দেওয়া হলেও তার প্রভাব পড়েনি বাজারে। অধিকাংশ নিত্যপণ্য কিনতে হিমশিম খেতে হচ্ছে ভোক্তাদের। নানা উদ্যোগ সত্ত্বেও উচ্চ মূল্যস্ফীতি কেন বাগে আসছে না, তা নিয়ে খোদ সরকারের মধ্যেই অস্বস্তি রয়েছে। সরকারের কোনো কোনো উপদেষ্টা অর্থনীতিবহির্ভূত কারণ যেমন পণ্য পরিবহণে চাঁদাবাজি কিংবা সিন্ডিকেটের কথাও বলছেন।
এক-দুইজন বলেছেন, বাজারে এমনভাবে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে যে ট্যাক্স কমিয়েও নিত্যপণ্যের দাম কমানো যাচ্ছে না। পণ্যের সরবরাহ ব্যবস্থায় চাঁদাবাজি বন্ধ করা যায়নি। দাম বাড়ানোর সিন্ডিকেট ভাঙা যায়নি। মানুষ বলছে পণ্যের দাম কমছে না, অথচ এনবিআর অনেক সুবিধা দিয়েছে। ট্যাক্স কমিয়ে দিলাম, তারপরও নিত্যপণ্যের দাম কমে না।
অন্যদিকে অধিকাংশ ব্যবসায়ীরা বলেছেন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির দৃশ্যমান উন্নতি হয়নি। এর সঙ্গে মূল্যস্ফীতি কমানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির প্রভাবে ঋণের সুদহার অনেক বেড়েছে। অন্যদিকে ডলারের দাম বৃদ্ধি, জ্বালানি সংকট এবং ঘুস-দুর্নীতির মতো সমস্যা রয়ে গেছে। সব মিলিয়ে কারখানার উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে, যা সরবরাহ শৃঙ্খলে সংকট তৈরি করছে। সম্প্রতি বিভিন্ন ফোরামে ব্যবসায়ী নেতাদের কেউ কেউ দাবি করেছেন, মূল্যস্ফীতি কমাতে সুদহার বাড়ানোর নীতি উলটো উৎপাদন খরচ বাড়িয়ে মূল্যস্ফীতিকেই উসকে দিচ্ছে।
উচ্চ মূল্যস্ফীতি বাংলাদেশে একটি কাঠামোগত সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি দিয়ে এর সমাধান করা যায়নি, যাবেও না। বাজারে পণ্যের প্রকৃত চাহিদা নিরূপণ করে পর্যাপ্ত সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে। মুদ্রানীতি, রাজস্বনীতি এবং বাজার ব্যবস্থাপনা, এই তিনের যথাযথ সমন্বয় ঘটাতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, এনবিআর, ট্যারিফ কমিশন, প্রতিযোগিতা কমিশন, ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তরসহ বাজারের সঙ্গে সম্পৃক্ত সরকারি সংস্থাগুলোকে একযোগে কাজ করতে হবে। সর্ষের ভেতরে ভূত থাকলেও তা খুঁজে বের করতে হবে। মধ্য ও দীর্ঘকালে কার্যকারণ খুঁজতে ও সমাধানে আরও গভীর গবেষণা করতে হবে। হয় আমাদের জনসংখ্যা বেশি কিংবা উৎপাদন কম, এমন পরিসংখ্যানগত সমস্যাও হতে পারে।
লেখক : অর্থনীতি বিশ্লেষক

